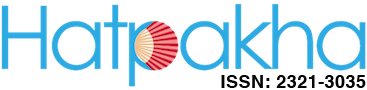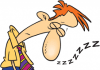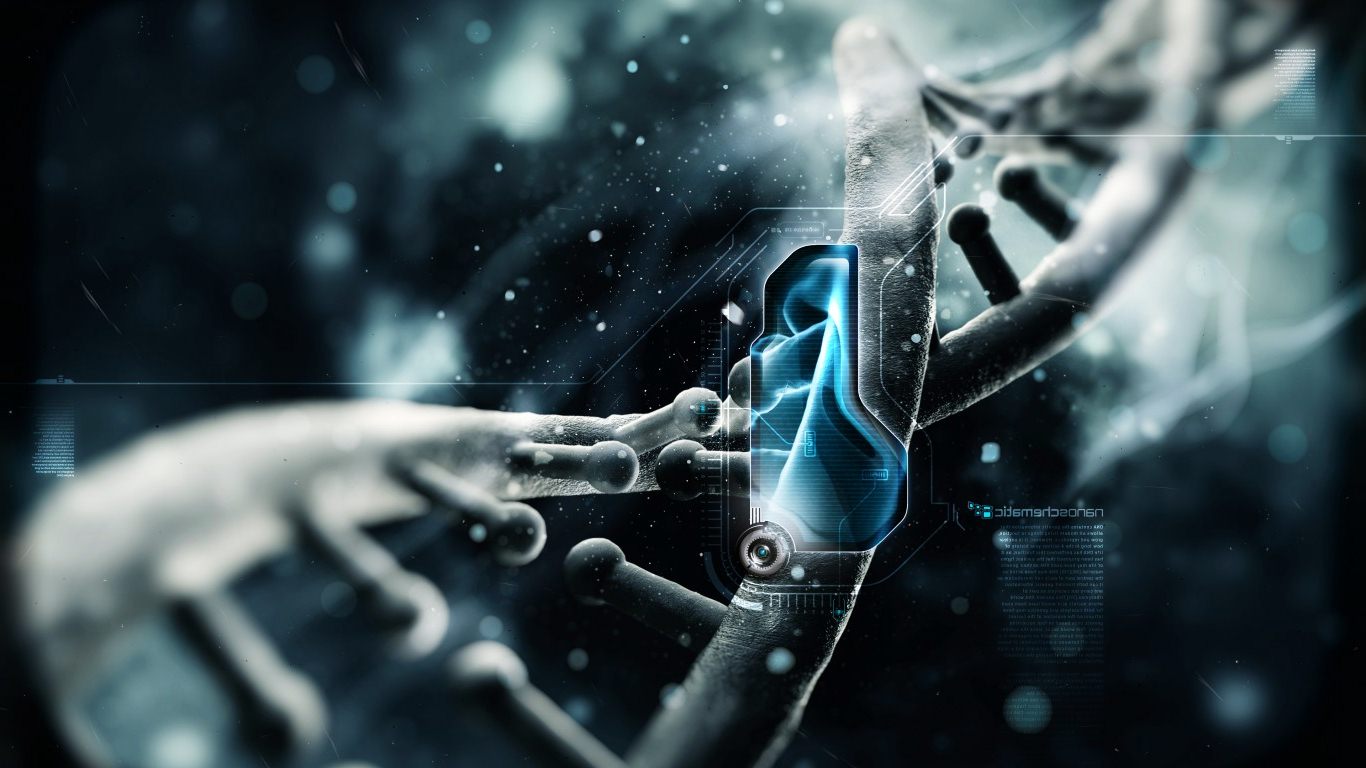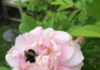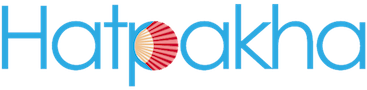হোটেলটার নাম একটি অতি পরিচিত টিভি চ্যানেলের নামে। খাবার যদিও মুখে তোলা যায় না কিন্তু যায়গাটা খুবই মনোরম। ধু ধু মাঠের মধ্যিখানে একটি রেস্তরা। যাকে পরিচিত ভাষায় ‘ধাবা’ বলা হয়। লম্বা বাস যাত্রায় রাতের আহারাদি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে এখানে থামানো। আমি হায়দ্রাবাদ থেকে মুম্বাই যাচ্ছিলাম। যাত্রার ধকল সঝ্য করতে না পেরে বাসে উঠেই শুয়ে পড়ার উপক্রম করি। আর ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটে। প্রথম দিকে অবশ্য বুঝতে একটু অসুবিধা হয়েছিল। যে লোকটার সাথে কামরা ভাগ করে নিতে হয়েছিল তাঁর মুখদর্শনের সৌভাগ্য তখনও হয়নি আমার। শুধু কিছু মৃদু শব্দ উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম। প্রথমবারে মনে হল লোকটা কাউকে মৃদু ভর্ৎসনা করছে। দেশের এই অংশের লোকেরা এমনিতেই পারিবারিক মর্যাদা সম্পর্কে অতি সতর্ক। এইজন্য অনেক সময়ই মহিলাদের উদ্দেশ্যে এ ধরনের কটূক্তি জাতীয় মৃদু ভর্ৎসনার সুর শোনা যায় পুরুষদের মুখে। তাই ব্যাপারটাকে বিশেষ আমল না দিয়ে বরং নিদ্রা যাওয়াকেও বাঞ্ছনীয় মনে হল। তাঁর ওপর আবার পরদিন সকালে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকার দরুন স্বাস্থ্য সুস্থ রাখাও দরকারি। প্রথম থেকেই বাসটা নির্ধারিত সময়ের থেকে তিন ঘণ্টা দেরিতে চলছে। এখন সময়মত পৌঁছুলে হয়। নাহলে আমি যে কোনও সুফল পাব না তা বলাই বাহুল্য।
লোকটার সাথে প্রথম কথা হল এই রেস্তরাঁতে। শুরুটা অবশ্য আমিই করলাম। আমার শয্যাসঙ্গি এই ব্যাপারে একটু উদাশিন মনে হল। মাঝরাতে বাসটা থামার সময়ই ঘোষণা করা হল মাত্র আধ ঘণ্টার হল্ট। যা কিছু পেটে দেওয়ার আছে এর মধ্যেই শেষ করতে হবে। প্রথমে নেমেই একটু হালকা হয়ে নিলাম। তারপর পাশের দোকান থেকে একটা সিগেরেট ধরিয়ে বেশ একটা আমেজের সুখটান দিচ্ছি তখনই নজরে এলো আমার সঙ্গি পেছনের সারির একটা টেবলে বসে চা পান করছে আর হাতের ওপর রাখা একটা গিনি পয়সার ওপর মনোনিবেশ করছে। দূর থেকে গিনিটাকে পিতলের বলে মনে হল। একটু কৌতূহল হওয়ায় এগিয়ে গেলাম। টেবলের কাছে গিয়ে বসবার জন্য আবেদন করাতে লোকটা মুখ তুলে চাইল। এই প্রথম ভাল করে তাঁকে দেখলাম। লোকটার বা চোখটা তুলনামুলক ভাবে একটু ছোট।বা দিকের ভুরুর ওপরে একটা জুরুল আছে। পুরু গোঁফ আর চাপদাড়ির সৌজন্যে অবশ্য মুখের অধিকাংশই আড়ালে, অবশ্য তাঁর একটা অলৌকিক অবয়ব তৈরি করতে বেশি বেগ পেতে হল না। মৌখিক সৌজন্যতায় ভর করে বসলাম তাঁর পাশে। তাঁকে দেখে মনে হল না আমার এই আচরনের প্রতি সে খুব একটা আগ্রহী। নিঃশব্দে নিজের পেয়ালার ওপর মনঃসংযোগ করতে লাগলো।
অতঃপর আমাকেই শুরু করতে হল।
-“আপনি কি মুম্বাই যাচ্ছেন?”- ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে আমি প্রস্ন করলাম
-“না”
-“তাহলে কি পুনে বা অন্য কোথাও?”
-“হিঞ্জেওাড়ি”
বেশ কিছুদিন মুম্বাইতে থেকে এটা আমার জানা ছিল যে হিঞ্জেওাড়ি পুনে শহরের অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম। অবশ্য দ্রুতসম্পাদিত নাগরিকায়নের দৌলতে তা এখন দেশের কর্পোরেট মানচিত্রে একটা নাম। স্বাভাবিক ভাবেই আমার পরের প্রশ্নগুলো সহজেই সাজিয়ে নেওয়া গেল।
-“আপনি তাহলে আইটি তে আছেন?”
-“মোটেই না। ওটা আমার পৈতৃক গ্রাম। হিঞ্জেওাড়ি আইটি পার্ক সম্বন্ধে সবাইরি একটা কৌতূহল অবশ্যই আছে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটা পৈতৃক বাড়িতে সস্তৃক থাকা হয়।”
-“ওহ! তাহলে হায়দ্রাবাদ নিশ্চয়ই কাজের সুত্রে?”
-“হ্যাঁ তা অবশ্য বলতে পারেন। একটা হারিয়ে যাওয়া জিনিসের খোঁজে এসেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে। পেয়ে গেছি তাই ফিরে যাচ্ছি।”
-“কি জিনিস?”
-“সব জিনিস কি আর বলে বোঝানো যায় মিঃ…”
-“বিশ্বাস। কিন্তু এ জিনিস নিশ্চয়ই কোনও দ্রব্য আশাকরি”
-“বিস্বাসে ফিরায় না চায় লাঙ্ঘিত চরণে-
তব হরি কি উপায় সময় এ ভুবনে”
-“বাহ! আপনি দেখছি ভালই শায়েরি (এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হল) করেন। আপনাকে তো মশাই কালটিভেট করতে হচ্ছে।”
-“অনেকেই পারেননি। আপনিও চেষ্টা করতে পারেন।”
-“তাঁর মানে হায়দ্রাবাদ স্রেফ ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে? তবে হায়দ্রাবাদ কেন? গোয়া যেতে পারতেন তো?”
-“আমি সময়কে ধরতে চেয়েছিলাম।”
-“পারলেন?”
একটু অন্যমনস্ক হয়ে পরেছিলেন, হঠাৎ আমার প্রস্ন শুনে চমকে উঠলেন, “কি? কি বললেন?”
-“বলছি ধরতে পারলেন সময়কে?”
-“সে তো সময়ই বলবে”, মুচকি হাসলেন তিনি।
মাঝে মাঝে কিছু চিন্তা তাঁকে ভাবিয়ে তুলছে। সেই গিনিটা নিয়ে অনবরত নাড়াচাড়া করে যাচ্ছেন তিনি। কখনও সামনে কখনও পিছনে হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন।
-“এই জিনিসটা কি বলতে পারেন?”
জিনিসটাকে হাতে নিয়ে দেখলাম আমি। একটু কাছ থেকে নিয়ে বুঝলাম। দূর থেকে যাকে তামার গিনি বলে মনে হচ্ছিল সেটি আসলে একটি সোনার পয়সা। অনেক পুরনো মোহর বা একটি অমুল্যরতন স্বর্ণমুদ্রা। মুদ্রার একদিকে খোদাই করা চিনহ। ঠিক যেমন রাজবংশের থেকে থাকে। মুদ্রার অন্যদিকটায় খোদাই করা একটি মানুষের প্রতিকৃতি। এই স্বল্প আলোতেই বেশ বুঝতে পারছি, এই মানুষটি বেশ সুপুরুষ।
-“দেখে তো মনে হচ্ছে খুব পুরনো একটি স্বর্ণমুদ্রা। কোন রাজবংশের তা বলতে পারব না।”
-“ঠিক ধরেছেন। এটি হল সময়। যার প্রকোপে রাজ্য ভেশে যায়, জীবন শেষ হয়। আমার বংশের একমাত্র চিহ্ন। কিছুদিন আগে হায়দ্রাবাদ চলে এসেছিল, এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সময় এখন আমার হাতের মুঠোয়।”, বেশ দৃপ্ত কন্থে জানালেন তিনি।
ওহ! তিনি মানে গুরুদাস জয়কর। নামটা অবশ্য অনেক আগেই জিগ্যেস করেছিলাম। এত পরে জানাবার ত্রুটি মার্জনা করবেন। কথায় কথায় জানতে পারি গুরুদাসবাবু জন্মসুত্রে একজন মারাঠি। জাতে পাঠাড়ে প্রভু। কথিত আছে ভৃগু ঋষি নাকি রাজা অশ্বপতিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে পাঠাড়ে প্রভুরা কালের ফেরে নিজ রাজত্ব হারিয়ে চাকুরীজীবীতে পরিণত হবেন। তাই অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে আস্তে আস্তে তাঁরা রাজ্যপাট হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রনি ভুমিকা পালন করার জন্য পরের দিকে বিভিন্ন মারাঠি রাজত্বের মন্ত্রিত্বে সফল হয়েছিলেন। এমনকি বলা হয় জাতি হিসেবে সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথাকে নস্যাৎ করে সমাজকে শুদ্ধ করার কাজেও তাঁদের মুখ্য ভুমিকা ছিল। মুম্বাই শহরের অন্যতম পীঠস্থান মহালক্ষি মন্দিরের স্থপতিও একজন পাঠারে প্রভুই। গুরুদাসবাবু একসময় অন্তঃরাজ্য ফুটবলে দাপিয়ে খেলেছেন। একবার নাকি ইস্টবেঙ্গলে ডাক ও পেয়েছিলেন। তখন বাইচুং কলকাতা ময়দান কাঁপাচ্ছে। অমল দত্তের ডায়মন্ড আর পি. কে. ব্যানার্জির ডায়মন্ড কাটার। এই নিয়ে ময়দান সরগরম। এখনও দেখলাম হালফিলের খবর রাখেন। কখন কোন টিম রেলিগেট হচ্ছে বা কে প্রোমোট হচ্ছে সবই তাঁর নখদর্পণে।
রেস্তরাটায় অবশ্য আমিও চা এর ওপরে কিছুই মুখে দিইনি। আধ ঘণ্টার বিরতি শেষে আমাদের সরকযানও পাড়ি দিল নিজের গন্তব্যের দিকে। বাঙ্কে উঠেই গুরুদাসবাবু শুয়ে পরলেন। আমার আবার এত তাড়াতাড়ি শোবার অভ্যেশ নেই। তাই সাথে আনা শরদিন্দু সমগ্রটাই খুলে বসলাম। আস্তে আস্তে আমারও চোখ ঢুলে এল একসময়। আমি তলিয়ে গেলাম নিদ্রার অতল গহ্বরে।
তখন রাত আনুমানিক তিনটে হবে। এ.সি. বাসের পুরু কাঁচের জানালা ভেদ করে বেশি দূর ঠাহর করা সম্ভব নয়। তবুও তাতে চোখ লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। সম্ভবত তেলেঙ্গানার গণ্ডি ছাড়িয়ে আমরা প্রবেশ করেছি মহারাষ্ট্রে। বাঙ্কের ভেতরটাও বেশ অন্ধকার। ওপর থেকে অনবরত নির্গত হিমশিতল আবহাওয়া মাঝে মাঝেই বেশ কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে সারা শরীরে। পায়ের কাছে রাখা চাদরটা টেনে নিলাম। সেটা খুলে গায়ে জড়িয়ে বেশ যুতশই করে শুতে যাব, ঠিক তখনই একটা আকস্মাত দৃশ্য হঠাৎ একটু নাড়িয়ে দিল আমায়। আমার পাশে যে ভদ্রলোক গভীর নিদ্রায় মগ্ন তাঁকে ভাল করে দেখার সৌভাগ্য এই প্রথম হল আমার। যা রেস্তোরার একশ পাওয়ারের আলো আমাকে দেখাতে দেখাতে পারেনি এখন এই নাইটল্যাম্পের আলোয় তা যেন দিনের মত পরিষ্কার। ঘুমের মধ্যে অসাবধানতায় হঠাৎই তাঁর চেহারার পলেস্তারা খশে পড়েছে। দাঁড়ি, গোঁফ সুদ্ধু লোকটাকে যেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মনে হয়। ওপরের আস্তরণ, মায় পরচুলাটাও এখন আর তাঁর মালিকের সঙ্গ দিতে রাজি নয়। এসবের মধ্যে একমাত্র বিদ্যমান হল সেই জুরুলটা। এবং সেটার সাহায্যেই গুরুদাসবাবুর এহেন অভিচরন চাক্ষুষ করার উপলব্ধি হল আমার। অনবরত গোয়েন্দা গল্প না পরলেও যে সহজ প্রস্নটা এই সময় সবার মনে অবশ্মভাবি তা হল, কেন? গুরুদাসবাবু কেন বা কীজন্যে এই ছদ্মবেশ ধারন করতে গেলেন তা অবশ্য এই অদ্ভুত বেশধারী লোকটির মনের অন্তরে শায়িত।
এরকম অবস্থায় কতক্ষন ছিলাম তা অবশ্য জানা নেই। বেশ কিচ্ছুক্ষন ধরেই অলীক কল্পনা করে যাচ্ছিলাম। আমার চিন্তায় ছেদ পরল বাসটা থেমে যাবার পর। পুনে পৌছতে এখনও দুঘণ্টা। এই মাঝরাতে হঠাৎ আজানা যায়গায় অসংকল্পিত ও অকস্মাৎ পথরুদ্ধ হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তার উদ্রেক হল। আর সেই চিন্তার ফলস্রুতি আগামি দুর্ঘটনার প্রতিরক্ষা স্বরূপ কিচ্ছু পদক্ষেপ মনে মনে ঠিক করে নেওয়া গেল। জানালা দিয়ে দেখার অবশ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিধি বাম। এই অন্ধকারে দৃষ্টি খুব বেশি দূর অগ্রসর হয়না।
শুধু এইতুকু বোঝা গেল সামনে একটা জীপ আমাদের পথ আগলে আছে আর বাসের ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে।
“যা থাকে কপালে”, এই ঠিক করে ব্যাংক থেকে নামতে যাচ্ছি অমনি আমার ডান হাতের কব্জি খপ করে ধরলেন গুরুদাসবাবু। ভদ্রলোক অনেক্ষন উঠেছেন। আমি অবশ্য খেয়াল করিনি। তাঁর বেশভূষা এখন অনেকটাই মার্জিত। তাঁর ছদ্মবেশ আবার যথারীতি নিজের অবস্থান গ্রহন করেছে।
তাঁর এই আচরণে যথারীতি বিরক্ত হয়ে তাঁর দিকে চাইতেই ভদ্রলোক পকেট থেকে সোনার গিনিটা বের করে আনলেন। তারপর সেটা আমার হাতে দিয়ে চাপা গলায় আমতা আমতা করে বললেন,”দয়া করে এটা মহালক্ষ্মী মন্দিরের পূজারীর হাতে দিয়ে দেবেন”। বলেই ভদ্রলোক লাফ দিয়ে নেমে পরলেন ব্যাংক থেকে।
ঠিক পাঁচ মিনিট পর সম্মিলিত বুটের আওয়াজে কৌতুহলবসত ব্যাংক থেকে নেমে দেখি কয়েকজন উর্দিধারি পুলিশের আগমন ঘটেছে সরকযানটার ওপরে। যাত্রিদের ধরে ধরে তাঁরা কিছু জিগ্যাসাবাদ করছে। তাঁদের মধ্যে একজন তাগরাই গোছের হাবিলদার আমার কাছে এগিয়ে এল। ব্যাপারটা কি জিগ্যেস করাতে, আমার চোখের সামনে একটা প্রিন্ট করা ফোটো তুলে ধরে জিগ্যেস করল,”ত্যালা ওরাক্তোস কা? আতা হায়দ্রাবাদচ্যা বাস মধে বসলা আহে”। অর্থাৎ আমি এই ছবির অধিকারীর কোনও খোঁজ দিতে পা্রি কিনা?
-মরেছে! আমি এমনিতেই মিতভাষী আর সংযমী। অকারণ দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়ই মনে করি। আর আমাকেই কিনা এখন সাক্ষ্য দিতে হবে পুলিশের কাছে?
একটু অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর হাতের ফটোটা নিয়ে একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু একি! এ কার ফোটো? এ মুখ তো আমার ভোলবার নয়। রাতের অন্ধকারেও যার মসৃন ভাবলেশহীন মুখমণ্ডল আমাকে চিন্তাশীল করে তুলেছিল, সেই গুরুদাস জয়করকে পুলিশ খুঁজছে। এই জন্নই কি?…
আমি আর ভাবতে পারলাম না। আমার পায়ের তলা থেকে মাটি আগেই সরে গেছিলো। মাথাটা ঘোরাচ্ছে হঠাৎ। একটু অস্বস্তি হচ্ছে। সামনে দাড়িয়ে থাকা, তাগরাই হাবিলদারটাকে একটা মেকি হাসি হেসে, মুহূর্তে সরে এলাম সেখান থেকে। বাঙ্কে উঠেই চাদর মুরি দিয়ে শুয়ে পরলাম। শরীরটা থেকে থেকে কাঁপুনি দিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে।
সেদিন আর অফিসে যাওয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই আমার মিটিংও ভেস্তে গেল। সারাদিন ধরে পুলিশের কাছে বিবৃতি দিয়ে আর কিছু জরুরী কাজ সেরে বিকেলবেলা বাড়িতে এসে ভাল করে স্নান করে নিলাম। জ্বরটা আর আসেনি। ড্রইংরুমের ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে একটা সিগেরেট ধরালাম। গুরুদাসবাবুর জন্মসুত্র সেদিন পরিষ্কার হয়নি আমার কাছে। পরে ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের কাছ থেকে জানতে পারি কিছুটা। তবে যতটুকু শুনলাম, তাতে এটুকু বুঝেছি যে মান সন্মানের জন্য মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে। অবশ্য সেটা আরও ভালো ভাবে বুঝতে গিয়ে বেশ কিছুটা ইতিহাসের বই ঘাটতে হয়েছে আমাকে। আর কিছুটা সেই ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের কাছ থেকে শোনা। বাকিটা আমার আন্দাজ। এই তিনে মিলে যা দাড়িয়েছে তা হলঃ
সতেরশো খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া বাজিরাওএর সাথে রানি মস্তানির বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিয়েটা অবশ্য বুন্দেলখন্ডের রাজা ও পেশয়াদের মধ্যে একটা সুকৌসুলি মৈত্রিবন্ধনের সুত্রে। রানি মস্তানির মা রুহানি বাঈ ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজসভার নৃত্যশিল্পী। অবশ্য এই নিয়ে অনেক রকম লেখা ও তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তবে সব তথ্য যে সঠিক তাঁর কোনও অকাট্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত্য মেলেনি। মহারাজা ছত্রশাল তখন যৌবনের পাদদেশে। মোঘল সম্রাট ওউরংজেবের সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ করে মোঘলদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন। আর গোয়ালিয়রের পুর্বে রিবা, সাগর, পান্না ও দমো জুড়ে জয় করলেন বিশাল প্রান্তর। এখানেই গড়ে উঠল তাঁর রাজ্য। নাম হল বুন্দেলখন্ড। ছত্রশাল ছিলেন বুন্দেলা উপজাতির রাজপুত। আর সেখান থেকেই এমন নামকরন। ইতিহাসবিদদের মতে ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের পর মহারাজা ছত্রশাল এবং বুন্দেলা উপজাতির মধ্যে বিভেদের কারণে বুন্দেলখন্ডের বহু শক্তিক্ষয় হয়। এই ক্রমাগত অন্তরকলহ থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার জন্য তিনি পারি দেন দেশের দক্ষিণ প্রান্তে। এই সময় দক্ষিনেও মোঘলদের রাজত্ত ছিল। মোঘলদের হয়ে বড়লাট (Chief Viceroy) ছিলেন কামারুদ্দিন খান নামক এক সাহসী ও শক্তিশালী যুবক। এই কামারুদ্দিন খানই ১৭২৪ সালে হায়দ্রাবাদের স্থাপত্য করেন মোঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের সেনাপতিকে হারিয়ে। সম্রাট তখন তাঁকে মোঘলদের সর্বচ্চ সম্মান ‘আসফ-জাহ’-তে ভূষিত করেন। যাই হোক, কামারুদ্দিন খান ছিলেন আলাদা মেজাজের লোক। তাঁর আশেপাসে সর্বসময়ের সুরক্ষা বেস্টনিতে থাকত কিন্নরদের নজরদারি। তাঁর আয়েশের সামগ্রি হিসেবে সর্বদা তৈরি রাখা হত সুন্দরী বাইজীদের। এই বাইজীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিলেন রুহানি বাই। রুহানি বাঈয়ের সৌন্দর্য খ্যাতি তখন মোঘল সাম্রাজ্যের গলিতে গলিতে শোনা যেত। এবং অতি স্বাভাবিক ভাবেই একসময় সেই খ্যাতি এসে পরে ছত্রশালের কানে। ছত্রশাল যদিও তখন মধ্যবয়সী তবুও তো রাজা। তাই হয়তো রুহানি বাঈও তাঁর আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হয়নি। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মহারাজা ছত্রশাল যখন তাঁর সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হন তখন দুজনে কামারুদ্দিন খানের রাজত্য থেকে পালিয়ে বিবাহ করেন। তিনি হলেন মহারাজার কনিষ্ঠতম রানি। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের একটি কন্যাসন্তান জন্মায়।
সর্বকনিষ্ঠ ও একমাত্র কন্যাসন্তান বলে মাস্তানির ওপরে রাজা ছিলেন বিশেষ স্নেহপ্রবন। বুন্দেলা উপজাতির নারীরা এইসময় উচ্চস্বাধিনতা উপভোগ করতেন। তাঁদের পালন করা হত রাজ্যের অন্য পুত্রসন্তানদের মতই। তাঁদের সম্বোধন করা হত ‘কুমারসা’ বলে। তাই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মস্তানি কুমারসা তাঁর ভাই হরদেসাহ, পদম সিংহ আর জগত্রাজের সাথে যুদ্ধকৌশল শিখতে শুরু করেন। আনুমানিক ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে মোঘল সেনাপতি মহম্মদ খান বাঙ্গশ যখন ছত্রশালের রাজত্ত আক্রমন করেন, তখন মস্তানি ও জেঠ কুমারসা (জগত্রাজের স্ত্রী) বুন্দেলখন্ডের নারী বাহিনিকে নেতৃত্ব দেন ও জগত্রাজকে মোঘলদের হাত থেকে রক্ষা করেন। মহারাজা ছত্রশাল তখন মোঘলদের হাত থেকে রাজ্য রক্ষা করার স্বার্থে পেশোয়া বাজি রাওএর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। পেশোয়া বাজি রাওএর বিরত্বের পরিচিতি তখন দেশের প্রতিটি প্রান্তে। তিনি তখন নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে গোয়ালিয়রের কাছেই ছিলেন। তাঁর সাহায্যে ও নারী বাহিনির বীরত্বে নির্ভর করে মোঘলদের পরাজিত করেন ছত্রশাল। তখনকার অতি সক্রিয় রেওয়াজ অনুযায়ী এই জয়ের ফলে মহারাজা ছত্রশাল পেশোয়া বাজি রাওকে ‘ডোলা’ (যুদ্ধজয়ের পুরস্কার) স্বরূপ তাঁর একতৃতীয়াংশ রাজত্ত আর কন্যা মস্তানির সাথে বিয়ে দেন। এর সাথে দেন ৩৩লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো তখনকার বুন্দেলখন্ডের অন্যতম সেরা সংকলন বলা যেতেই পারে। এই স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে যেটি সবচেয়ে দামি সেটি হল অমুল্য রতন। এই অমুল্য রতনই গুরুদাসবাবু আমাকে সেদিন রেস্তোরায় বসে দেখিয়েছিলেন। এই রত্নটার অন্যতম আকর্ষণ হল ভাগ্য। পেশোয়াদের মতে এই রত্ন যার কাছেই গেছে সেই সুসময়ের অধিকারি হতে পেরেছে। সম্প্রতি নিজামের বংশের একজন উত্তরাধিকারী এই রত্নের খোঁজ পায় এবং কোনও উপায়ে সে সেটাকে আত্বস্মাত করে। ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা ছত্রশালের মৃত্যুর পর তৎকালিন বুন্দেলখন্ডের মধের অন্তরকলহ বেড়ে যায়। অবশেষে একসময় তাঁর থেকে ছোট ছোট রাজ্য যেমন ঝাঁসি, চিত্রকুট, খাজুরাহো আলাদা হয়ে যায়। এই সময় বুন্দেলখান্দের রাজধানি পান্নার রাজপাট গ্রহন করেন হরদেসাহ। গুরদাসবাবু হলেন এই হরদেসাহের বংশধর। পান্নায় থাকাকালীন গুরুদাসবাবু জানতে পারেন এই রত্নটার কথা। তখন অবশ্য তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। যারপরনাই সময়কে ধরার জন্য প্রথমে নাম ও পরিচিতি বদল করে মুম্বাই ও তারপর পুনের হিঞ্জেওাড়ি। পাঠারে প্রভুর গল্পটাও ওই সময়ই বানানো। তাঁর পরের গল্পটা অতি সংক্ষেপে। হায়দ্রাবাদে গমন ও ফিরে আসার সময় আমার সাথে সাক্ষ্যাৎ, মাঝের এই সময় গুরুদাসবাবু কোথায় ছিলেন, কিভাবে তিনি এই অমুল্যরতনের খোঁজ পান, এবং সেটাকে কিভাবে দখল করেন এই সময়ের কোনও হদিশই অবশ্য পুলিশ দিতে পারেনি অথবা দিতে চায়নি। তাঁরা অবশ্য গুরুদাসবাবুকে হায়দ্রাবাদেই ধরতেন কিন্তু বাঁধ সাধল আমাদের বাসটা লেট করাতে। সময় মতন পৌছুতে না পেরে বাসটা শহরের অন্য প্রান্তে এক জায়গায় হল্ট করে আর তারপর অন্য একটি টেম্পো করে যাত্রিদের ঘুর পথে পৌঁছে দেওয়া হয় শহরের বাইরে দাড়িয়ে থাকা বাসটায়।
সময় নিজের দাম ঠিক করে নেয় নিজেই। বাসটা লেট করেছিলো বলেই গুরুদাসবাবু সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়ার মুহূর্তে তাঁর সময়কে তিনি কেন যে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন তা জানতে পারিনি এখনও। আমার কাছ থেকে এতটা ভরসাই বা পেলেন কি করে। আমি যদি গিনিটা সেদিনই পুলিশের হাতে তুলে দিতাম। তাহলে তো তাঁর সমস্ত কাজ ও কৌশল ব্যর্থ হত। আর এখন সবচেয়ে বড় প্রস্ন হল সত্যিই কি গিনিটার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে? সত্যিই কি সেটা ভাগ্য বদলায়? মুম্বাইগামি আমাদের বাস হঠাৎই লেট করা আর আমাদের মানে যাত্রিদের ঘুর পথে নিয়ে যাওয়াও কি গিনিটার আনা সৌভাগ্যের ফল। যে সৌভাগ্যের ফলে এখনও গুরুদাসবাবু বেঁচেবর্তে আছেন। আর তাছাড়া গিনিটার যদি এরকম কোনও ক্ষমতা থেকেই থাকে তাহলে কি তাঁর ফল অন্ন কেউ ও ভোগ করতে পেরেছে? এই ধরুন যেমন নিদেনপক্ষে আমি। গিনিটা সেইদিন থেকে মানে আজ প্রায় এক মাস হয়ে গেলো আমার কাছেই রয়েছে। কই আমি তো এমন কিছু অনুভব করিনি বা বুঝিনি যাতে আমি বলতে পারি যে আমার ভাগ্য খুলেছে। যেদিন গিনিটা আমি প্রথম পেলাম সেদিনও অবশ্য আমার আঁখেরে কোনও লাভই হয়নি। বরং আমার একটি ইম্পর্টেন্ট মিটিং মিস হওয়াতে একটা বড় ডিল হাতছারা হয়েছে। তাই এখনি অবশ্য এটা বলা ঠিক হবে না যে আমার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে।
এত কিছুর পরেও আমি অবশ্য সেই গিনিটা এখনও আমার কাছেই রেখেছি। অবশ্য এই ব্যাপারে যে আমি খুব একটা উৎসাহী ছিলাম তা কিন্তু নয়। বরং দু দু বার মহালক্ষী মন্দিরে আমি গিয়েছিলাম গিনিটাকে ফেরত দেবার জন্য। সে আরেকটা ঘটনা। মহালক্ষী মন্দিরের প্রধান পূজারী গোবিন্দ গোখলে মহাশয় অতিশয় ধার্মিক ও জ্ঞানী পুরুষ। তাছারা তাঁর বয়সও হয়েছে অনেক। জীবনের প্রায় আশি বসন্ত পার হওয়া এই পুরুষটি এখন বয়শের ভারে নাকি ভীষণ অসুস্থ আর তাই বাইরের লোকের সাথে দেখা করবেন না। অনেক করে অনুরোধ করার পরেও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। পাঠকেরা হয়তো বলতে পারেন এত কিছু করার চেয়ে আমি গিনিটা পুলিশের হাথে দিলাম না কেন? এইসব ব্যাপার নিজের কাছে না রাখাই ভালো। সত্যি কথা বলতে তা কিন্তু নয়। আসলে আমার লোভ ছিল সময়ের ওপর। হয়তো কোনোদিন সত্যি সত্যি সময় আমাকে ধরা দেবে, কিম্বা কোনও সত্যির কাছে হয়তো সময় থাকতে পৌছুতে পারব। তাই বা কম কিসের?…