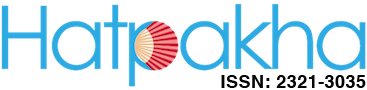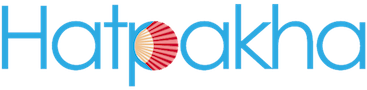<< ট্রাম্প ওবামার দেশে: বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা – ১ম পর্ব
হিথ্রো টু ডালাস
ঠিক সন্ধ্যে ৬ টায় আমেরিকান এয়ারলাইন্সের গেটে চেক-ইন শুরু হল। আমরা সময়মত সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম কঠিন নিরাপত্তা তল্লাশি পর্ব। জুতা, মোজা, জামা বেল্ট সবই খুলে চেক করা হল। গায়ে থাকলো শুধু মৌলিক পোশাক, যা না থাকলে নিজেকে সভ্য সমাজের অংশ ভাবা যাবে না।
তল্লাশির সময় নিরাপত্তা কর্মীরা এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন আমরা ওসামা বিন লাদেনের জ্ঞাতি গোষ্ঠী,যদিও আমাদের কারোই চেহারা সুরতে বিন লাদেনের কোন ছাপের চিহ্নমাত্র নেই। আমার মুখ মন্ডলের আকার লম্বাটে নয়, তাতে দাঁড়ি গোঁফও নেই। যাহোক নিরাপত্তা বুহ্য পার হয়ে বিশাল আকৃতির ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বিমানে গিয়ে উঠলাম। এবারও সিট পড়লো জানালার কাছে। আটলান্টিক মহাসাগর দেখার অপূর্ব সুযোগ পেলাম। যথাসময়ে বিমান আকাশে উড়ল।
তখন কেবল সূর্য আটলান্টিকের কোল ঘেঁষে অস্ত যাচ্ছে। আকাশের সর্বত্র লাল আর কমলা রংয়ের মাখামাখি। নিচে মহাসাগরের নীল রং। রংয়ের খেলায় আকাশ এবং সমুদ্র যেন আনন্দে মেতে উঠেছে। ওরা যেন হলি উৎসব করে প্রতি সন্ধ্যা ও সকালে। সব কিছু মিলে মায়াময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফ্লাইটে কোন কবি থাকলে কাগজ কলম নিয়ে একটি ছোট্ট কবিতা তিনি নিশ্চয় লিখে ফেলতেন। আমাদের গ্রুপে কোন কবি ছিল না বিধায় এ সুযোগটা কেউ কাজে লাগাতে পারেনি। আমার মধ্যে কবি ভাব জাগ্রত হল কিন্তু তা প্রকাশ করা ক্ষমতা ছিল না।
আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটের সকল ফ্লাইট এটেন্ডেন্ট বা বিমানবালা দেখলাম বেশ বয়স্ক এবং শারীরিকভাবে দারুণ শক্তিশালী। আমেরিকার সবগুলো এয়ার লাইনের এখন এ অবস্থা। ইমিরাতের ফ্লাইটে ছিল অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়ে। চেহারা সুরতও বেশ আকর্ষণীয়। আমেরিকানরা কেন বেশি বয়সের লোকজনকে ফ্লাইট এটেন্ডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেন সে বিষয়টি আমার বোধগম্য হল না।
ফ্লাইটে যাত্রীদের সেবা যত্নের পাশাপাশি হাইজাকার রূপী যাত্রীদের দমন করার জন্যই এসকল এয়ার মার্শাল কাম ফ্লাইট এটেন্ডেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে মনে হল। একের ভিতরে দুই, লোক একজন সার্ভিস দিবে দু’প্রকারের। কিছুক্ষণ বাদে যাত্রীদের আপ্যায়ন পর্ব শুরু হল। যত্নে কোন কমতি হল না। হিথ্রো টু ডালাস ছয় ঘণ্টার পথে বেশ কয়েকবার খাবার দেয়া হল। কিছু ড্রাই স্ন্যাকস ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সাথে নিলাম।
হিথ্রো থেকে উড়াল দেয়া বিমানটি ল্যান্ড করবে ডালাস বিমান বন্দরে, টিকেট ও বোর্ডিং পাসে এরকমটি লেখা আছে। আমার ধারণা ছিল এটি টেক্সাসের ডালাস। ঢাকা থেকে যখন আমেরিকার পথে রওনা দেই তখন এরাইভাল এবং ডিপার্চার পোর্ট নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। আমেরিকা যাচ্ছি এটাই বড় কথা, কোন বিমান বন্দর থেকে যাত্রা শুরু হবে এবং কোথায় গিয়ে শেষ হবে এটা নিয়ে ভাবনা ছিল না মোটেই। ডালাস বিমান বন্দরে নামার পর বুঝলাম এটি টেক্সাসের ডালাস নয়, এটি হচ্ছে ভার্জিনিয়ার ডালাস। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি ভার্জিনিয়া এবং মেরিল্যান্ডের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত।
ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস থেকে ভিসা দেবার সময় সিল গালা একটি ডকুমেন্ট হাতে ধরিয়ে দেয়া হল এবং বলা হল এটি যেন ডালাস ইমিগ্রেশনে গিয়ে জমা দেই। স্টেট ডিপার্টমেন্টের গেস্ট এ কারণেই হয়তো এ বিশেষ ব্যবস্থা। নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল, যদিও ঐ ডকুমেন্টের বিষয়বস্তু কখনই জানা হয়নি। এয়ারপোর্টে কোন ঝামেলা হবে না, এমনটি আমরা আশা করছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। বিশাল এক গ্যাঞ্জামে পড়ে গেলাম ডালাস এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন কর্তা ব্যক্তিদেরই হাতে।
বের হবার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার সহাস্যে জানতে চাইলো আমাদের ভিজিট প্রোগ্রাম কে স্পন্সর করেছে। আমি জবাবে বললাম স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব ইউএসএ। মনে হল অফিসার মাইন্ড করেছেন। তিনি মৃদু প্রতিবাদের ভাষায় বললেন ‘তোমাদের ভিজিটের টাকা আমাদের পরিশোধিত ট্যাক্স ও ভ্যাটের অর্থ থেকে এসেছে’। তার কথার আগা মাথা কিছু মগজে ঢুকল না। হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন তাদের সরকার মানেই জনগণ বা জনগণ মানেই সরকার। আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্রের সেই বিখ্যাত সংজ্ঞা এদের চিন্তা ও কাজে প্রতিফলিত হয়।
আমেরিকান সরকার কোন ব্যবসা করে না। বাস বা বিমান চালায় না বা টেলিফোন লাইনের সংযোগও দেয় না। সরকারের কাজ হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষা বিধান আর এসব কাজে অর্থায়নের জন্য জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স তোলা। এ ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে সরকার তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালায়-এরকম এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ঐ ইমিগ্রেশন কর্তা আমাকে শোনালেন। প্রায় দু’দিনের ভ্রমণ শেষে ভীষণ ক্লান্ত থাকায় বিশাল বিপুর কৃষ্ণাঙ্গ ঐ অফিসারের কথায় সামিল হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না।
চারপাশে সবাই যেন কথা বলার জন্য মুখিয়ে আছে। শোনার লোকের বড়ই অভাব। মাথা নাড়িয়ে মৃদু সম্মতি দিয়ে বের হয়ে আসলাম। আমার মনে হল ঐ অফিসার পুলিশের চাকরির আগে নিশ্চয় কোন কলেজের লেকচারার ছিল। এখন যাকে পায় তাকেই লেকচার শুনায়। গণতন্ত্রের লেকচার, আমেরিকান সরকার কিভাবে চলে তার লেকচার। ভদ্রলোক পুরানো অভ্যাস এখনো ভুলতে পারেনি!
আমি এ পর্যন্ত যতগুলো দেশ ভ্রমণ করেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বাজে ইমিগ্রেশন দেখেছি দক্ষিণ কোরিয়ায়। এখানকার ইমিগ্রেশন পুলিশকে বলা যায় অপদার্থের হাড্ডি। আপনার পাসপোর্টে ঠিকমতো ভিসা থাকলেও ওরা সেটি অযথাই উল্টো পাল্টা করে খুঁটে খুঁটে দেখবে। অফিসিয়াল পাসপোর্টেও কোন ছাড় নেই। ওদের কাছে মনে হয় যারা দক্ষিণ কোরিয়ায় আসে তারা সকলেই অবৈধভাবে এসেছে এবং তারা দেশটাকে লুটেপুটে খাবে। একবার কোইকার আমন্ত্রণে কোরিয়া ভ্রমণের সময় আমার এ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। মনে হচ্ছিল কোরিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশের এ আচরণের বিষয়টি ওদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনি। সময়ের স্বল্পতার কারণে সেটি আর হয়ে উঠেনি। আমার মনে হয়েছে কোরিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশের আগত বিদেশিদের সাথে আচরণ ব্যবহার সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দরকার।
ফ্লাইটে থাকা অবস্থায় এয়ার হোস্টেজ একটি অবতরণ ফরম হাতে দিলো পূরণ করার জন্য। লম্বা ফ্লাইটের ক্লান্তির কারণে ফরম পূরণে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলো। ইমিগ্রেশন অফিসার বেশ বিনয়ের সাথেই ফরমটি সংশোধন করে আনতে বললেন। মনে হল উনি বিষয়টি ইগনর করলেও পারতেন। যাহোক ইমিগ্রেশন এর পর কাস্টম খুব সহজেই পার করলাম। কাস্টম কর্তাব্যক্তি কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই সোজা চলে যাবার জন্য বললেন। লাগেজে জামা কাপড় ছাড়া আর তেমন কিছু ছিল না। লাগেজ চেক করে কিছুই পাবে না। তাই ঝামেলা হবারও কথা নয়।
বিমান বন্দরের বাইরে ওয়েটিং রুমে এসে দেখলাম একজন ষাট বছরের কাছাকাছি বয়সের ভদ্র মহিলার সাথে তারেক এবং শহীদ বেশ আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে। আমার বুঝতে দেরী হল না এ মহিলাই হচ্ছে আমাদের গাইড। পুরো একমাস তিনি আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে তথ্য প্রযুক্তি স্থাপনাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাবেন। ঢাকা থেকে এরকমটিই আমাদের আভাস দেওয়া হয়েছিল।
‘মাই নেম ইজ মেরী গার্থ’ বলে সহাস্যে তিনি আমার দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমিও নিজের পরিচয় দিলাম। এ পর্যায়ে পার্থ’র বিষয়ে জানতে চাইলাম তার কি অবস্থা। পার্থ এখনো ইমিগ্রেশন পার হয়ে বের হতে পারেনি। প্রথমে মনে করেছিলাম হয়তো দু’ চার মিনিটের মধ্যে সে চলে আসবে। কিন্তু বেশ কিছু পরে বুঝতে পারলাম পার্থ বেশ ঝামেলায় পড়ে গেছে। ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে সহজেই ছাড়ছে না। আমেরিকান দূতাবাস থেকে দেয়া সিল বন্ধ পত্র তাকে কতটুকু সহায়তা করতে পারবে তা কেবল স্রষ্টাই জানেন।
এরমধ্যে এক ঘণ্টার বেশি সময় পার হয়ে গেছে। মেরীসহ আমরা সকলেই বেশ ঘাবড়ে গেলাম। একে একে পুরো বিমান বন্দর খালি হয়ে গেছে। ভিতরে থেকে বের হবার মত খুব কম যাত্রীই আছে। পার্থসহ চার পাঁচ জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিশেষ কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। এ খবর আমায় দিলেন একজন ইমিগ্রেশন স্টাফ। তিনি আমাদের ধৈর্য ধরে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন।
অপেক্ষার পালা লম্বা হচ্ছে। দেখতে দেখতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ইতোমধ্যে আমরা পার করে দিয়েছি। ক্ষুধায় পেটের নাড়ি হজম হয়ে যাবার মতো অবস্থা, যদিও টেনশনে ক্ষুধার কথা প্রথম দিকে অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলাম। মনে মনে পার্থর সহি সালামতের জন্য স্রষ্টাকে ডাকছি। তার সর্বশেষ হাল হকিকত জানান জন্য মেরী সব রকমের চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম পার্থ ডালাস ইমিগ্রেশন পার না হতে পারলে পুরো ট্যুরের আনন্দই মাটি হয়ে যাবে।
প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে পার্থ যখন বিদ্যুৎ গতিতে গেট দিয়ে বের হয়ে আসলো তখন ঘটনাটি জানার জন্য আমরা একযোগে হড় হড় করে একগাদা প্রশ্ন ছুঁড়লাম। পার্থ এগুতে এগুতে সংক্ষেপে যা বলল তার সারমর্ম হচ্ছে ডালাস ইমিগ্রেশন চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দৈব চয়ন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করেছে। এদের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে পার্থ পড়ে গেছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে চারজনকেই সহি সালামতে ইমিগ্রেশন ছেড়ে দিয়েছে। কাউকেই রিটার্ন টিকেট কাজে লাগাতে দেয়নি। তবে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা তাকে যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলো জানার মতো ধৈর্য ঐ সময় আমাদের কারোই ছিল না। বিষয়টি সবাই এড়িয়ে গেলাম। ভাবলাম পরে কোন এক সময় জেনে নিবো। দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে পুনরায় আড়াই ঘণ্টা এয়ারপোর্টে লম্বা প্রতীক্ষা আর ইমিগ্রেশন কর্মকর্তার প্রশ্নবাণে পার্থ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এটা ওর চোখে মুখে বেশ স্পষ্ট। আমরা বাকীরাও একইভাবে ক্লান্তিতে আকণ্ঠ নিমগ্ন।
আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই মেরী হোটেলে যাবার জন্য গাড়ি ভাড়া করে ফেলেছে। সকলেই যার যার লাগেজ নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। পাজেরো টাইপের বিলাসবহুল গাড়ি। ড্রাইভার ভারতের পাঞ্জাবী সর্দার। গাড়িতে উঠার সাথে সাথে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলো আমরা ভারতীয় কিনা। চেহারা সুরতে ভারতীয় এবং বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক মিলের কারণে এ ধরনের ভ্রম প্রায়ই ঘটে থাকে। গায়ের রং দিয়ে আমাদেরকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে।
স্বাভাবিক কারণে বিদেশের মাটিতে স্বদেশী লোকের সাথে সাক্ষাত পাবার জন্য সকলের মতো এ পাঞ্জাবী সর্দার দেখলাম বেশ উদগ্রীব। যাত্রী হিসেবে আমাদের পেয়ে তিনি নিশ্চয় অনেক খুশি হয়েছেন, তার স্বতঃস্ফূর্ত কথাবার্তা এবং আচার আচরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে। পাঞ্জাবি ড্রাইভারটি বেশ স্মার্ট বলতে হবে। সে তার সিটের পাশে রাখা ল্যাপটপে ঐশ্বরিয়া রায়ের গানের ভিডিও চালাচ্ছে। গানের বিষয়ে আগ্রহ নেই, এ মুহূর্তে আমার আকর্ষণ ডালাস থেকে ওয়াশিংটন ডিসি যেতে রাস্তার দু’পাশের দৃশ্য। রাত প্রায় এগারো টা’র মতো তখন বাজে। রাস্তায় গাড়ি চলাচল কমে এসেছে। দু’পাশে সারি সারি গাছ। মনে হল এক গহীন বন বনানীর সমারোহ। তাতে চেরি আর মেফেললিফের মাখামাখি। এর মাঝ দিকে দ্রুত বেগে গাড়ি এগিয়ে চলছে।
অনেক বিদেশি আছেন যারা বাংলাদেশকে সেভাবে চেনেন না। তারা বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান জানতে চান। এ প্রসঙ্গে না চাইলেও ভারতকে টেনে আনতে হয়। পৃথিবী বহু দেশ আছে যেগুলো আয়তনে বাংলাদেশের চাইতে অনেক ছোট কিন্তু এক নামে তাদেরকে সকলেই চেনে। পরিচিত করার জন্য প্রতিবেশী বড় দেশকে টেনে আনতে হয় না। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুখ্যাতি দ্বারা নিজেদেরকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করা সহজ। উদাহরণস্বরূপ সিঙ্গাপুরের কথা বলা যায়। মাত্র ৬২৫ বর্গ কিলোমিটারের এ দেশটি এশিয়া তো বটেই বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনী দেশ হিসেবে স্বীকৃত। প্রতিবেশী বড় দেশগুলোর উদাহরণ টেনে সিঙ্গাপুরকে চিনাতে হয় না। নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিই এদেরকে এনে দিয়েছে পরিচিতি এবং সম্মান।
ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া ও ম্যারিল্যান্ড
গাড়ি ভার্জিনিয়ার প্রধান রাস্তা দিয়ে পেন্টাগনের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসি’র দিকে দ্রুত গতিতে ছুটে চলছে। একে তো ডিসি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের ক্যাপিটাল, তার ওপর আমাদের হোটেলে অবস্থান হোয়াইট হাউজের খুব কাছেই। মেরির কাছে হোটেলের অবস্থান জানার পর আমার অসম্ভব ভালো লাগছে।
পার্থ’র নিখোঁজ হওয়ার টেনশনে সুযোগ পায়নি বিধায় গাড়িতে বসে আমরা মেরির কাছে নিজেদের পরিচয় দিলাম। মেরি আগে স্টেটস ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো। এখন ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রামের আওতায় যারা আমেরিকায় আসে তাদের গাইড বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অফিসার হিসেবে কাজ করেন। দায়িত্ব একই, তবে গাইডের পরিবর্তে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অফিসার বললে শুনতে ভালো লাগে।
মেরির নিজের আবাস হচ্ছে মিনোসোটা। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিম প্রান্তে। বয়স ষাটের কাছাকাছি, তবে দেখলে মনে হয় সে এখনও বেশ সক্ষম ও সক্রিয়। কথাবার্তায় ভীষণ স্মাট। আলাপ চারিতায় জানলাম ওর লেখাপড়ার প্রতি এখনও প্রচুর আগ্রহ আছে। ইউএফও বা আন আইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্টের ওপর তার গবেষণার ইচ্ছে আছে বলে জানালো। বাংলাদেশে ইউএফও দেখা যায় কিনা তা মেরি আমার কাছে জানতে চাইলো। ইউএফও বিষয়টি যে এখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আমার কাছে স্রেফ গুজব বা ফালতু একটি বিষয় তা বললাম না। বললে তার উৎসাহে ভাটা পড়তো। আমেরিকানরা কল্পনা করতে ভালোবাসে। কল্পনার পাখা মেলতে মেলতে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে। মনে মনে ভাবলাম যে জাতি কল্পনা করতে জানে না তারা সামনে এগুতে পারে না। কল্পনায় না ভাসতে পারলেও সামান্য স্বার্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি করতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি না।
রাত বেশ গভীর, রাস্তা একেবারে শুনশান। ওয়াশিংটন ডিসি পৌঁছতে আরও বেশ কিছু সময় লাগবে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও কমে এসেছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কোন জায়গা সামনে পড়লে ড্রাইভার আমাদের তা দেখাচ্ছে এবং তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা তুলে ধরছে। আলো আধারীর কারণে ভালো মতো সব কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ‘সামনে পেন্টাগন সিটি’- ড্রাইভারের এ কথায় আমরা খানিকটা নড়ে চড়ে বসলাম। বর্তমান বিশ্বে যে সকল যুদ্ধ বা অপকর্ম ঘটছে তার প্রধান উৎস হিসেবে পেন্টাগনকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। পেন্টাগনের উপর এ কারণেই হয়তো ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এ হামলা হয়েছিল। তবে হামলায় পেন্টাগনের খুব বেশি ক্ষতি হয়নি।
আমরা যে সময় আমেরিকা সফর করছিলাম তখন পেন্টাগনের মেরামত কাজ প্রায় শেষ পর্যায়। এসব সিএনএন ও সিএনবিসি ইত্যাদি টেলিভিশন চ্যানেলে দেখছিলাম। পেন্টাগন সিটি পার হয়েই চলে আসলাম আরলিংটন নামক জায়গায়। এখানকার ওয়ার সিমেট্রি খুব বিখ্যাত। মেরি জানালো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত আমেরিকান সৈন্যদের এখানে সমাহিত করা হয়েছে। এসব নিহত সৈন্যদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ করা হয় এবং তাদের প্রতি সম্মান দেখানো হয়।
গাড়িতে থাকা অবস্থাতেই মেরি পরদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে আমাদের ব্রীফ করেছিলেন। জেটল্যাগ তথা ভ্রমণ ক্লান্তির কারণে পরদিনের কর্মসূচি ছিল খুবই হালকা পাতলা। কেবলমাত্র রাজধানী শহর ওয়াশিংটন ডিসি ঘুরে ঘুরে দেখা ছিল পরের দিনের প্রধান কাজ। তার পরদিন থেকেই শুরু হবে আসল কর্মকাণ্ড, প্রোগ্রাম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে দম ফেলার ফুসরত থাকবে না। মেরি আমাদের এ বিষয়টা বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল।
ড্রাইভার অনেকটা গাইডের সুরে জানালো সামনের মোড় ঘুরলেই হোয়াইট হাউজ, যদিও এগুলো জানানোর দায়িত্ব ছিল মেরির নিজের। ক্লান্তি আর ঘুমের টানে সে অনেকটা নিস্তেজ হয়ে আসছে। হোয়াইট হাউজ দেখার জন্য খানিকটা নড়ে চড়ে বসে প্রস্তুতি নিলাম। রাস্তা ফাঁকা থাকার কারণে খুব দ্রুত হোয়াইট হাউজের সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি টার্ন নিলো। এরই মধ্যে দেখলাম হোয়াইট হাউসের চারদিকে শশব্যস্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের পাদচারণা। ১১ সেপ্টেম্বরের পরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহুগুণে মজবুত করা হয়েছে। তবে প্রবাদ আছে বজ্র আঁটুনি ফসকা গিরা।
মনে পড়ে বেশ কয়েক বছর আগে সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থার চোখে ধুলো দিয়ে ছোট একটি প্লেন হোয়াইট হাউসের চত্বরে ঢুকে পড়েছিল। তবে চালক কেবলমাত্র ফান করার জন্য ঐ কর্মটি করে বসেন, কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়। আমেরিকানরা ফান করতে ভালোবাসে। ফান করতে করতে অন্যের বারোটা এরা বাজিয়ে দেয়। যেমনটি আমার সাথে হয়েছিলো পরবর্তী সময়ে কানসাস সিটিতে। কানসাস সিটির গল্প পরে বলবো। আর হ্যাঁ, হোয়াইট হাউজে অনুপ্রবেশকারীর ফানি আহাম্মক পাইলটের যে কি শাস্তি হয়েছিলো তা অবশ্য আমার জানা নেই।
কিছুক্ষণ বাদেই গাড়ি আমাদের হোটেলের সামনে এসে থামল। থমাস সার্কেলের পাশেই আমাদের হোটেল ‘হোমউড হিলটন’। খুব দামী এলাকায় হোটেলের অবস্থান। হোটেলের বেলকনিতে দাঁড়ালে হোয়াইট হাউজ, ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল এর বিশাল টাওয়ার, ইউএস ক্যাপিটাল (আমেরিকানদের সংসদ যেখানে পৃথিবীর অনেক দেশ এবং মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে মার্কিন সরকার) ইত্যাদি নজরে আসে। হোটেলটি নিঃসন্দেহে বিলাস বহুল বলা যায়। প্রত্যেকের জন্য পৃথক সুইট এর ব্যবস্থা। প্রতিদিনের জন্য ভাড়া তিনশ’ মার্কিন ডলার এর কাছাকাছি, সাথে থাকছে শুধুমাত্র সকালের নাস্তা। বাকী দুবেলা নিজের পয়সায় খেতে হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট এসব খরচ যোগাচ্ছে, এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা না করলেও চলবে।
আমাদের প্রতিটি সুইটে রয়েছে একটি মস্ত বেড রুম এবং একটি ড্রয়িং রুম। দু’রুমেই ওয়ালে টাঙ্গানো আছে দুটো বিশাল আকারের প্লাজমা টেলিভিশন। টেলিভিশনের সাথে কী-বোর্ড ইন্টারনেট সার্ফিং এর জন্য রাখা আছে। ড্রয়িং রুমে রয়েছে রান্না করার যাবতীয় উপকরণ ও ব্যবস্থা। তবে সময়ের স্বল্পতার কারণে রান্না খুব একটা করা হয়নি। এজন্য অবশ্য আফসোস হয়েছে পরে। টুক টাক রান্না করতে পারলে ম্যাগডোনালসের উপর আর অতিমাত্রায় নির্ভর করতে হতো না।
বিলাসবহুল হোটেল সুইটে প্রবেশ করার পর আমার কলেজ জীবনের কিছু স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এসএসসি পাশ করে ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছি মাত্র। লক্ষ্মীপুরে চাচার বাসায় থাকলাম দু’মাস। তারপর লেখাপড়ার বৃহত্তর স্বার্থে টেপাখোলা এলাকায় একটি মেস ভাড়া নিলাম। একরুমে তিনজন থাকতাম। কাঁচা ফ্লোর, উপরের টিন এবং বেড়া চাটাইয়ের। ভাড়া গুনতাম প্রতিমাসে মাত্র আশি টাকা। আর ওয়াশিংটন ডিসিতে এসে প্রতিদিন গুনছি চব্বিশ হাজার টাকা। একদিকে বিলাসিতা (তবে আমেরিকান সরকারের অর্থে), অন্যদিকে জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই, দুটো অবস্থাই আমার জীবনে এসেছে বলে দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলনা করতে সহজ হল। বিলাসিতায় আমেরিকানদের টাকা ওদেরকেই ফেরত দিচ্ছি বলে মনে খুব বেশি কষ্ট হল না। যেন নদীর জল নদীতেই ফেলছি। কষ্টটা কেবল সাময়িক বহনের।
ক্লান্তিতে সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। রুমে এসে যখন জামা কাপড় ছাড়লাম তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। ইচ্ছে হচ্ছিল থমাস সার্কেলের সামনে খানিকটা হাঁটাহাঁটি করে ডিসি শহরটা একটু দেখে নেই। শরীর সায় দিল না। হাতমুখে কোন রকম পানির ছিটা দিয়ে মখমলে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম ঘুমটা সকাল দশটা অব্ধি জারি থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। ঘুম ভাঙ্গল সকাল সাড়ে চারটায়। চারদিকে তখনও ঘোর অন্ধকার। ওয়াশিংটন ডিসি’র জ্বলজ্বল করা স্ট্রিট লাইটগুলো তার সাক্ষী দিচ্ছে।
মনে হল ক্ষুধায় পেটটা জ্বলে যাচ্ছে। ফ্লাইটের খাবার ছাড়া পথে আর কোন খাওয়া দাওয়া হয়নি। পেটটা বেজায় খাই খাই করছে। ক্ষুধার তাড়না হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। তিনশ’ ডলারে ভাড়ার বিছানায় শুয়ে আছি, কিন্তু ঘুম আসছে না। ঢাকা এবং ওয়াশিংটন ডিসি’র বারো ঘণ্টার সময়ের ব্যবধানের কারণে ঘুমে বেশ সমস্যা হচ্ছিল পুরো সফরকালে। দিনে ঘুম আসছিল চোখ ভরে, আর রাতে জেগে থাকার পালা। এ যেন এক উটকো ঝামেলা, যার থেকে সহজে বের হবার কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।
অগত্যা কিছু একটা খাবো বলে রুমের ফ্রিজটা খুললাম। এর মধ্যে পেলাম কিছু কুকিস, পানির বোতল আর কোক ক্যান। ফ্রিজে আরও কিছু দামী ওয়াইন এবং হুইস্কি দেখলাম। দামে তিনগুণ হলেও ক্ষুধার তাড়নায় হাপুস হুপুস করে কিছু কুকিস এবং পানি পেটে দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করার চেষ্টা করলাম, যদিও তা ক্ষুধার বিশালত্বের কাছে যথেষ্ট ছিল না। বিলের বিষয়টি ঐ মুহূর্তে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম।
সকালে নাস্তা করতে লবিতে নামতেই পার্থ’র সাথে দেখা। পার্থ সবসময় হাসিখুশি থাকে। কিন্তু মুখটা বেশ মলিন দেখায় প্রশ্ন করলাম-
কোন সমস্যা?
ভাই আমার ক্যামেরাটা পাচ্ছি না। আপনি কি এটি দেখেছেন? পার্থ’র পাল্টা প্রশ্ন আমার দিকে।
আমার মনে হল পার্থ ইমিগ্রেশন পার হয়ে আমার কাছে যে জিনিসগুলো দিয়েছিলো তার মধ্যে ক্যামেরা ছিল না। সান্তনা দিয়ে বললাম-
-ক্যামেরা কি খুব দামী?
উত্তরে যা বুঝলাম ক্যামেরা আহামরি দামী না। তবে এটি ওর স্ত্রীর ক্যামেরা বলে সমস্যাটা হয়েছে। ক্যামেরা দেয়ার সময়ই বৌদি সাবধান করে দিয়েছিলো যত্নে রাখতে। কিন্তু আমেরিকার মাটিতে নামতেই ক্যামেরা খোয়া যাওয়াতে পার্থ সঙ্গত কারণে খুব আপসেট ছিল। বেচারা বউয়ের কাছে ঝাড়ি খাবে সে ভয়তেই এখন শঙ্কিত।
তবে কেন জানি আমার মনে হয়েছিলো ক্যামেরাটি পাওয়া যাবে। আমেরিকানরাও অন্তত পার্থ বাবু’র এ মামুলি ক্যামেরা মেরে দিবে না। এদের মান সম্মান বোধ বেশ টনটনে। সেপ্টেম্বর ১১ ঘটনার পর সৌদি যুবরাজ টুইন টাওয়ার পুনর্নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা দিতে চাইলে আমেরিকান সরকার তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। সৌদি যুবরাজ ভুলে গিয়েছিলেন ওরা মিসকিন জাতি নয়। কারো দান খয়রাত নেয়ার জন্য আমেরিকানরা মোটেই প্রস্তুত নয়। এরা অন্যকে করুণা করতে (সেই সাথে আপদ বিপদ দিতে) অভ্যস্ত, নিতে নয়।
এর মধ্যেই শহীদ এবং তারেক লবিতে এসে গেছে। আমরা একসঙ্গে নাস্তা করতে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম মেরি আমাদের সামনের টেবিলে নাস্তার বিশাল এক পাহাড় নিয়ে বসে আছে, বিশেষ কোন আইটেমের জন্য হয়তো সে তখনও অপেক্ষা করছে। পার্থ’র ক্যামেরা হারানোর বিষয়টি মেরিকে জানানো হল। মেরি তড়িৎ একশনে গেলেন। একেবারে ডাইরেক্ট একশন। আমেরিকানরা একশনে বিশ্বাসী, চাপাবাজিতে নয়।
প্রথমে চেষ্টা করা হল গত রাতের ভারতীয় পাঞ্জাবী জীপ ড্রাইভারের কাছে। তার কাছ থেকে ক্যামেরার খোঁজ পাওয়া গেল না। তারপর ফোন করা হল ডালাস ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে যেখানে পার্থকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিলো। যেখানে ক্যামেরার কোন হদিস মিলল না। আমার অবশ্য আস্থা অটুট ছিল ক্যামেরা ফেরত পাওয়া যাবে। ঠিক দুদিন পর আমার অনুমান সত্যি হল। ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে মেরিকে ফোন করে ক্যামেরা ফেরত নিতে বলল। ক্যামেরা ফেরত পাওয়াতে মেরি খুশি, পার্থ আনন্দে আটখানা আর আমরাও ক্যামেরা ফিরে পাবার খুশি সেলিব্রেট করার জন্য বিকেলে হোটেলের লবিতে আয়োজিত বৈকালিক হ্যাপি আওয়ারে মেরিসহ সকলে একসঙ্গে যোগ দিলাম।
সন্ধ্যায় হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটন শহরের সৌন্দর্য প্রাণভরে দেখলাম। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো চোখে পড়লো। হোটেলের এক পাশে থমাস সার্কেল, অন্য দিকে ডুপন্ট সার্কেল। এ রোডেই অবস্থিত আমেরিকান ইন্সটিটিউট অব ইকনোমিকস, জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অফিস, আমেরিকান পাইলটদের এসোসিয়েশনের অফিস, আরও অনেক কিছু। মেরি আমাদের জানালো আমেরিকান পাইলটদের এসোসিয়েশন খুব মজবুত একটি সংগঠন। ঐ সময় পাইলটরা প্লেনের ককপিটে আর্মস বহনের অনুমোদনের জন্য লবি করছিলো। তদবিরের আমেরিকান ভার্সন হচ্ছে লবি, এরাবিয়ানরা বলে ওয়াস্তা আর আমরা বলি তৈল মর্দন।
আমেরিকান লবিস্টদের নিয়ে একটি গল্পও প্রচলিত আছে যা মেরি আমাদের শোনালো। হোয়াইট হাউজের সামনে একটি বিখ্যাত হোটেল আছে। ঐ হোটেলে আমেরিকান প্রেসিডেন্টরা আসতেন মাঝে মধ্যে তাদের ভক্ত বা নেতা কর্মীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য। ক্রমান্বয়ে ঐ হোটেলটি হয়ে যায় লবিস্ট বা তদবির বাজদের আড্ডাখানা। ভালো লোকের সাথে খারাপ লোকেরাও প্রেসিডেন্টের কৃপা লাভের জন্য ঐ হোটেলে ভিড় জমাতে থাকে। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ঐ হোটেলে আসা বন্ধ করে দেন। প্রেসিডেন্ট হোটেলে আসা বন্ধ করলেও আমেরিকান লবিস্টদের সরকারের ওপর প্রভাব একটুও কমেনি। আমেরিকান অর্থনীতি থেকে শুরু করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে লবিস্টরা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।
মিসোনিয়ান মিউজিয়াম
হোয়াইট হাউজের ওয়াকিং ডিস্ট্যান্সের মধ্যে আছি, ভাবতেই আমার কাছে খুব অবাক লাগছে। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। আমি খুব সামান্য ঘটনাতেই বিস্মিত হই। স্বপ্ন পূরণের ঘটনাতো আকাশের মতো বিশাল বিস্ময়। পরদিন ছিল একদম ফ্রি ডে। পূর্ব নির্ধারিত কোন কোন ভিজিট ছিল না। মেরি প্রস্তাব করলো হোটেলের খুব কাছেই অবস্থিত স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম ঘুরে দেখে আসার জন্য। খুব বিখ্যাত মিউজিয়াম এটি। আমেরিকানরা একে ডাকেন মিসোনিয়ান মিউজিয়াম হিসেবে। বানান এবং উচ্চারণে এ অদ্ভুত বিসদৃশতার হেতু জানতে চাইলাম মেরির কাছে। মেরি কোন সদুত্তর দিতে পারলো না, কেবল মৃদু হাসল। এ নিয়ে অবশ্য ওর সাথে আর কথা বাড়ায়নি। দুনিয়ার সব জায়গাতেই বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম বিষয় থাকে। এটিও তার মধ্যে একটি।
মেরির বর্ণনা থেকে জানা গেল ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত মিস্টার স্মিথসোনিয়ান ছিলেন খুব হত দরিদ্র একজন মানুষ। দু’বেলা ভালোমতো খেতে পারতেন না। নিজের চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থের মালিক হন। পরিবার পরিজন না থাকায় জমা কৃত অর্থ দিয়ে মিউজিয়ামটি তৈরি শুরু করেন। পরে আমেরিকান সরকার এর পূর্ণতা দান করেন। এই মিউজিয়ামেই চিত্রায়িত হয় বিখ্যাত হলিউড ছবি ‘নাইট এট দ্য মিউজিয়াম’। ছবিতে দেখানো হয় রাতে ডাইনোসরসহ মিউজিয়ামের বিভিন্ন কংকাল জীবন্ত হয়ে উঠে এবং তারা বিভিন্ন কীর্তিকলাপ করতে থাকে।
আমেরিকানরা মিসোনিয়ান মিউজিয়াম বললেও এর অফিসিয়াল নাম ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি যার পরিচালনা করেন ওয়াশিংটন ডিসি’র স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট। এতে প্রবেশের জন্য কোন ফি’র প্রয়োজন হয় না। এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান মিউজিয়াম যেখানে সব ধরনের দর্শকরা ভিড় করেন। ১৯১০ সালে মিউজিয়ামটি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এর প্রধান ভবনের আয়তন ১,৩২০,০০০ বর্গফুট যার মধ্যে দর্শনীয় বস্তুগুলো দখল করে আছে ৩৫০,০০০ বর্গফুট। এখানে রয়েছে ১২৬ মিলিয়ন বা বার কোটি ষাট লক্ষ দর্শনীয় বস্তু যার মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদ, প্রাণী, ফসিল, মিনারেল, পাথর, মহাকাশ থেকে ছুটে আসা মেট্যরাইটস, মানুষের ধ্বংসাবশেষ, আদিযুগের জিনিসপত্র ইত্যাদি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন পুরো মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে কয়েক দিনের প্রয়োজন হয়, যদিও আমাদের হাতে ঐ পরিমাণ সময় ছিল না।
মিসোনিয়ান মিউজিয়াম দেখতে আমরা যেদিন যাই ঐ দিন ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। এ কারণেই মিউজিয়াম এর প্রতিটি গ্যালারী ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। ডায়নোসারের বিশাল স্ক্যালাটন এবং এর কৃত্রিম হুঙ্কার বেশ উপভোগ্য। বাচ্চারা বেশি পছন্দ করে এগুলো। এছাড়া বিভিন্ন এক্সিবিট এর মাধ্যমে আমেরিকার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ইনোভেশন এর কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। শুনেছি ফ্রি বলতে আমেরিকাতে কিছু নেই। তবে মিসোনিয়ান মিউজিয়াম ঘুরে দেখতে কোন ডলার লাগলো না। শিক্ষার সাথে এ বিষয়টি জড়িত বলে এ ব্যবস্থা।
মিসোনিয়ানমিউজিয়ামে আবার বিশেষ আকর্ষণ ছিল In quest of Eternal Soul নামক ভবনটি। এখানে মিশরীয় রাজাদের কিছু মমি রাখা আছে। এ ভবনটিতে দেখলাম উপচে পড়া ভিড়। Eternal Soul খুঁজতে সব শ্রেণির সব বয়সের দর্শনার্থীরা এখানে ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে আসেন। ভিড়ের পরিমাণ এতো ব্যাপক যে আমরা আর মমির কাছে ভিড়তে পারলাম না। মমিকে নিরাপদ দূর থেকেই এক নজর দেখলাম। মমি’র রাজার প্রতি যথাযথ সম্মান জানালো হল কিনা কে জানে। ভিড় দেখে ইটারনাল সোল না খুঁজে আমরা বাইরে আসার রাস্তা খুঁজতে লাগলাম।
মিউজিয়ামের খুব কাজেই বিশাল স্তম্ভ আকারে ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল। ক্যাপিটাল হিল, হোয়াইট হাউজ আর ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল যেন সারা আমেরিকাকে উপস্থাপন করে। যারা বিবিসি, সিএনএন বা আল-জাজিরা টিভি চ্যানেল দেখেন তারা হয়তো লক্ষ্য করবেন আমেরিকা সম্পর্কে কোন সংবাদ বা ফিচার প্রচার করা হলেই সংবাদ পাঠকের পিছনে ঐ সিম্বলগুলো তুলে ধরা হয়। ভিয়েতনাম মেমোরিয়ালের অদূরে অবস্থিত কোরিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল। এখানে দেখা যায় কোরিয়াতে যুদ্ধরত মার্কিন সেনাদের ডামি। কবরের উপর সৈন্যদের ডামি অস্ত্র উঁচিয়ে যুদ্ধের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।
মেমোরিয়ালগুলোর মাঝখান দিয়ে বইছে দৃষ্টিনন্দন লেক। লেকের পশ্চিম পাশে রয়েছে বিখ্যাত লিঙ্কন মেমোরিয়াল। শত শত দর্শনার্থী প্রতিদিন লিঙ্কন মেমোরিয়াল দেখার জন্য ভিড় করে। আমরাও লিঙ্কন মেমোরিয়াল এর ভিতর এবং এর চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অনেক হলিউড সিনেমায় উপজীব্য হিসেবে বিভিন্নভাবে বিখ্যাত এ লিঙ্কন মেমোরিয়াল উপস্থাপন করা হয়। আমেরিকার চুয়াল্লিশ জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন বিখ্যাত হয়ে আছেন, তেমনি খ্যাতি পেয়েছে মেমোরিয়ালের অভ্যন্তরে রাখা লিঙ্কনের মূর্তিটিও।
লিঙ্কন মেমোরিয়ালের ঠিক পিছনে কুল কুল ধারায় বইছে পোটোম্যাক নদী। নদীর ওপারেই ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্য। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে আমেরিকানদের পূর্বসূরিরা ভার্জিনিয়ায় প্রথমে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ব্রিটিশরা জেমসটাউন নামে প্রথম শহরটি এ রাজ্যেই গড়ে তোলে। ভার্জিনিয়া থেকে এরা পর্যায়ক্রমে পশ্চিমের দিকে যেতে থাকে বিভিন্ন রিসোর্স বা সম্পদের সন্ধানে। এরা যেমন ভারত উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া নামে বাণিজ্য শুরু করেছিল, ঠিক তেমনি আমেরিকাতে ভার্জিনিয়া কোম্পানি নামে প্রাথমিকভাবে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে।
ব্যবসার অন্তরালে ব্রিটিশদের মনে আমেরিকা নামের বিশাল ভূখণ্ড জয়ের দুরভিসন্ধি ছিল। ঠিক যেমনটি এরা করেছিলো পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশ গ্রাসের নীল নকশা। ব্রিটিশরা উভয়ক্ষেত্রেই আশাতীতভাবে সফল হয়েছিলো। পটোম্যাক নদীর ঠিক ওপার থেকে ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে প্রতি মুহূর্তে বিমান উড্ডয়ন এবং ল্যান্ডিং এর প্রচণ্ড- শব্দ ভেসে আসছিল। এ বিমান বন্দর থেকেই ৯/১১ এ একটি বিমান ছিনতাই করে তা দিয়ে পেন্টাগনে আঘাত হানা হয়।
আমার কাছে মনে হয়েছে আমেরিকানরা প্রচণ্ড ব্যস্ত একটি জাতি। পুরো দেশটাই যেন একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। সবাই ছুটছে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্য প্রতিযোগিতা প্রবল। সকালে কোন রকম নাস্তা সেরে চা বা কফি’র কাপ হাতে নিয়েই ছুটছেন কর্মস্থলের দিকে। আমাদের সাথে আমেরিকানদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে আমরা একে অপরের সমালোচনায় ব্যস্ত। আর ওরা সমালোচনার পরিবর্তে কাজে বিশ্বাসী। সমালোচনা বা ব্যাক বাইটিং আমাদের সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে গেছে। নিজেরা কিছুতো করবোই না, বরং অন্যরা কিছু করলে তার খুঁত ধরতে আদাজল খেয়ে লেগে যাই। কেউ এগিয়ে যাইতে চাইলে তাকে পেছন থেকে টেনে ধরি। এসব বিষয় নিয়ে অনেক গল্প কাহিনী রয়েছে যেগুলো আমাদের প্রায় সকলেরই জানা।
মেরিডিয়ান সেন্টার ও বাল্টিমোর
সফরের তৃতীয় দিন মেরি আমাদের সকালের নাস্তার পর পরই ইন্টারন্যাশনাল মেরিডিয়ান সেন্টার নিয়ে গেল। ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষে এরা আমাদের সফরের যাবতীয় বিষয়াদি সমন্বয় করছিলো। আমার মনে হল আমেরিকান সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি এ ধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। সরকারের কাজে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়।
আমাদের হোটেলের খুব কাছেই মেরিডিয়ান সেন্টারের অবস্থান। সেন্টারটি যে ভবনে অবস্থিত সেটি খুব বিখ্যাত একটি স্থাপনা। আমেরিকার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট এ ভবন থেকে যাত্রা শুরু করে। নানা ধরনের লতা পাতা আর ফুল গাছে মোড়া দ্বিতল এ ভবনটি। নির্ধারিত সময়ে আমরা একটি ট্যাক্সি ক্যাবে করে মেরিডিয়ান সেন্টারে উপস্থিত হলাম। রিসিপশন পার হতেই অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় ‘শুভ সকাল, ভালো আছেন তো?’ বলে স্বাগত জানালো। পাশ থেকে মাঝ বয়সী আরেকজন সহাস্যে বলে উঠলো ‘হি ইজ মিস্টার পিটার, এ ম্যান ফ্রম কুষ্টিয়া’।
ওয়াশিংটন ডিসি’র বাসিন্দা পিটার একসময় যুক্তরাষ্ট্রের দাতা সংস্থা ইউএসএআইডি’র স্টাফ হিসেবে কুষ্টিয়ায় দীর্ঘ দিন কাজ করেছে। বাংলাদেশে অবস্থান করার সুবাদে বাংলা ভাষা রপ্ত করেছে সে। মেরিডিয়ান সেন্টারে পিটারের সাথে আমাদের কথাবার্তা এরপর বাংলাতেই চলল। মনে হল সহস্র মাইল দূরে এসে একজন স্বদেশী পেয়েছি। বাংলাদেশ কানেকশনের কারণে হয়তো আমাদের খোঁজ খবর পিটার একটু বেশি রাখতো। আমেরিকাতে আমাদের গ্রুপের অবস্থান যাতে আরামদায়ক এবং নিরাপদ হয় সে বিষয়ে পিটারের প্রচেষ্টা অন্যান্যদের চাইতে একটু বেশি ছিল বলে আমার মনে হল।
আপ্যায়ন শেষে আমাদেরকে মিটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হলাম। সেন্টার প্রধান মিসেস লোরা আমাদের সফরের উদ্দেশ্যসহ করণীয় বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন। ব্রিফিং এর পর আমরা রওনা হলাম বাল্টিমোরের উদ্দেশ্যে। আয়তনে মেগা শহর না হলেও বাল্টিমোর বিভিন্ন দিক থেকে আমেরিকার বিশেষ শহর হিসেবে পরিচিত।
সফরের নিয়ম ছিল সিটির মধ্যে যাতায়াত ভাড়া আমরা মেরির সাথে শেয়ার করবো। তবে লম্বা পথের যাত্রায় আমরা পকেট থেকে কোন পয়সা খরচ করতে হবে না। স্টেটস ডিপার্টমেন্ট এর দায়িত্ব নিবে। মেরি গাড়ি ভাড়া করে নিজেই ড্রাইভ করেছে ডিসি থেকে বাল্টিমোরের পথে। বয়সে ষাটের কাছাকাছি হলেও মেরি অত্যন্ত সাবলীলভাবে গাড়ি চালিয়েছে। কোথাও তেমন কোন অঘটন ঘটেনি। তবে বাল্টিমোর থেকে ফেরার পথে একটি অঘটন প্রায় ঘটতেই যাচ্ছিল। আমেরিকার সকল গাড়ি লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ। অর্থাৎ ড্রাইভার সামনে বাম সিটে বসেন, চলে রাস্তার ডান ধার ধরে। আমাদের দেশে ড্রাইভার বসে ডান দিকে, চলে রাস্তার বাম দিক দিয়ে।
সময় সংকুলানের জন্য মেরি বেশ দ্রুততার সাথে গাড়ি চালাচ্ছিল। সামনের ডান দিকে আমি বসেছিলাম। পিছনে তারেক, পার্থ আর শহীদ। কিছুদূর আসার পর দেখলাম রাস্তার পাশে একটি সামান্য উঁচু জায়গার অনেকগুলো ফুলের মালা রাখা হয়েছে। এর হেতু জানতে চাইলে মেরি জানালো এ রাস্তায় গত এক বছর আগে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় কয়েকজন মারা যায়। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই স্বজনেরা ফুলের মালা দিয়ে নিহতদের স্মরণ করেছে। মেরি আরও জানালো এ রাস্তাটি বেশ বিপদজনক। মনে মনে বললাম, বাল্টিমোর টু ডিসি আবার আমাদের ঢাকা আরিচা রোড তো নয়!
আর একটু সামনে যেতেই দেখলাম রাস্তার দু’পাশেই বেশ জঙ্গল, আর জঙ্গলের মাঝ দিয়ে কুল কুল ধারায় বইছে ছোট আকারে নদী। পানি অত্যন্ত পরিষ্কার, মনে হল ছোট ছোট মাছ এতে কিলবিল করছে। মাছের পরিবর্তে এগুলো পোকাও হতে পারে। খুব কাছ থেকে নদীটি দেখতে ইচ্ছে হল। কিন্তু মেরির অনুমোদন মিলল না। এটি দেখে কবিগুরুর লেখা ‘আমাদের ছোট নদী’র কথা মনে পড়লো। নদী, সাগর আর বৃষ্টি’র প্রতি আমার দুর্বলতা আজন্ম থেকে।
মেরির ড্রাইভিং এর ওপর আমাদের সকলেরই গভীর আস্থা ছিল। পিছনের ছিটে ওরা তিনজন বেশ মজা করে গল্প করছে। গল্পের বিষয়বস্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু সামনের ছিটে বসার কারণে অংশ নিতে পারছিলাম না। আমার কাছে মনে হচ্ছিল মেরি মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি চালানোর সময় সে গতির বিষয়ে কোন প্রকার ইন্টারফেয়ার একদম পছন্দ করে না। মনে মনে শুধু বিড়বিড় করে বললাম, বুড়ি আস্তে চালাও, ভয় লাগছে ভীষণ….।
বলতে বলতেই সামনের একটি জীপকে ওভার টেক করতে গিয়ে দেখা গেলো বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতিতে একটি মাইক্রো বাস ছুটে আসছে। উভয় দিকের চালকের বিচক্ষণতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলো। গাড়ি থামিয়ে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে মেরি প্রথমে জীপ চালককে সরি বলল। জীপ চালক অনুরূপ ভদ্রতা দেখিয়ে বললেন, টেক কেয়ার..। এমন পরিস্থিতি আমাদের দেশে হলে কি হতো নিশ্চয় চিন্তা করতে পারছেন। চালক যতোই ভদ্রলোক হন না কেন তিনি অবলীলায় অন্য চালকের চৌদ্দ-গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়তেন। খিস্তি খিউড় তো বাড়তি বোনাস। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকার কথা নয়।
ওয়াশিংটন ডিসি থেকে বাল্টিমোর গাড়িতে প্রায় আড়াই ঘণ্টার পথ। ভারী সুন্দর এ শহরটি। আকারে খুব বেশি বড় নয়। বাল্টিমোর হারবার শুধু আমেরিকাতেই নয় সারা দুনিয়াতেই বিখ্যাত। এখানে বিশ্ববিখ্যাত জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ সায়েন্স এর ক্যাম্পাস অবস্থিত।
বাল্টিমোরো পৌঁছে বেশ ঝামেলায় পড়লাম। আমেরিকান হওয়া সত্ত্বেও মেরি এর আগে কখনো এ শহরে আসেনি। সে ঠিকানা ধরে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছে এসে পড়লেও সেটি সনাক্ত করতে পারছিল না। আমরা পুলিশের ও স্থানীয় জনতার সাহায্য নিলাম। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ভবনটিতে পৌঁছতে পারছিলাম না কোনভাবেই। মেরিকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। আগেই এপয়নমেন্ট করা ছিল। কোনক্রমে দেরি হলে ওরা মাইন্ড করবে। আমেরিকানরা দশটার মিটিং দশটাতেই শুরু করতে পছন্দ করে। কথা ও সময় রক্ষা করা ওদের সংস্কৃতি এবং ভদ্রতার অংশ। যাহোক শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে কাঁটায় কাঁটায় আমরা ওখানে পৌঁছলাম।
শহীদের টেলি মেডিসিনের ওপর বিশেষ আগ্রহ ছিল বিধায় ওর অনুরোধে মেরি এখানে আমাদের প্রোগ্রাম রেখেছিল। জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সফল করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও এ সংস্থাটি বেশ কয়েক বছর আগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করেছে। ভিজিটিং রুমে গিয়ে দেখলাম আফসানা মিমি’র ছবিসহ একটি পোস্টার শোভা পাচ্ছে। সহজেই বুঝতে পারলাম বাংলাদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জনপ্রিয় করার জন্য জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় যে নাটকটি জনপ্রিয় নির্মাতা হুমায়ুন আহমেদ তৈরি করেছিলেন এটি তারই পোস্টার। নাটকে অভিনেত্রী আফসানা মিমি পুষ্টি আপার অভিনয় করে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
বাল্টিমোর শহরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ শহরে গাছপালার সংখ্যা তুলনামূলক কম। প্রায় সবগুলো ভবনই মনে হল হাল আমলে তৈরি হয়েছে। আমরা সম্ভবত: শহরের নতুন এক্সটেনশন এলাকায় এসেছি। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে শহরটি অবস্থিত। স্বাধীন আমেরিকার প্রথম পতাকাটি যে স্থানে উড়ানো হয়েছিলো আমরা সে ভবনটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। হারবারে দেখা গেল বিশাল আকৃতির জাহাজগুলো নোঙ্গর করে আছে। জাহাজগুলো এতো বিশাল ছিল যে এগুলোকে মনে হলে এক একটি আকাশচুম্বী অট্টালিকা। জনহপকিন্স ছাড়াও এখানে আরও বেশ কতকগুলো প্রসিদ্ধ হাসপাতাল রয়েছে। এর একটিতেই ভারতের মাস্টার ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকারের পায়ের গোড়ালির অস্ত্রোপচার হয় বলে মনে পড়ে। খুব স্বল্প সময় অবস্থান করলেই মেরিল্যান্ডের এ শহরটি আমার মনে বেশ দাগ কেটেছে।
ইউএস ক্যাপিটাল ও সিনেটর বব ক্লিমেন্ট
হোয়াইট হাউজের খুব কাছেই ইউএস ক্যাপিটাল এর অবস্থান। ইউএস ক্যাপিটালে বসেই কংগ্রেস ম্যান এবং সিনেটররা আমেরিকার জনগণের পাশাপাশি দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে। ইউএস ক্যাপিটাল আমাদের জাতীয় সংসদের ভার্সন। উপরিভাগে বিশাল গম্বুজসহ দৃষ্টিনন্দন সুরম্য ভবন এটি। এ ভবনটির প্রতিকৃতি আমেরিকান সংবাদের সাথে প্রায়ই বিবিসি ও আল-জাজিরা টিভি চ্যানেলে দেখা যায়। কঠিন তল্লাশি শেষ করে আমরা দলবলসহ ভবনটিতে প্রবেশ করলাম। মেরিও তল্লাশি থেকে বাদ পড়লো না।
ক্যাপিটাল ভবনের ভিতরে হাঁটতে থাকলে কিছুদূর পর পরই দেখা যায় প্রাক্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের প্রতিকৃতি। ইউএস ক্যাপিটালের ঠিক মাঝখানে বিশাল আকৃতির গম্বুজটির অবস্থান। আমাদের দেশেও ব্রিটিশ আমলের কিছু ভবনে এ ধরনের গম্বুজ চোখে পড়ে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে গম্বুজের ঠিক নিচে একটি জায়গা আছে যেখানে দু’জন লোক সামন্তরালে বেশ দূরে দাঁড়িয়েও কানে কানে কথা বলতে পারে। আমরা সকলেই কান কথা বলার এ বিষয়টি বেশ উপভোগ করলাম। ইউএস ক্যাপিটালে টেনিসিস থেকে নির্বাচিত সিনেটর বব ক্লিমেন্ট এর অফিসে এবং এখানকার বাংলাদেশ ককাসে আমাদের পূর্বনির্ধারিত সভা ছিল। মেরি এগুলো আগে থেকেই ব্যবস্থা করেছিলো।
সিনেটররা বছরের এ সময় ভীষণ ব্যস্ত ছিলেন সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিতর্কে। কংগ্রেসে নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায় বব ক্লিমেন্টের সাথে দেখা হল না। এজন্য সিনেটর সাহেবের পার্সোনাল এসিস্টেন্ট মিস সুজান আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তবে সান্ত্বনা হিসেবে তিনি আমাদেরকে ইউএস ক্যাপিটালের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখানোর আশ্বাস দিলেন। বব ক্লিমেন্টের অফিসে এসে জানতে পারলাম প্রত্যেক আমেরিকান সিনেটর ও কংগ্রেস ম্যানের একজন করে এটর্নি বা আইনজীবী রয়েছে। আমেরিকান ল’মেকাররা যাতে ফালতু বা অহেতুক কথা না বলতে পারে সেজন্য এটর্নিরা তাদের বক্তব্য কাঁটা ছেড়া করে পরিমার্জন করেন। অহেতুক ঝামেলা সৃষ্টি থেকে রাজনীতিবিদদের বিরত রাখতে এটি একটি উত্তম ব্যবস্থা বলে মনে হয়েছে।
উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছিল সিনেটর সাহেবের অফিসে। এপয়েনমেন্ট বাতিল করার কারণে হয়তো ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাড়তি কিছু আয়োজন ছিল। চা-নাস্তা পর্ব শেষে সুজান ক্যাপিটাল ট্যুর শুরু করলো। ঘুরতে ঘুরতে অল্প সময়েই ওর সাথে আমার বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে তারেক আমার সাথে রসিকতা করা শুরু করলো। সুজানের সাথে আমার যুগলবন্দী কিছু ছবি তিনি ক্যামেরা বন্দী করলেন, তবে সেগুলোর প্রিন্ট কপি আর পাওয়া যায়নি।
সুজান বিশ বাইশ বছরের একজন টগবগে তরুণী। দেখলে মনে হয় আইরিশদের বংশধর। টেনেসিস থেকে আইন বিষয়ে গ্রাজুয়েশন শেষ করে সিনেটরের পার্সোনাল এসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করছে। কথা প্রসঙ্গে সে নিজের বিষয়ে আমাকে অনেক কিছু বলল যদিও তা ছিল আমার প্রত্যাশার বাইরে। সুজান বিয়ে শাদী এখনও করেনি, কমিটেড কোন বয় ফ্রেন্ডও নেই। ভালো কোন চাকরির খোঁজ সে করছে। আমেরিকাতে স্থায়ী চাকরির সুযোগ খুব সীমিত। স্থায়ী চাকরির জন্য দেখলাম সুজানের তীব্র বাসনা আছে। সিনেটরের মেয়াদ চার বছর। বব ক্লিমেন্টের মেয়াদ সমাপ্তির সাথে সাথে সুজানের চাকরির মেয়াদ শেষ হবে।
আলাপের এক পর্যায়ে সুজানকে জানালাম প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে আমি সরকারি চাকরি করতে পারবো। আমার চাকরি স্থায়ী, ভয়াবহ কিছু না ঘটলে সহজে চলে যাবার সুযোগ কম। আমার চাকরির স্থায়িত্বের বিষয়টা জেনে সুজান বেশ অবাক হল। আমি বললাম স্থায়ী চাকরির কতকগুলো নেগেটিভ দিকও আছে। সহজে চাকরি হারানোর ভয় থাকে না বটে, কিন্তু কাজকর্মে অনেক সময় গতিশীলতা হারিয়ে যায় এবং তা কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। এছাড়া স্থায়ী চাকরিতে বেতনও কম। মনে মনে বললাম কেবলমাত্র দুর্বলেরাই স্থায়ী চাকরি খোঁজে। যোগ্য লোকেরা চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করে। চাকরির স্থায়িত্ব তাদের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় নয়। নিজেদের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানে তাদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে।
আলাপের এক পর্যায়ে সুজান জানালো ডিসিতে সে তার এক চাচার সঙ্গে থাকে। বিয়ে শাদী নিয়ে তার মা-বাবা বেশ চিন্তিত। পৃথিবীর সব দেশের মা-বাবাই মনে হয় তার বিবাহযোগ্য মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে। সুজানের কথাও সেরকমই একটু আভাস আমি পেলাম। বাইরে থেকে যে আমেরিকানদের আমি চিন্তা করেছি সুজানের মতো বাস্তব আমেরিকানদের সঙ্গে তা মেলাতে বেশ কষ্টই হচ্ছে। আমরা শুনি আঠার বছর হলেই পশ্চিমা দেশের ছেলে মেয়েরা নিজের মতো করে চলতে পারে। ওদের কাছে মা-বাবার মতামত গৌণ। কিন্তু সুজানের মতো গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের সন্তানদের ক্ষেত্রে এ নিয়মের হয়তো ব্যতিক্রম আছে।
আমরা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হাঁটাহাঁটি করে ইউএস ক্যাপিটালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখে নিলাম। এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে গেলে ক্যাপিটালের ক্যাফেটেরিয়াতে লাঞ্চ করতে গেলাম। সুজানকেও আমাদের সাথে অংশ নিতে অনুরোধ করলাম। বাসা থেকে নিজের লাঞ্চ নিয়ে আসছে বলে প্রথমদিকে রাজী হচ্ছিল না। শেষমেশ আমাদের পীড়াপীড়িতে অংশ নিতে রাজী হল। সুজানের বাসা থেকে লাঞ্চ বক্স নিয়ে আসার বিষয়টিও আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হল না। এ নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও তা করা হল না। এটা ওর ব্যক্তিগত বিষয়। কারণে অকারণে চারজনের মধ্যে আমার সাথেই সুজানের কথাবার্তা বেশি হচ্ছে। বিষয়টি আমার সফরসঙ্গীরা বেশ উপভোগ করতে লাগলো।
সুজানের দেখলাম দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর রাজনীতি নিয়ে বেশ আগ্রহ রয়েছে। কোথায় কী ঘটছে সে বিষয়ে আপডেটেড খবর তার কাছে রয়েছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে কাজটি অনেক সহজ হয়ে গেছে। ইউএস ক্যাপিটাল থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় সুজান জানতে চাইলো আমরা কোন হোটেলে আছি। আমি হোটেলের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দিয়ে আসলাম। একই সাথে দু’জনের ই-মেইল এড্রেসও বিনিময় করলাম।
আমাকে অবাক করে দিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় সুজান হোটেলে এসে হাজির। রিসিপশন থেকে আমাকে ফোনে ওর উপস্থিতি জানালো হল। বাকীদের না জানিয়ে চুপি চুপি লবিতে নেমে আসলাম। মনে হল ও শুধু আমার সাথে কথা বলতে চায়। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল বিধায় লবিতেই কফি খেতে খেতে সুজানের সাথে আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হল। বাংলাদেশ বন্যা, সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এখনও আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে আছে এরকম ধারণা ওর। বাংলাদেশে হরতাল, রাজনৈতিক অস্থিরতা বিষয়গুলো দেখলাম তার বেশ জানা রয়েছে।
আলাপচারিতার মাঝে আমি তাকে জানালাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়মিত বিষয় হলেও বাংলাদেশ অনেক দিক থেকে অত্যন্ত রিসোর্স ফুল। দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে যা দুনিয়ার খুব কম দেশেই পাওয়া যায়। প্রকৃতির বৈরিতার সাথে মোকাবেলা করে আমরা দ্রুত সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এ কথা ওকে ভালো করে বুঝাতে পারলাম। একইসাথে সুজানের সামনে আমাদের বেশ কিছু অগ্রগতির উদাহরণ তুলে ধরলাম।
আমাদের সাক্ষরতার হার বাড়ছে, শিশু ও প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার কমছে, রাস্তা ঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে, মাথাপিছু আয় বাড়ছে, টেলি-ডেনসিটি বেড়েছে নাটকীয়ভাবে, ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ব্যবহারে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। আমার ভালো লাগলো ওকে আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা দিতে পেরেছি। সুজান হোটেল থেকে চলে যাওয়ার পর মনে হল আমার সাথে ওর হঠাৎ সাক্ষাতের বিষয়টি কী নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, নাকি সিনেটরের অফিস থেকে এটি ছিল ওর অফিসিয়াল এসাইনমেন্ট!
সাদ্দামকে শায়েস্তা করার বিষয়টি জায়েজ করার জন্য ইউএস কংগ্রেস তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। জাতিসংঘের কোন ধার ধারছে না মার্কিন সরকার। যুদ্ধে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে টিভিতে সিনেটরদের বাক বিতণ্ডা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রেসিডেন্ট যুদ্ধে যেতে পারবে না। এ কারণে কংগ্রেসকে রাজী করার জন্য জোর তদবিরও চলছে। সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে অবসন্ন দেহে হোটেলে এসে টিভি চ্যানেলে এসব তর্ক বিতর্ক বেশ উপভোগ করতাম।
একদিন দেখলাম মাঝ বয়সী ম্যাক্সিকান (ম্যাক্সিকান আমেরিকানদের সাধারণত চুল কালো রংয়ের হয়ে থাকে, যদিও গায়ের রং ফকফকে সাদা) আমেরিকান মহিলা সিনেটর যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভীষণভাবে উত্তেজিত এবং ইমোশনাল হয়ে পড়েছেন। এক পর্যায়ে তিনি উত্তেজনার বিস্ফোরণ ঘটালেন এবং ইংরেজি ত্যাগ করে স্প্যানিশ ভাষায় বক্তৃতা দেয়া শুরু করলেন। টিভি চ্যানেল ক্ষুব্ধ সিনেটরের বক্তব্য নন-স্প্যানিশ দর্শকদের বুঝার সুবিধার্থে ইংরেজিতে তরজমা করে টাইটেল আকারে প্রদর্শন করলো।
সিনেটরের বক্তৃতার সারকথা আমার কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তাহলো-শক্তি দিয়ে সন্ত্রাস বিশ্বের বুক থেকে নির্মূল করা যাবে না। সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য এর কারণগুলো আগে চিহ্নিত করতে হবে, তারপর সেগুলো সমাধানে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। ক্ষুধা, অশিক্ষা, বৈরি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সন্ত্রাসের মূল কারণ হিসেবে সিনেটর তার বক্তৃতায় চিহ্নিত করলেন। তার এ কথাগুলো যে মহা সত্যি তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।
ইউএস কংগ্রেসের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ঐ সময়ে কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল সিনিয়র বুশের মতো জুনিয়র বুশও যুদ্ধে নামবেন। বিরোধী সিনেটরদের শত শত ভালো কথা আর যুক্ত তর্ক তাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। এর কয়েক মাস পরই আমার অনুমান সত্যি হল। মেরি অত্যন্ত কঠিন টাইপের রিপাবলিকান সাপোর্টর। সরাসরি না বললেও তার বিভিন্ন কার্যকলাপে এর প্রমাণ পেলাম।
মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন
ওয়াশিংটন ডিসি’র খুব কাছেই মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এটি একটি। পাতাল রেলে চেপে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মেরিল্যান্ড রেল স্টেশনে। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসে করে যেতে হল মূল ক্যাম্পাসে। বাসে কোন ভাড়া লাগে না। ছাত্র-ছাত্রী এবং ভিজিটরদের সুবিধার্থে এ ব্যবস্থা। মনোরম ক্যাম্পাস এটি। ছোট ছোট টিলা বেষ্টিত চারদিকে সবুজে মোড়া ভবনগুলো।
আমাদের পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউটের পরিচালকের সাথে। পরিচালক প্রফেসর ভ্যান বাস্টেন আমার পূর্ব পরিচিত। ঢাকাতে বাস্টেন এসেছিলেন ‘আইরিশ’ প্রকল্পের প্রতিনিধি হিসেবে। আইরিশ প্রকল্প বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তথ্য প্রযুক্তি প্রসার সংক্রান্ত আইন বা নীতিমালা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। আমি প্রফেসর বাস্টেনের সাথে ঢাকায় কাজ করেছিলাম তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে। ঢাকাতে এ বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপও হয়েছিল যেখানে বাস্টেন উপস্থিত ছিল। এসব কারণে মেরিল্যান্ড ক্যাম্পাসে তার সাথে দেখা পাওয়াটা আমার জন্য বিশেষ আনন্দের ছিল।
যথাসময়ে আমরা প্রফেসর বাস্টেনের অফিসে পৌঁছে গেলাম। মেরি নাম থেকেই আন্দাজ করেছিল প্রফেসর সাহেব একজন ডাচ আমেরিকান। অবশ্য এ বিষয়ে আমার কোন বাড়তি কৌতূহল ছিল না। কারণ, আমেরিকান মানে আমেরিকান। তাদের পূর্ব পুরুষ কোন দেশের তা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে লাভ কী। সকল আমেরিকানই কোন না কোন পর্যায়ে অভিবাসী হিসেবে এদেশে এসেছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। প্রফেসর বাস্টেন আমাদের বেশ আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানালেন।
দেখলাম তার সাথে বেশ কয়েকজন ভারতীয় এবং শ্রীলঙ্কান শিক্ষার্থী গবেষণার কাজ করছে। প্রফেসর বাস্টেন আইরিশ প্রকল্পের বিভিন্ন দিক আমাদেরকে ব্যাখ্যা করলেন। সভার শেষে তিনি হালকা আপ্যায়নও করালেন, তবে সেটা আমাদের অতিথি আপ্যায়ন সংস্কৃতির কাজে একবারেই নস্যি। আমেরিকার যত জায়গাতেই গিয়েছি সব জায়গাতেই আপ্যায়ন ছিল হালকা প্রকৃতির। আমাদের মতো ওরা অতিথিদের ভুঁড়ি ভোজ করানোর সাথে অভ্যস্ত নয়। প্রফেসর বাস্টেনের অফিসে আমাদের কাজ শেষে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সকলে মিলে পরিদর্শনে বের হয়ে গেলাম।
মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি বিশাল। হেঁটে এক ভবন থেকে আরেক ভবনে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এর মধ্যেই দুপুরের খাবারের সময় হয়ে গেল। সবার সম্মতিক্রমে মেরিসহ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে ঢুকে পড়লাম। খাবারের জন্য আমাদের মাত্র ত্রিশ মিনিট সময় বেঁধে দিলো মেরি। আমরা চটপট খেয়ে নিলাম। খাওয়ার সাথে সাথে উপভোগ করলাম ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ ও গান, যা ছিল একদম ফ্রি। ক্যান্টিনের এক পাশে মঞ্চ রয়েছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পছন্দমতো সময়ে এসে গান নাচ পরিবেশন করে। বলা যায় অনেকটা মুক্ত মঞ্চের মতো। কারও ইচ্ছে হচ্ছে দেখছে, অন্যরা নিজ মনে খেয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।
এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মতে’র অমিল থাকলেও আমাদের মতো তা লাঠি, পিস্তল বা ককটেল এর মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ করে না। পড়াশুনাটাই এদের কাছে মুখ্য। এরা চার বছরের গ্রাজুয়েশন চার বছরেই শেষ করে, আট বছরে নয়। শিক্ষা জীবনে অতিরিক্ত সময় লাগায় আমাদের কী পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে তা কী কখনও কেউ হিসেব করে দেখেছে। কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরা এর যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পান। খুব কষ্ট হল এ ভেবে যে আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতিপয় ছাত্র নামধারী মাস্তানের কাছে জিম্মি। তবে সম্প্রতি সময়ে সেশনজট কমানোসহ সার্বিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সত্যিকারের জ্ঞান চর্চার উর্বর ভূমি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরের সময় দেখলাম বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী বৃষ্টিতে ভিজে যুদ্ধ বিরোধী মিছিল করছে। তবে এদের মিছিল বেশ শান্তিপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের মিছিলের মতো অতটা তপ্ত নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আকর্ষণীয় প্ল্যাকার্ড, তাতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ বিরোধী শ্লোগান লেখা আছে। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে ওদের সাথে ছবি তুললাম। এদের মধ্যে একজনের সাথে আমার তড়িৎ খানিকটা আলাপও হল। ছেলেটি ইসরাইলী ইহুদী। আরবদের সাথে এদের জন্ম জন্মান্তরের শত্রুতা থাকলেও এ ছেলেটি ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন চাচ্ছে না। সাদ্দামকে শায়েস্তা করলে ইসরাইলের লাভ। এ বোকা ইহুদী ছেলেটি বিষয়টি কেন বুঝতে পারছে না বা বুঝেও না বুঝার ভান করছে তা আমি মিলাতে পারলাম না। সব সমীকরণ হয়তো সব সময় মিলে না।
মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শান্তি মিছিলকে আমি ব্যবহার করলাম মেরিকে এক হাত নিতে। মেরিকে বললাম- ‘দেখ, খোদ তোমাদের দেশেই সাদ্দামের পক্ষে মিছিল, আর তোমাদের প্রেসিডেন্ট যাচ্ছে ওখানে যুদ্ধ করতে’। আমার কথায় মেরি সাময়িকভাবে হজম করলেও বিষয়টি যে খুব সহজভাবে নেয়নি তা ওর চোখমুখে ফুটে উঠলো। বিকেলে হোটেল রুমে বিশ্রাম নিচ্ছি এমন সময় মেরি ইন্টার কমে আমাকে ফোন করে লবিতে নামতে অনুরোধ করলো। ঐ সময় কোন নির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল না। তাই নিচে ডাকার হেতু মাথায় ঢুকল না। লবিতে এসে দেখলাম মেরি শুধু আমাকে আসতে বলেছে, অন্য কাউকে নয়। খুব স্পেশাল প্রোগ্রাম হয়তো!
নিচে নামতেই মেরি আমাকে ডুপন্ট সার্কেলে বিশেষ একটি ঘটনা দেখাতে নিয়ে গেল। এই প্রথমবার কোন কাজে মেরিকে অতি উৎসাহী মনে হল। হোটেল থেকে ডুপন্ট সার্কেল মাত্র তিন চার মিনিটের পথ। ওখানে গিয়ে দেখলাম বিশাল মিছিল। মিছিল সাদ্দামের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধে নামার সমর্থনে। মিছিলকারীদের দেখে সহজেই সনাক্ত করা যায়। এদের সিংহভাগ প্রবাসী ইরাকী। যাদের মধ্যে একটি বড় অংশ রয়েছে শিয়া ও কুর্দি ইরাকী। কুর্দিদের বহুদিন যাবত সাদ্দাম বিভিন্নভাবে দমিয়ে রেখেছে। সাদ্দামের হাতে নির্যাতিত হয়ে এরা দেশ ছেড়েছে।
কেউ হারিয়েছে স্বজন, ভিটে, মাটি বা মান সম্মান। এ দৃশ্য আমাকে দেখাতে পেরে মেরি ভীষণ খুশি ও তৃপ্ত হল। সকালে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত চিত্র যে এত অল্প সময়ে মেরি আমাকে উপহার দিতে পারবে তা হয়তো নিজেও সে জানতো না। একেই বলে টিট ফর ট্যাট। আমার কিছু বলার ছিল না। ওকে শুধুমাত্র অনুসরণ করলাম, বিনিময়ে পেলাম কমপ্লিমেন্টারী এক কাপ স্টারবাগ কফি। মেরি এই প্রথম আমাদের কারো জন্য নিজের ওয়ালেট থেকে পয়সা খরচ করলো!
আমেরিকা আসলেই এক অবাক দেশ। আমেরিকানরা নিজেদের সমালোচনা নিজেরাই আগে করে। নিজেদের ভুলগুলো নিজেরাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এরা কেউ রিপাবলিকান, আবার কেউ বা ডেমোক্রেট। কিন্তু তার আগে এরা আমেরিকান। দেশের স্বার্থে সকলে এক। জাতীয় স্বার্থে একবিন্দুও এরা কাউকে ছাড় দিবে না। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম বা গোত্রের লোকজন এখানে এসে এক অজানা যাদুর ছোঁয়ায় এক সূত্রে নিজেদেরকে গেঁথে খাঁটি আমেরিকান বনে যায়।
একটা জাতি হিসেবে এটি অনেক বড় পাওনা। সিমেন্টের মতো ঐক্য আর কমিটমেন্টের কারণে আমেরিকা সারা বিশ্বে এখনও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বহাল রেখেছে। তবে অনেক বোদ্ধা মনে করেন আমেরিকা তার এই প্রভাব খুব বেশি দিন ধরে রাখতে পারবে না। আমেরিকার খ্যাতনামা দার্শনিক এমআইটি’র প্রফেসর নোয়াম চমোস্কি এসব বোদ্ধাদের একজন।
আমেরিকার মাটিতে পা দিয়ে একটি বিষয় বেশ অবাক হয়ে দেখলাম। এখানকার শহরগুলোর প্রায় প্রতিটি অফিস ও আবাসিক ভবনে বিশাল আকৃতির আমেরিকান পতাকা টাঙ্গানো রয়েছে। ভাবলাম আমেরিকা হয়তো জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ কোন দিবস পালন করছে। কৌতূহল সামলাতে না পেরে বিশাল পতাকা টাঙ্গানোর হেতু মেরির কাছে জানতে চাইলাম। মেরি জানালো আমেরিকানরা সারা বছরই পতাকা টানিয়ে রাখে। পতাকা টানাতে বিশেষ কোন দিন বা দিবসের প্রয়োজন হয় না। এটি ওদের দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ মনে হল। পার্ট টাইম আমেরিকান বা দেশপ্রেমিক এরা নন।
দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল সফরের সময়ে দেখেছিলাম আমেরিকানদের এ পতাকা কালচার কোরিয়ানরাও বেশ ভালোমতো রপ্ত করে নিয়েছে। পতাকা সব সময় চোখের সামনে থাকলে দেশপ্রেম বাড়ে এমন একটি ধারণা থেকে হয়তো এ ধরনের কালচার গড়ে উঠেছে। আমরা অবশ্য ২৬ মার্চ এবং ১৬ ডিসেম্বর এর আগে পতাকা ফেরিওয়ালাকে বিভিন্ন সাইজের পতাকা বিক্রি করতে দেখি। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঐ দিবসগুলোতে আমাদের জাতীয় পতাকা শোভা পায়। পত্ পত্ শব্দে উড্ডীয়মান পতাকা দেখে আমরাও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হই একটি সোনার বাংলা গড়তে। জাতীয় পতাকার সাথে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশের একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে বলে আমার মনে হয়েছে।