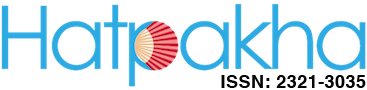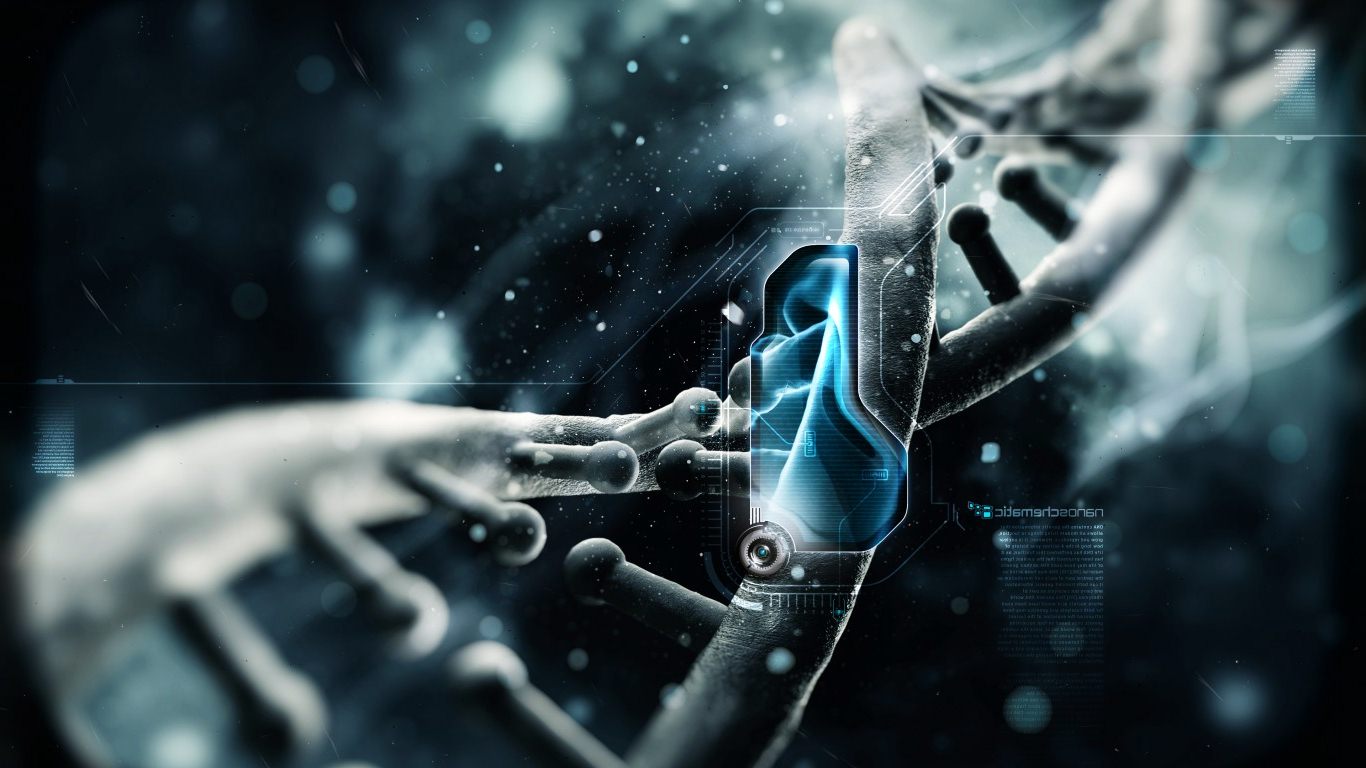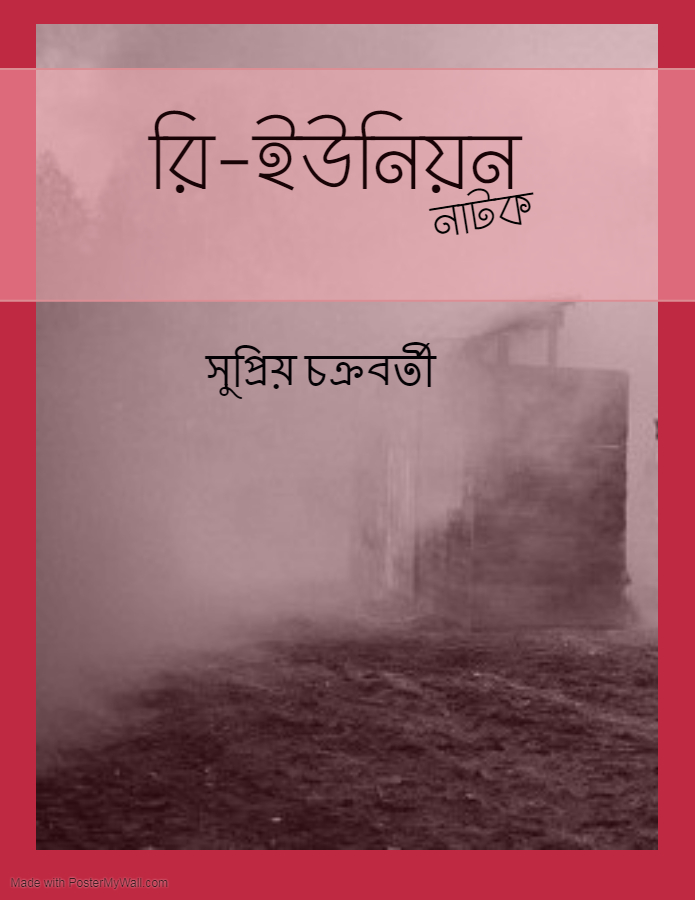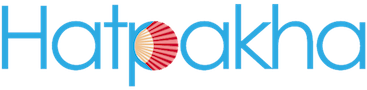কোড নেম প্রমিথিউস
তোমরা এখন বলবে যে, প্রমিথিউসের সাথে এই সেলুলার রিজেনারেশনের সম্পর্কটা কি? বুঝতে পারছ না? আজ থেকে প্রায় তিন,চার হাজার বছর আগে লেখা পুরাণে একদম সঠিক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে লিভারের মতো ইউনিপোটেণ্ট কোশ আর একটাও ছিলনা মানবদেহে। আর সেইজন্যই প্রমিথিউসের লিভার সেই ঈগল খেয়ে যাওয়ার পরেও সেই লিভার আবার রাতারাতি তৈরি হয়ে যেত।
তখন তো অ্যানাটমির অত প্রচলন হয়নি, ১৬০০ সালের সময় আন্দ্রে ভেসালিয়াসের সময় অ্যানাটমির জন্ম। তাহলে মানুষ জানলো কি করে, লিভারের এই রিজেনারেশনের কথা? তখন তো অ্যানাটমি, প্যাথলজি, মাইক্রোস্কোপি, হিষ্টোপ্যাথলজিক্যাল স্টাডি, এসব তো কিছুই ছিল না।তখন তো কোনভাবেই মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, লিভারের কোষগুলো এত তাড়াতাড়ি নিজেই নিজেকে গড়ে নিতে পারে বলে। তাহলে মানুষ জানল কি করে?”
বলে স্যার সবার মুখের দিকে তাকালেন। বলা বাহুল্য, সেইদিনের মত আমরাও নিরুত্তর। সত্যিই তো, মানুষের পক্ষে তো এই প্রশ্নের উত্তর তখন জানা অসম্ভব।
স্যার বললেন, “শুধু প্রমিথিউস বলেই বলছি না। এই তো, হাইড্রার কথাই ধর না, সাত মাথার সেই বিষাক্ত সাপের কথা, যার মাথা কেটে দিলে কাটা মাথার জায়গায় আরও দুটো মাথা গজিয়ে উঠত। সেলুলার রিজেনারেশন শুধুমাত্র প্রমিথিউসের কাহিনীতেই বর্ণনা করা হয়েছে, তাই নয়। আরও অনেক জায়গাতেই বর্ণনা করেছে মানুষ, জেনে বা না জেনে।
আমার একটাই ধারনা এই ব্যাপারে। হয় পুরো ব্যাপারটাই একটা মিথ, আর নয় প্রমিথিউস কোনোভাবে এই সেলুলার রিজেনারেশনের ব্যাপারে জেনেছিল এবং প্রয়োগ করেছিল নিজের শরীরের ওপর। আর তাই সে অমরত্ব লাভ করেছিল। সে পুরাণের নয়, বরং বাস্তবেরই এক মানুষ ছিল, যার অমরতার জন্য বাকিরা তাকে শাস্তি দিয়েছিল।
কিন্তু ধারনা থাকলেই তো হল না। প্রমাণ চাই। বিজ্ঞান এমনই এক শাস্ত্র, যা পুরোপুরি প্রমানের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোথায় পাব সেই হাজার হাজার বছর আগেকার প্রামান্য পুঁথি, যা আমার ধারনাকে সমর্থন করবে?”
সমুদ্র তখন বলল, “ তাই তখন আপনি কেম্ব্রিজ থেকে আথেন্সে চলে এলেন, তাই তো?”
স্যার সটান তাকালেন সমুদ্রের দিকে। তারপর মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, “হ্যাঁ। তার পরেই আমরা ঠিক করি, আমাদের গবেষণাগারটা কেম্ব্রিজ থেকে সরিয়ে এখানে, এই অ্যাথেন্সেই নিয়ে আসা ভালো, যেখানে গ্রীক পুরাণগুলো জন্ম নিয়েছে। আমরা মোটামুটি ডেলফি, মিকোনোস, অ্যাথেন্স সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম যাতে বিন্দুমাত্র কোনও চিহ্ন, কোনও নথি পাওয়া যায় এই ব্যাপারের ওপর। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, কোনও কিছুই সেরকম আশাব্যঞ্জক পেলাম না। গাইড বুকে নিশ্চয়ই পড়েছো যে এখানে তিন হাজারেরও বেশি দ্বীপ রয়েছে। তখন ঠিক করলাম, মেনল্যান্ডে না পাওয়া গেলে দ্বীপগুলোই খুঁজে আসা যাক। যা বলা, সেই কাজ। বলা বাহুল্য, এগুলোর জন্য কোনও সরকারি সাহায্য পাচ্ছিলাম না, পুরোটাই হাইনরিখের পার্সোনাল ফান্ড থেকে আসছিল। এরকমই খুঁজতে খুঁজতে, একটা অজানা দ্বীপে একদিন আমরা যা খুঁজছিলাম, তা খুঁজে পেলাম।
শীতকালে, এক ঝড়ের মধ্যে আমরা গিয়ে পৌঁছেছিলাম দ্বীপটায়। অ্যান্টিকাইরা থেকে ২৫০ মাইল দক্ষিন পশ্চিমে এই ভলক্যানিক দ্বীপটা। জুলিয়াস, আমি আর হাইনরিখ গিয়েছিলাম বোটে করে। জুলিয়াসকে বোটের পাহারায় রেখে আমরা ঢুকলাম দ্বীপে। পেছনে মাইলের পর মাইল জুড়ে শান্ত ইজিয়ান সাগর ছড়িয়ে রয়েছে তার হাত পা মেলে।
দ্বীপটা বেশি বড় না। ব্যাস সর্বসাকুল্যে আট মাইলের মত। চারদিকেই কালো, ভ্লক্যানিক মাটি। গাছপালা গজিয়েছে, তবে মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে হবার জন্য এখানকার ফনা আর ফ্লোরা অনেকটাই আলাদা। ঘন জঙ্গল কেটে কেটে আমরা যখন এগিয়ে চলেছি, তখনই চোখে পড়ে মন্দিরটা। মন্দির না বলে, একটা বাড়ি বললেই ভালো হত, কারন সেখানে কোনও দেবদেবীর মূর্তি নেই। বাড়িটার সামনে থাকা পিলারগুলো উন্নত গ্রিক স্থাপত্যের পরিচয় দিচ্ছিল।
জনমানবহীন একটা দ্বীপে কে এরকম একটা বাড়ি বানাবে? তাও আবার এরকম প্রাচীন? খানিকটা কৌতূহলবশেই ওটার দিকে আমরা হাঁটতে থাকি।
বাড়িটার ভেতরে শুধু জংধরা কিছু লোহার জিনিস আর কাঁচের ভাঙা টুকরো পাই। তার মধ্যে থেকে একটা লোহার টুকরো এনে আমি পরে রেডিওকার্বন ডেটিং করাই। জিনিসটার বয়স দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। প্রায় সাতাশশো বছরের পুরনো।
যন্ত্রপাতিগুলো দেখে আমরা একটা ধারনা করতে পারি, যে যে এখানে থাকত, তার গবেষণা করার অভ্যেস ছিল। কিন্তু, আমরা শুধু যন্ত্রপাতিই পাইনি, আমরা আরও একটা জিনিস পেয়েছিলাম। সেটা একটা পাথরের কোডেক্স ট্যাবলেট। চৌকো, গ্র্যানাইটের একটা পাথর, যার ওপর অচেনা ভাষায় কিছু লেখা।
আমাদের গ্রিক ভাষার জ্ঞান সীমিত ছিল। তবু যা বুঝতে পারি, ওতে বিভিন্ন নির্দেশাবলী খোদাই করে লেখা ছিল। আমরা পাথরটা নিয়ে আসি। নিয়ে এসে প্রাচীন গ্রিক ভাষায় দক্ষ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পাঠোদ্ধার করাই। তারপর লেখাটার যা অর্থ বেরিয়ে আসে, তা শুনে আমরা নিজেরাই অবাক হয়ে যাই।
ট্যাবলেটটা যিনি লিখেছিলেন তাঁর নাম হেসিয়ড। হ্যাঁ, সেই হেসিয়ড যার নাম, মহাকবি হোমারের সাথে একসাথে উচ্চারন করা হয়। হেসিয়ডই সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম প্রমিথিউসের ইউলজি লিখেছিলেন। যাই হোক, পরে কোনও একদিন ওনার সাহিত্য নিয়ে চর্চা করা যাবে।
ব্যাপারটা হল, এই লেখাগুলো ওনার নিজের লেখা নয়। ওনার বক্তব্য অনুযায়ী, স্বয়ং প্রমিথিউস এসেছিলেন ওনার সাথে দেখা করতে। এবং তিনিই ওনাকে এগুলো লিখে যেতে বলেছিলেন। লেখাগুলোর মানে যখন জানতে চেয়েছিলেন উনি, প্রমিথিউস বলেছিলেন, কালের নিয়মে একদিন এই লেখার পাঠোদ্ধার মানুষ নিজেই করবে। এই যুগের জন্য সেই লেখা নয়।
লেখাতে প্রাচীন গ্রিক ভাষায় বর্ণনা করে হয়েছে কিভাবে মানুষ এই রিজেনারেশনকে নিজের জেনেটিক কন্টেন্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অন্য এক মাত্রায় নিয়ে যেতে পারে। কি নেই তাতে, জিন নিয়ে গবেষণার ব্যাপারে? সাড়ে তিন হাজার বছর আগে কোন মানুষ জিন এডিটিং এর কথা ভাববে এটা আমরা ভাবতে পারিনি। কারোর পক্ষেই ভাবা সম্ভব নয়। অথচ নিজের চোখের সামনে যা দেখেছিলাম, সেটাকে অস্বীকার করি কি করে? ট্যাবলেটে স্পষ্ট করে প্রাচীন গ্রিক ভাষাতে জিন এডিটিং কি বা কিরকম সেটা বোঝানো হয়েছিল, আর কি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঐ সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে, তার কথা বলা হয়েছিল। অথচ মানুষের পক্ষে পুরো ব্যাপারটাই জানা অসম্ভব।“
সমুদ্র ভীষণ অবাক হয়ে যায়। বস্তুত আমরা তিনজনেই অবাক তখন। আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করি, “কিন্তু স্যার, জিন শব্দটারই তো উদ্ভব এই ১৯০০ সাল নাগাদ। জোহানসেন প্রথম শব্দটা কয়েন আউট করেছিলেন। তাহলে আজ থেকে অত বছর আগে কি করে জিন শব্দটার উল্লেখ থাকবে ঐ ট্যাবলেটে?”
স্যারের মুখে সেই পুরনো রহস্যময় হাসিটা খেলে যায়। স্যার স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, “সেটা আমি যদি জানতাম, তাহলে তো হয়েই যেত। সেদিন আমি সেটা দেখে যতটা অবাক হয়েছিলাম, আজও ঠিক ততটাই অবাক হই তোমাদেরকে এই ঘটনাটা বলতে গিয়ে।“ শেষদিকে স্যারের কথাগুলো যেন স্বগতোক্তি বলে মনে হয়, “মাঝে মাঝে আমার কেন জানি না মনে হয়, কেউ যেন আমাকে দিয়ে কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নিতে চাইছে। ঐ ট্যাবলেটের মাধ্যমে কেউ যেন হাজার হাজার বছর পেরিয়েও আমার সাথে যোগাযোগ রাখছে…”
~ কোড নেম: প্রমিথিউস (পর্ব ১০) ~