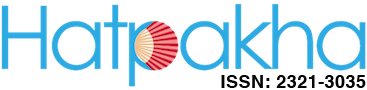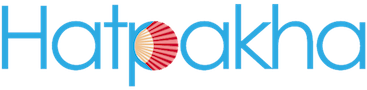(চট্টগ্রাম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০)
মানুষের মধ্যে যাকে বেশি ভালবাসা হয় তাকে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে নানাবিধ নামে-উপনামে আর উপমায় পারণ ভরে বার বার ডাকতে ইচ্ছে করে। যেমন শিশুদেরকে সবাই খুব বেশি ভালবাসে। এজন্য মানুষেরা অনায়াসে এক নিঃশ্বাসে একশটা নামে তাদেরকে ডাকতে পারে – আমার সোনা কই, আমার মধু কই, আমার যাদু কই, আমার পাখি কই, আমার হুনুলুলু কই। ইত্যাদি। ইত্যাদি।
প্রেমিক-প্রেমিকাদের দুনিয়ায় নাম পদানোর ঠাট আরো খানিকটা বেশি। যেমন ধরুন ’জানু’, ‘পাগলী’ ’সোনা’, ‘বাবু’ আরো কত কি। যারা প্রেম করেছে তারা এ ব্যাপারে বেশি বলতে পারবে।
মনের রঙ্গে আর রসে নিত্য-নতুন এক একটা নাম আবিষ্কার করা আর সেই সব অপূর্ব, অদ্ভত নাম ধরে প্রিয় দিল আফরোজ কে দুনিয়ার সমস্ত আহ্লাদে ডেকে ডেকে তার কান ঝালাফালা করে দেওয়া ফারুখের নৈমিত্তিক কর্ম। এ যাবৎ ফারুখ আফরোজকে যত নামে ডেকেছে তত কলাও সম্ভবত আফরোজের খাওয়া হয়ে ওঠেনি।এক একটা আহ্লাদী নাম পদানোর ঘটনা শুনে যে কারো বিচারে ফারুখের দুটো বিশেষ গুণ ধরা পড়বে-
এক, ফারূখ সারাদিন আফরোজের ভাবনা-চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘোরে। আর সেই অবিরাম প্রেয়সী ভাবনা ফারুখকে আফরোজের জন্য হরেক রকমের নাম পদায়নে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি সৃজনশীল করে তোলে। অভাবনায় প্রেমিকার জন্য আদর-সোহাগের এত্ত এত্ত বাড়তি নাম আবিষ্কার হওয়ার কথা নয়; বরং অভাবনায় কখনো কখনো প্রেমিকার আসল নামটাই ভুলে যাবার চান্স থেকে যায়।
দুই, ফারুখ ছেলেটি অতিশয় মেধাবী। কারণ মাথা খাটিয়ে খাঠিয়ে মজার মজার নাম আবিষ্কার করতে হলে উন্নত জাতের, উর্বর ব্রেইন দরকার হয় । গর্ধব টাইপের কারো দ্বারা প্রেমিকাকে পাগল করে দেওয়ার জন্য, তাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে ফেলার জন্য বিশেষ আবিষ্কারের এ কাজ এত সোজা নয়। একটা গাধা টাইপের প্রেমিক পকেটের জোরে প্রেমিকাকে বাজার থেকে একগাদা কৃত্রিম-অকৃত্রিম ফুল কিনে উপহার দিয়ে বাহবা আশা করতে পারে। কিন্তু একটা পটু, জাত মেধাবী প্রেমিক ব্রেইন শক্তির জোরে ফুলের উপরে মনোহর কবিতা রচনা করে তা নিজের কন্ঠে মনোরমভাবে আবৃতি করে শোনায়ে দিয়ে প্রেমিকাকে পাগল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তেমনি এক সক্ষমতার অধিকারী একজন প্রেমিক হলো এই ফারুখ।
দিল আফরোজের প্রতি ফারুখের ভালবাসার বীজ তার অন্তরের গভীরে মূল গেড়েছিল। শক্তভাবে অন্তর জমিনের উপরিভাগ ভেদ করে সে বীজ ক্রমে ক্রমে কখন যেন কান্ড, ডাল-পালা,পত্র-পল্লব ছড়ায়ে পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষের রুপ ধারণ করেছিল, সে কথা শুধু ফারুখই বলতে পারে। আর আফরোজ ভাল মতো তার সাক্ষ্য দিতে পারে। একটু আবেগের বাতাস উঠলেই ফারুখের ভালবাসার গাছটিতে ভীষণ আন্দোলন হয়ে যেত। আর সেই আন্দলিত পরাণে পরমানন্দে তার মুখ হতে প্রেয়সী আফরোজ এর প্রশংসায় আর পুলকে দিনের পর দিন নানান নাম, ছদ্মনাম, উপনাম সব ঝরে ঝরে পড়তো।
একদিন ভার্সিটি’র সকালের ক্লাস শেষে দিল আফরোজ কলা ভবন থেকে হেটে হেটে তার হলের দিকে যাচ্ছে। ফারুখ তার সাথে যোগ দিয়ে তাকে হল পর্যন্ত পৌছে দিতে তার পাশে পাশে হেটে যাচ্ছে। হলের মেয়েদের সাথে প্রেম করলে মেয়ে হলের রাস্তায় মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের পদধূলি একটু বেশিই পড়ে বেশি। তাই মেয়েদের হলের রাস্তা একটু বেশি ক্ষয় হয়। এই রাস্তা ক্ষয় করেই হলের মেয়েদের মন জয় করতে হয় ছেলেদের।
বেলা তখন এগারটা বাজে। ক্ষুধায় আফরোজের পেট চু চু করছিল। কিচ্ছু না খেয়ে সকাল বেলা খালি পেটে সাড়ে আটটার ক্লাস ধরতে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে ভার্সিটি গিয়েছিল। তাই উদ্দেশ্য হলো হলে ফিরে কিছু একটা খেয়ে পেট ঠান্ডা করবে আগে। তাই সে একটু জোরে জোরে হাটতে লাগলো। এমনিতেই প্রেমিক-প্রেমিকার পথ খুব দ্রæত ফুরায়ে যায় কিন্তু প্রেমের আলাপের শেষ হয় না। পৃথিবীর দীর্ঘতর আলাপ হলো প্রেমিক -প্রেমিকার আলাপ আর স্বল্পতম আলাপ হলো স্বামী-স্ত্রীর আলাপ।
কলাভবন থেকে শামসুন নাহার হলের সামান্য এই পথ ফুরিয়ে একটু পরেই আফরোজ হলের ভেতরে ঢুকে যাবে। কিন্তু এই একটুখানি পথ হেটে আর দুটো চারটে কথা বলে ফরুখের পরাণ ভরছে না। আফরোজকে তার অনেকক্ষণ ধরে দরকার। গত রাত থেকে ফারুখের মাথায় নতুন একটা নাম এসেছে। সেই নতুন নামটা আফরোজকে না বলতে পারলে তার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না। সেই নতুন নামে তাকে কয়েকবার না ডাকা পর্যন্ত সে স্থির হতে পারছিল না। এ নিয়ে তার সাথে একটু পাগলামী করার জন্য তার মন-প্রাণ আকুপাকু করছিল। তাই আফরোজের গতি থামানোর জন্য ধাঁ করে চোখে-মুখে বিরাট সিরিয়াসনেস নিয়ে এক লাফে তার সামনে গিয়ে দু’হাত দুদিকে প্রসারিত করে পথ আটিকিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল-
“শোন, শোন, আফরোজ, তোমার সাথে একটা জরুরী বিষয়ে কথা বলার দরকার।”, ফারুখ আফরোজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।
“কি এমন সিরিয়াস কথা তোমার? তাড়াতাড়ি বল। ক্ষুদায় আমার পেটের নাড়ি জ্বলছে।”
“না, বলছি যে…”, ফারুখ কথা শেষ না করে একটু থামলো।
“ হ্যাঁ, শেষ কর। থামলে কেন?”, আফরোজ পুরো কথাটা শুনতে চাইলো।
“আচ্ছা, তোমাকে দেশের মাটি বলে ডাকা যাবে?”, ফারুখ প্রস্তাব দিল আফরোজ কে।
“কেন? ঠিক দেশের মাটি ডাকতে হবে কেন আমাকে, বলতো?”, আফরোজ আশ্চর্য হয়ে কারণ জানতে চাইলো।
“ না, ঐ যে তোমার পরে ঠেকায় মাথা। এ জন্য।”, ফারুখ কারণ ব্যখ্যা করলো।
“হা হা হা…”, যুক্তি শুনে দিল আফরোজ হেসে ক্ষুণ হতে লাগলো।
সেদিনের সেই হাসি-পাগলামী-আনন্দ-আশ্চর্যের নামকরণের ঘটনার পর থেকে আজীবন ফারুখ আফরোজ কে দেশের মাটি বলেই ডাকতো আর এভাবে পাগলামী করতো। প্রেমে পাগলামীটাই বুদ্ধির কাজ। আর বাদবাকী সব পাগলামী।
দেশের মাটি বলে আফরোজকে ফারুখ গোচরে -অগোচরে ডাকতো। কাছে থাকলে সরাসরি ডাকতো, দূরে থাকলে টেলিফোনেও ডাকতো। প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে ডাকতো। দিল আফরোজও এই ডাকে বিনা আপত্তিতে সাড়ে দিতে অভ্যাস করে নিয়েছিল আর শীঘ্রই তার আসল নামটা ভুলতে বসেছিল। বিশেষ মানুষের দেওয়া বিশেষ নামের ডাক শুনতে তার বিশেষ মজাও লাগতো আফরোজের।
ফারুখ যখন অনার্স শেষ করেছে তখন দিল আফরোজ তারই ডিপার্টমেন্টে প্রথম বর্ষে পড়ে। দর্শনে। ফারুখের বাড়ি ব্রা²নবাড়িয়ায়। নদী ভাঙনের অঞ্চলে। দিল আফরোজের বাড়ি ঝিনাইাদহে। ফারুখের এলাকার এক পরিচিত ছোট ভাই দিল আফরোজের ক্লাসে পড়তো। তার নাম ইমন। একদিন শুভক্ষণে কলা ভবনের সামনের মাঠে দাড়িয়ে সেই ছোট ভাই ইমন তার বান্দবী দিল আফরোজের সাথে ফারুখের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা জমিনে দু’জনের সেই দিনের ক্ষণকালের পরিচয় পা বাড়িয়ে আস্তে আস্তে পণয়ের পথ ধরেছিল। কিন্তু এক বছরের মাথায় একদিন নিষ্ঠুর নিয়তি তাদের দুজনকে একেবারে আলাদা করে দিল। বিচ্ছিন্ন করে টানা তিন বছর বছর ধরে ফারুখকে দিল আফরোজ এর কাছ থেকে সম্পূর্ণ অজানা, অদেখা ও অখবর করে দিল। ঘটনাটা নি¤œরুপঃ
সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। ঘড়িতে তখন সকাল দশটা বাজে। ফারুখ তখনো হলে আরাম করে ঘুমাচ্ছিল। আর দিল আফরোজের ঐ সময় ক্লাস ছিল। ঘুম শেষে আর ক্লাস শেষে সাড়ে এগারোটার দিকে তাদের দুজনের কলাভবনের সামনে দেখা করার কথা ছিল। কলা ভবনের সামনের মাঠই ছিল তাদের সচারাচর মিলন স্থান। এখানে গল্প-গুজব করে, বাদাম খেয়ে আর আড্ডা মেরে তাদের সকাল গড়ায়ে বিকাল আর বিকাল গড়ায়ে রাত হয়ে যায়।
সেই বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ করে ফারুখের বাড়ি থেকে মোবাইল কল আসলো। সে জানতে পারলো যে, মেঘনা নদীর প্রচন্ড স্রােতের আঘাতে নদীর কুল ভাঙতে ভ্ঙাতে একেবারে তাদের দক্ষিনের ঘরের পেছনের দেওয়াল ঘেষে পৌছে গেছে। যেভাবে পানির অবিরাম আঘাতের চোট এসে লাগছে তাতে আর একদিনও তাদের বাড়ি-ঘর টিকে থাকবে কিনা তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। যে কোন মুহুর্তে নদী গর্ভে তাদের ভিটে মাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।
এই খবর শুনে ফারুখের শরীর ভয়ে শীতল হয়ে আসলো। শরীর শুধু প্রচন্ড শীতে ঠান্ডা হয় তা নয়, মাঝে মাঝে প্রচন্ড ভয়েও শরীর হীম শীতল হয়ে যায়। বিছানায় যেমনি শুয়ে ছিল তেমনি উঠে ঘুমের মুখ-চোখ নিয়ে হ্যাঙ্গার থেকে টান দিয়ে একটা প্যান্ট পরে তখনই হল থেকে বেরিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল ফরুখ। রিক্সায় বাস স্ট্যান্ডে যেতে যেত দ্রæত হাতে টাইপ করে ম্যাসেঞ্জারে দিল আফরোজকে একটা ক্ষুদে বার্তা পাঠায়ে জানিয়ে রাখলো-
“ প্রিয় দেশের মাটি, জরুরী প্রয়োজনে আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। আজ আর দেখা হচ্ছে না। সাক্ষাতে সব খুলে বলব।”
ফারুখের বাড়িতে তার বিধবা মা থাকে। সে ছাড়া তার আর কোন ভাই-বোন নেই। ফলে বাড়ি-ঘরে, মায়ে, দ্বায়ীত্বে তার আর কোন পৈত্রিক অংশীদার কেউ নেই। মা বাপের একমাত্র সন্তান হলে একটা বিশেষ সুবিধা যেমন হয় তেমনি একটা বিশেষ অসুবিধাও হয়। সুবিধাটা হলো বাপের যত সম্পদ সম্পত্তি থাকে একাই ভোগ করা যায়। আর অসুবিধাটা হলো সংসারের সব রকমের দুঃখ-কষ্টও একাই ভোগ করতে হয়; ভাগ নেওয়ার জন্য বড়-ছোট কোন ভাই-বোন থাকেনা।
ফরুখের বাবা ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে বছর পনের আগে। দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছর ধরে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে তার চিকিৎসার খরচ মেটাতে মাঠের জমাজমি সব বিক্রি করে ছাপ করে দিতে হয়েছিল। এখন ফারুখদের সহায়-সম্বল বলতে বাজারে জায়গাসহ দুইটা দোকান। ঐ দুই দোকান ভাড়ার ছয় হাজার টাকা দিয়ে তাদের সংসারের যাবতীয় সব খরচ চলে। ঢাকায় ফারুখের লেখা পড়া চলে।
পাঁচ-ছয় বছর হলো ফারুখের খালাত বোন সুবহানা তাদের বাড়িতে এসে থাকে। ফারুখ তাকে প্রথম কিছু দিন তার নামের সুব বাদ দিয়ে শুধু হানা বলে ডাকতো। কিছুদিন পরে এই হানা নামটির ইংরেজি অনুবাদ করে ফেলল সে। হা এর অনুবাদ ইয়েস আর না এর অনুবাদ নো। সুতারাং সুবহানার অনুবাদিত সংক্ষিত নাম হয়ে গেল ইয়েস-নো। এক সময় ফারুখের মাও সুবহানা কে ইয়েস-নো বলে ডাকা শুরু করেছিল।
ইয়েস-নো মেয়েটা বড়ই অসহায়, এতিম। বাবার বিরুদ্ধে মাদক সেবন ও মাদকের ব্যবসার অভিযোগ ছিল। ছয় বছর আগে ক্রসফায়ারে মারা পড়ে। মা দ্বিতীয় বিয়ে করে তাকে ছেড়ে নতুন সংসারে চলে যায়। ইয়েস-নো’র আর যাওয়ার জায়গা থাকলো না। প্রকৃতিতে এক গাছের বাকল অন্য গাছে জোড়া লাগলেও মানব সমাজে মা কিংবা বাবার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারে প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়ের কিছুতেই জোড়া লাগে না।
মেয়েটা হঠাৎ এভাবে আশ্রয়হীন হয়ে পড়লে ফারুখের মা নিজে গিয়ে ইয়েস-নোকে তার কাছে নিয়ে এসেছিল। সেই থেকে নিজের পেটে ধরা মেয়ের মত করে লালন পালন করছিল। ফারুখও ইয়েস-নোকে খুব ভাল জানতো। খুব ¯েœহ করতো। এটা-ওটা বলে তাকে ক্ষেপাতো, হাসাতো, কাঁদাতো। ফারুখের দেওয়া ইয়েস-নো নামটা সুবহানার খুব ভাল লেগেছিল।
ফারুখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি আসলে যে কদিন বাড়িতে থাকতো সে কদিন প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ইয়েস-নো কে পড়াতে বসাতো। ইয়েস-নো ফারুখকে মনে মনে খুব পছন্দ করতো। কিন্তু কখনো প্রকাশ করতে পারেনি, না মুখে , না ভাবে-ভঙিÍতে। আত্মীয়তার সম্পর্কের রং বদলায়ে নতুন সম্পর্কের কথা ভাবতে গেলে ভেতরে সংকোচ একটু বেশি হয়, পরিবারে আপনজনদের বাধাও অনেক সময় একটু প্রবল হয়।
একদিন ফারুখের মা ইয়েস-নো কে ফারুখের সাথে বিয়ে দিয়ে চিরকালের জন্য তার কাছে রেখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল ছেলের কাছে। কিন্তু ফারুখ সে সময় তার মায়ের প্রস্তাবটা নাকচ করে দিয়েছিল। দিল আফরোজের সাথে তার সম্পর্কের কথাও সেদিন সে মাকে জানিয়ে রেখেছিল। মা- ছেলের এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার আলাপ-আলাপনের ব্যাপারে ইয়েস-নো কিছুই জানতো না। ফলে খালা কিংবা খালাতো ভায়ের প্রকাশ্য উৎসাহের অভাবে ইয়েস-নো’র মনের মধ্যে বুদ বুদ করে জেগে ওঠা স্বপ্ন তার মধ্যেই গোপন হয়ে রইলো।
সেদিন বাড়ির আসন্ন বিপদের খবর শুনে মাথা পাগল হয়ে যাওয়া ফারুখের বাড়ি ফেরার ভীষণ তাড়া থাকায় বাসের ভাল-মন্দ ক্লাস যাচাই-বাছাই করার কোন সময় ছিলনা তার হাতে। স্ট্যান্ডে গিয়েই খেয়াল করলো ব্রা²নবাড়িয়ার উদ্দেশ্যে একটা যাত্রী বোঝায় গাড়ি স্টান্ড ছেড়ে আস্তে আস্তে গড়াতে আরম্ভ করেছে। হেলপার তখনো যাত্রী ডেকে ডেকে গলা ফাটিয়ে ফেলছে। অনেক ক্ষেত্রেই সেবা বঞ্চিত, খাতির বঞ্চিত বাঙালীর সবাই এক বাক্যে স্বীকার করবে যে, লোকাল বাসই একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে মানুষকে ডাকাডাকি করে, টানাটানি করে সেবা দেওয়ার জন্য। ফারুখ এদিক ওদিক না তাকিয়ে, আগ-পাছ কিছু না ভেবে সেই মুহুর্তেই দৌড়ে গিয়ে ঐ লোকাল টাইাপের বাসে ঝুলে, ঠেলে উঠে পড়লো। ফরুখের একদম মাথা ঠিক ছিল না যে, লোকাল বাসে যাত্রীর তাড়া থাকে কিন্তু বাসের তাড়া থাকে না।
বাসে সিটের অতিরিক্তি যাত্রী তোলা হয়েছিল। অতিরিক্ত যাত্রী বোঝায় যে কোন বহনের জন্য ঝুকিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান কালের বাঙালীরা এই একটি বিষয়ে জীবনের ঝুঁকি নিতে সর্বদা রাজি থাকে। দ্’ুজন লোকে একজন মানুষকে দিনে-দুপুরে রাস্তায় ফেলে কোপায়ে টুকরো টুকরো করবে তবুও আশে পাশের শত শত লোকের মধ্যে থেকে একটা লোক এগিয়ে যাবেনা। বলবে, ভাই, জীবনের ঝুঁকি আছে। কিন্তু পঞ্চাশ জনের ধারণ ক্ষমতার নৌকায় আরো অতিরিক্ত একশ জন আল্লাহর বান্দা চড়ে বসে জীবনের চরম ঝুঁকি নিতে এখানে এই বাঙালীরা একবাক্যে রাজি হয়ে যাবে।
ঐ বাসের নিয়ম হলো সীট বরাদ্দের বেলায় দূরের যাত্রী অগ্রগন্য। যতদূর গন্তব্য হবে, তত বেশি ভাড়ার টাকা আদায় হবে।দূর যাত্রীদের সীট প্র্প্তাীর অগ্রগন্যতার ফজিলত মূলত এখানে। ব্রা²বাড়িয়া গন্তব্য জানতে পেরে বাসের কন্ডাকটর আপন চেষ্টায় একজন লোকাল যাত্রীকে উঠায়ে দিয়ে ফারুখকে তার সীটৈ বসায়ে দিল। সকালে না খাওয়া শরীররটাতে বাড়িতে বিপদের আশংকায় একবারে কাপন ধরেছিল। বিপদে দুর্বল প্রকৃতির মানুষের শীরর-মন টিকতে চায় না, ভেঙে পড়ে। তাই দাঁড়ানো অবস্থা থেকে একটু সীটে বসে শরীরকে স্থির করাটা সত্যিই ঐ মুহূর্তের একটা অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল ফারুখের। না চাইলেও বাস কন্ডাকটর যেন ফারুখের সেই প্রয়োজনটা আপন দ্বায়ীত্বে মিটিয়ে দিল।
সময়ে , সময়ে মানুষের ভূমিকা ও কর্তব্য পাল্টে যায়। মানুষ সব সময় কেয়ার গিভারের ভুমিকায় থাকতে পারে না; কখনো কখনো তাকে কেয়ার রিসিভারের অবস্থায়ও পড়তে হয়। কাউকে সিট থেকে উঠায়ে দিয়ে সেই সিটে বসে বাসে ভ্রমন করার অমানবিক অভ্যাস ফারুখের কখনো ছিল না। বরং সে মুরব্বী মানুষ, মহিলা মানুষ দেখলেই নিজের সিট ছেড়ে দেওয়া ছেলে। কিন্তু সেদিন বিপদাতঙ্কে ভারাক্রান্ত হয়ে ফারুখ নিজেই একবারে যেন একজন অচল বুড়োলোকের অধম অনুভব করছিল। তাই এই প্রথম বাস ভ্রমনে কাউকে উঠায়ে দেওয়া সীটে বসতে সে না করতে পারলো না।
নরসিংদি বিশ্বরোডে গিয়ে বাস থেমে গেল। শোনা গেল বাস আর সামনে এগোবে না। গাড়ি ঘোড়ায় একদম মাইলের পর মাইল লাইন হয়ে গিয়েছিল। চার মাইল সামনে একজন নেতার ছেলেকে পরিবহরন বাসে ডলে-পিষে মারার ঘটনা ঘটায় রাস্তা অবরোধ, গাড়ি ভাংচুর চলছিল। এদেশের মানুষের রাগ প্রকাশের আর্ট হলো ভাঙচুর করা আর আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। নেতার ছেলে তো, তাই ভাঙচুর একটু বেশি হচ্ছিল। যদু-মধু ট্ইাপের কেউ হলে ভাঙচুরে এত লোক পাওয়া যেত না।
ঐদিন তখন পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয়নি ফারুখের। দুই-আড়াই ঘন্টা বাসের মধ্যে অলস বসে থেকে থেকে খুব ক্ষুধা লেগে গিয়েছিল তার। আলস্যে পাকস্থলী ক্ষুধা সৃষ্টি করে আর মস্তিষ্ক শয়তানী বুদ্ধির যোগান দেয়। ক্ষুধা মেটাবার জন্য ফারুখ বাস থেকে নেমে অদূরেই বিশ্বরোডের পাশের একটা টঙ্রে দোকানে পাতা বেঞ্চের উপরে গিয়ে বসলো। অনুমতি নিয়ে একটা পামরুটি আর একটা কলা ছিড়ে খাওয়া শুরু করলো। আর এক কাপ রং চায়ের অর্ডার করে রাখলো। তৃষ্ণার্ত কন্ঠে পানির আকাঙ্খা আর বিপদাশংকিত মনে বাড়ির সাথে মিলনের ব্যাকুলতা সমান। তাই কলা-রুটি শেষ করে তৃষ্ণার্ত গলা ঠান্ডা করতে ঢকঢক করে এক গøাস পানি খেয়ে দিল। এবার আরাম করে সময় নিয়ে রং চায়ে এক একটা চুমুক দিতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো রাস্তার এই গোলযোগ কখন উঠে যাবে আর কখন তার বাস আবার বাড়ির পথে চলতে শুরু করবে।
কিন্তু কথায় আছে দুঃখের নিশি বেড় দীর্ঘতর, সহজে তো ভোর হতে চায় না। ঠিক তেমনি করে বিপদের পথও খুব টানা হয়। সহজে ফুরাতে চায় না।
চা খেয়ে ফারুখের চোখে যেন এক মরণ ঘুম নেমে আসলো। উঠে দাড়িয়ে সেখান থেকে নড়ার মত কোন বল শরীরে পাচ্ছিল না সে। মুহুর্তের মধ্যেই দোকানের বেঞ্চের উপরেই অচেতন হয়ে পড়লো সে।
পরের দিন শুক্রবার সকাল দশটা। তার ঘুম ভাঙলো। জেগে উঠে দেখলো সে নরসিংদি সদর হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। চায়ের দোকান থেকে হাসপাতাল। মাঝামাঝি সময়টাতে কি ঘটেছিল তা তার কিচ্ছু মনে নেই। বিছানা, জামা , প্যান্ট হাতড়ে দেখলো তার মোবাইল নাই, পকেটে তিন’শ চল্লিশটা টাকা ছিল, তাও নাই। নার্স এর কাছ থেকে তার হাসপাতালে আসার কাহিণী শুনে বুঝলো যে, গতকাল চায়ের সাথে অচেতনকারী কিছু একটা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর অজ্ঞান হয়ে পড়লে কোন শয়তান মানুষেরা তার টাকা পয়সা এবং মোবাইল ফোন হাতিয়ে নিয়েছিল ।
শরীরটা খুব দুর্বল লাগছিল তার। তখনো ঘুমের চোটে ভাল করে চোখ খুলতে পারছিলনা। কিন্তু তার যে হাসপাতালে শুয়ে থাকলে চলছে না। তাই ঐ অবস্থায় সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছাড়তে চাচ্ছিল না। সেই এক প্রকার জোর করে নাম কেটে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ির দিকে হাটা দিল। সম্মুখে বাড়ির মায়ার শক্ত টান আর পেছনে দ্বায়ীত্বের জোর ঠেলা থাকলে দুর্বল শরীরও পথে পা বাড়াতে উৎসাহ পায়।
সেদিন দুপুরের সময় ক্লান্ত, অসুস্থ্য ফারুখ বাড়ি পৌছে গেল। কিন্তু ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগীটি মারা গেল- এই কথাটার একটা বাস্তব ফল যেন তার জীবনে ফলে গেল।
গতরাতে তার মায়ের দক্ষিনের শোয়ার ঘর, গোয়াল ঘর, তিনটা নারকেল গাছ, মুরগির ঘর- সব নদী গর্ভে ধসে পড়ে কোথা থেকে কোথা হারিয়ে গেছে। সে ক্ষতি হয়তো মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ফারুখের জনম দুঃখিনি মাও যে ঘরের সাথে সাথে নদীতে ভেসে গেছে। সে ক্ষতি সে কি করে সইবে?
সে কাল রাতে তার হতভাগিনী মা ঐ ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। পাড়া থেকে অনেক শুভাকাঙ্খিই ফারুখদের বাড়ি এসে ভাঙনের গতি বিধি চাক্ষুষ দেখে ফারুখের মাকে ঐ রাতে দক্ষিণের ঘরটাতে শুতে মানা করেছিল, কিন্তু সে শুনেনি। ঐ ঘর তার প্রিয় স্বামীর হাতে তৈরী ঘর। মরে গেলেও সে ঐ ঘর ছাড়বে না। এই জেদ করেই সে মরলো। কাউকে মরণ ডাকলে কারো মানাই তাকে আটকাতে পারে না।
গ্রামের বিধবা মহিলাদের কাছে স্বামীর ভিটে-মাটি-ঘর তীর্থস্থানের মত পবিত্র আর পূজনীয়। এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারা তাদের কাছে স্বর্গ প্রাপ্তীর সমান। ফারুখের মাও যেন স্বামীর ঘরের পালকি চড়ে নদী স্রোতের ঘাড়ে সোয়ার হয়ে স্বামীর সাথে মিলিত হতে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। নীরবে, নিভৃতে একাই সেই চিরপ্রস্থানের আয়োজন সেরে রাতের অন্ধকারে কখন যে অথৈ নদীতে হারিয়ে গেল তার টু শব্দটুকুও কেউ শুনতে পেল না।
নদীর বুকে মায়ের ভেসে যাওয়ার খবর শুনে আধমরা হয়ে বাড়িতে ফেরা ফারুখ যেন এবার পুরোটাই মরে গেল। মাকে হারানোর ব্যথা তার সহ্য হচ্ছিল না কোন ভাবে। বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল আর বুক চাপড়ে শুধু আহাজারী করছিল-
“ একটা রাত তুই ক্যান আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারলিনে, মা? ক্যান দক্ষিনের ঘরে শুতে গেলি, তুই? ক্যান সকলের কথা শুনলিনে, মা? আমারে তুই কার কাছে রেখে গেলি , মা? আমি এখন কার কাছে থাকবো?”
কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তির আত্মা কষ্ট পায়। মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। কিন্তু বাস্তবে মৃত ব্যক্তির স্বজনরা এই উপদেশ ভঙ্গকারী হয় আর বাদবাকী সব মানুষ এই উপদেশ দাতার ভূমিকায় থাকে। অন্যের মা মারা গেলে আপনি খুব সহজেই এই উপদেশ দিতে পারবেন কিন্তু আপনার নিজের মা মারা গেলে আপনার বন্ধুর দেওয়া একই উপদেশ মেনে না কেঁদে চুপ থাকতে পারবেন না। বাস্তবতা ঠিক এমনই।
এমনি উপদেশ দিয়ে গ্রামবাসী মায়ের শোকে ফারুখের বুকফাটা কèানাকাটি থামানোর চেষ্ট করে ব্যর্থ হতে লাগলো। দুই-তিন ঘন্টা পরে তার ছটফটানি একটুখানি থেমে আসলে প্রতিবেশিরা ধরাধরি করে ফরুখকে তার মায়ের গায়েবী জানাজায় নিয়ে দাড় করালো। জানাযায় দাড়িয়ে উপরে আকাশের দিকে মাথা তুলে আল্লাহকে ডেকে ফরিয়াদ করতে লাগলো-
“ হে মহান আল্লাহ, তুমি আমার মাকে তার স্বামীর প্রিয় ঘর সহ দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছো। তোমার জান্নাতে এই ঘর সমেত তাকে তার স্বামীর সাথে মিলিয়ে দাও।”
ভাগ্যের ফয়সালায় সে রাতে ফারুখের খালাত বোন ইয়েস-নো বেচে গিয়েছিল। রাতের খাবার খেয়ে খালাকে অনেক করে বলে, বোঝায়েও দক্ষিণ ঘর থেকে বের করে তার সাথে উত্তর পাশের রান্না ঘরে শুতে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই একান্ত নিরুপায় হয়ে ইয়েস-নো একাই রান্না ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছিল। আর এভাবেই অদৃষ্ট তাকে রেখে তার খালাকে নিয়ে চলে গেল। পৃথিবী থেকে মানুষকে তুলে নেওয়ার এমনি নিখুঁত খেলা খেলেন সৃষ্টিকর্তা। এভাবেই তিনি ডাক পড়াদের থেকে ডাক না পড়াদের আালাদা করে দেয়।
জানাযা শেষে ফারুখদের বাড়ি থেকে ইয়েস-নোকে তাদের প্রতিবেশি বাশার চাচা নিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে রাখলো। কিন্তু অনেক বলে কয়েও ফারুখকে কিছুতেই কেউ কারো বাড়ি নিয়ে যেতে পারলো না। বাশার চাচা খুব জোরাজুরি করছিল তার বাড়িতে থাকার জন্য। কিন্তু ফারুখ কিছুতেই রাজি হলো না। সে বলেছিল-
“আমার মা তার প্রিয় ঘর নিয়ে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। অন্য কারো ঘরে আমার ঘুম আসবে না, বাশার চাচা।”
রাত হয়ে গেল। ফারুখ কারো বাড়িতেও আশ্রয় নিল না, আবার জঙ্গলেও গেল না। অবশেষ সে বাড়ির পাশের মসজিদে গিয়ে উঠলো। মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ঘরে থাকা সব বান্দার অধিককার।
প্রতিবেশিদের দেওয়া খাবার নিয়ে ইয়েস-নো মসজিদে তার ভাই ফারুখকে খাওয়ায়ে আসলো। দুই গাল খেয়ে সব ফিরিয়ে দিয়েছিল। এমন মাতৃশোকের সময় সন্তানের খাদ্যে স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে না। মুখ হয়ে খাবার গলা দিয়ে নামতে চায় না। এ সময় মায়ের সাথে নানান স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠে হ্রদয়ের ভেতরে এমন এক বেগ তৈরী করে যা মুখকে আড়ষ্ঠ করে দয়ে, কন্ঠনালী ধরে আনে আর খাদ্য নালী বন্ধ করে দেয়।
ভেঙে পড়া শরীর আর দুঃখ ভরা মন নিয়ে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত ফারুখ মসজিদে বসে বসে নামাজ-কালাম পড়লো আর মায়ের জন্য প্রার্থনা করে কাটিয়ে দিল। এর পর ক্লান্তি-শ্রান্তিতে তার শরীর এলিয়ে পড়তে লাগলো; ঘুমে তার দুচোখ বুজে আসতে লাগলো।
এ দুনিয়ায় মা ছাড়া দুঃখের ভাগ কেউ নিতে রাজি হয় না। তবে একজনের দুঃখ আরেকজনকে বলে কিছুটা হালকা হওয়া যায়। তাই দুঃখ দেওয়ার মানুষের যেমন অভাব হয় না, তেমনি শত দুঃখেও বেচেঁ থাকলে হলে অন্তত দুঃখ শোনার খুব কাছের দু’একজন মানুষ প্রত্যেকের জীবনে থাকতে হয়।
গত দুইদিন ধরে বয়ে যাওয়া মানব সৃষ্ট , প্রকৃতি সৃষ্ট কাল বৈশাখী ঝড়ে ফারুখের শরীর ও মন লন্ড-ভন্ড হয়ে যে কি নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে সেই দুঃখের কাহিনী আফরোজকে বলে দিয়ে একটু হালকা হওয়ার ইচ্ছে দু-একবার ফারুখের মনের মধ্যে জেগেছিল সেই রাতে। তার ইচ্ছে হয়েছিল আফরোজকে বলতে-
“মেঘনা নদীর হিং¯্র ভাঙনে আমার মা গেছে, ভিটে গেছে, ঘর গেছে। সব গেছে। আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি, দেশের মাটি। আমি রিক্ত হয়ে গেছি।”
কিন্তু আগের দিন তার মোবাইল খোয়া যাওয়ার কারণে আর দুই দিনের ধোকল সয়ে বেহাল হয়ে যাওয়া শরীরে সেই ইচ্ছা পূরণ আর বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠলো না । শীঘ্রই মসজিদের টাইলসপাতা মেঝেতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো ফারুখ।
রাত তখন তিনটা বাজে। হঠাৎ সেই গভীর রাতে মসজিদের গেইটে কারা যেন জোরে জোরে ঝাকা-ঝাকি করতে লাগলো আর দরজা খোলার জন্য বার বার বলতে লাগলো। কিন্তু ফারুখের এমন ঘুম এসেছিল যে, সে কিছুই টের পেল না। একবারে ঘুমে মরে ছিল। ঘুম আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য হলো জেগে ওঠা। ফারুখ তখনো ডাকাডাকি শুনে জেগে ওঠেনি।
অনেক ডাকাডাকি আর গেইটে গুতোগুতির পরেও যখন ফারুখের ঘুম ভাঙলো না তখন গেইট ভেঙে মসজিদের ভেতরে ঢুকে গিয়ে পাঁচ-ছয়জন অস্ত্রধারী লোক চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে লাথি মেরে ফারুখকে জাগিয়ে তুলল। এরপর মসজিদের ভেতরেই তাকে সংক্ষিপ্ত জেরা করলো-
“ ইউর নেইম ইজ ফারুখ মোল্ল্যা?”
“ইয়েস। বাট হু আর ইউ অল? হুয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ফ্রম মি?”
“ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট। উই হ্যাভ বিন লুকিং ফর ইউ ফর টু ইয়ারস। ইউ আর দি লিডার অব আল কায়েদা বাংলাদেশ।”
এরপর ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই সেই লোকগুলো ফারুখের চোখ মুখ শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ দেওয়া হল না। এতগুলো অচেনা, অপরিচিত লোকজন তাকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যাচ্ছে অথচ বাচার জন্য একটা চিৎকার দিয়ে মানুষজন জড়ো কারার জন্য তার বুদ্ধির জোর, গায়ের জোর কোনটাই সাড়া দিল না। চিল যেমন ছো মেরে চোখের পলকেই মুরগির বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়, তেমনি করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘুমের মানুষটাকে একটা মাইক্রোবাসে উঠায়ে নিয়ে দ্রæত গতিতে অজানা কোথা থেকে কোথায় যে নিয়ে চলল সেটা ফরুখ চোখ বাঁধা থাকায় একটুও ঠাওর করতে পারলো না।
চোখ বন্ধ থাকলেও চলা যায় কিন্তু এ চলায় কোথায় যাওয়া হলো তা চোখ খোলা মানুষদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হয়। চার দিন চোখ বাঁধা অবস্থায় অবিরাম চলার পরে অবশেষে যখন চোখ খুলে দেওয়া হলো তখন তার অপহরণকারীদের কাছ থেকে জানতে পারলো যে, সে তখন আমেরিকায়। আর যারা তাকে তুলে নিয়ে এসেছে তারা আমেরকিার গোয়েন্দা। বিশেষ গোয়েন্দা বিমানে করে তাকে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছে।
ইন্ট্রোগেশন সেলে যখন গোয়েন্দারা তার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল, তখন ফারুখ অনেক কান্নাকাটি আর অনুনয়-বিনয় করে তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, তাদের কোথাও একটা মারাত্মক ভুল হচ্ছে। তারা যে ফারুখ মোল্ল্যা কে খুজছে সে আসলে সেই ব্যক্তি নয়। কিন্তু গোয়েন্দরা তার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করলো না। নামে মিলে গিয়েছিল। মুখের দাড়িতে মিলে গিয়েছিল। গোয়েন্দারা জানতো না যে, ফারুখের মুখের দাড়ি ধর্মের না, স্টাইলের। একজন আল্লাহ ভক্ত খাটি ধার্মিক উপাসনার জন্য সব সময় মসজিদে পড়ে থাকে। ফারুখের মসজিতে অবস্থান যে সেই অর্থে নয়, এটা যে দু’একদিনের আবেগের আর আশ্রয়ের জন্য তাও গোয়েন্দারা জানলো না।
না জেনে, না বুঝে, শুরু হলো নিয়ম করে টর্চার করা। আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের তথ্য আদায়ের চেষ্টা করা হতো তার কাছ থেকে। কিন্তু যার দিন চলে যায়, রাত কেটে যায় পড়াশোনায়, ভবিষ্যৎ পেশা জীবন গঠনের ভাবনায় আর তার আফরোজের জন্য নিত্য নতুন নাম আবিষ্কারের সাধনায় তার কাছে দেশীয় কিংবা আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসের খবর থাকবে কি করে। তাই গোয়েন্দাদের সব প্রশ্নের উত্তরে ফারুখ শুধু তাদেরকে তিনটা কথা বলতো আর চিৎকার করে কাঁদতো-
“ আাই ডোন্ট নো এ্যানিথিং। আই এ্যাম নট দ্যাট ফারুখ মোল্ল্যা হুম ইউ আর লুকিং ফর। ইউ আর ছারটেইনলি মিসটেকেন সামহোয়্যার।”
এভাবে আমারেকিার গোয়েন্দা হেফাজতে এক বছর কেটে গেল।
অবশেষে ফারুখের কথা প্রমানিত হলো। দে অয়ার রিয়েলী মিসটেকেন। মার্কিন গোয়েন্দারা নিশ্চিত হলেন যে, একবছর পূর্বে তারা ভুল ফারুখ মোল্ল্যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের কাছে সেদিন তথ্য ছিল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন আল কায়েদার বাংলাদেশ প্রধান ব্রা²ণবাড়িয়ার মেঘনা নদীর কুলে অবস্থিত একটি গ্রামের মসজিদের ভেতরে আজ একসপ্তাহ ধরে অবস্থান করছে। তথ্যটি সত্য ছিল। কিন্তু গোয়েন্দারা ভুল করেছিল এই খানে যে,ঐ গ্রামে মসজিদ ছিল দুইটা। তারা পশ্চিশ পাড়ার মসজিদে গিয়ে আসল ফারুখ মোল্ল্যাকে না ধরে পূর্ব পাড়ার মসজিদে এসে ভুল ফারুখ মোল্ল্যাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এক বছর পর এই ভুল ধরা পড়ল যখন বাংলাদেশে সেই আসল ফারুখ মোল্ল্যা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলো। বাংলাদেশে আসল ফারুখ মোল্ল্যার ধরা পড়া প্রমান করলো যে , আমেরিকায় বন্দী ফারুখ মোল্ল্যা নকল; সে নিরপরাধ।
এদিকে একরাতের মধ্যে ফারুখের এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় সবাই খুব বিষ্মিত হয়েছিল। সবার খুব মায়াও হয়েছিল ছেলেটার প্রতি।কোথাও ফারুখের সন্ধান না মেলায় যত দিন যেতে লাগলো মানুষেরা তত বেশি জোর দিয়ে দিয়ে তার উধাও হওয়ার সাম্ভাব্য অনেক গল্প অনুমান করতে লাগলো। কেউ বলল জ্বীন-ভুতে তুলে নিয়ে গেছে। জ্বীন-ভুতে মানুষ তুলে নিয়ে যাওয়ার কোন অকাট্য প্রমান কেউ কোনদিন দেখেনি তবুও মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই গল্পে বিশ্বাস করে এসেছে। কেউ কেউ বলল মায়ের শোক চাপা দিতে না পেরে সম্ভবত ঐ রাতে কোন এক সময় সেও নদীতে ঝাপ দিয়ে মরেছে। আরো কতজনে কত কিছু যে অনুমান করেছিল তার ঠিক কোন হিসেব ছিলনা।
মায়ের মৃত্যুর একদিনের মধ্যেই অপহৃত হয়ে ফারুখ যখন আমেরিকান গোয়েন্দা হেফাজতে তার জীবনের চরম যাতনার দিন পার করছিল, তখন দিল আফরোজের কাছে খবর গিয়েছিল যে, ফারুখ তার খালাতো বোন সুবহানাকে বিয়ে করে গ্রামে সংসার বেঁধেছে। খবরটি নিরেট মিথ্যে ছিল। এই মিথ্যে, বানোয়াট খবরটা আফরোজকে দিয়েছিল ফারুখের এলাকার সেই ছোট ভাই, আফরোজের ক্লাসমেইট ইমন। স্বার্থের আকার আকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে মিথ্যে কথা বড়, ছোট হয়। মানুষ বড় স্বার্থে বড় মিথ্যে, আর ছোট স্বার্থে ছোট মিথ্যে বলে। এত বড় মিথ্যে খবর আফরোজের কানে দিয়ে ফারুখের উপর তার মনে ঘৃনা তৈরী করাতে চেয়েছিল। এই ঘৃনার বিক্রিয়া ঘটায়ে আফরোজ কে ইমন নিজের দিকে টানতে চেয়েছিল। ইমন নিজেই আফরোজের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল।
মিথ্যের উপর ভর করে পৃথিবীর কোন সম্পর্কই দাড়াতে পারে না। প্রেম, ভালবাসার সম্পর্কও না। মিথ্যে গল্প ফেঁদে আফরোজের মনে ফারুখের অবস্থান নড়বড়ে করে দিতে পেরেছিল ঠিকই কিন্ত সেখানে নতুন করে ইমন নিজের ভালবাসার নাম নিশানার কোন খুটি গাড়তে পারেনি। ইমনের প্রেমের প্রস্তাব আপরোজ নির্দিধায় নাকচ করে দিয়েছিল।
মোবাইল ফোনে হাজার বার চেষ্টা করে, ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে কোন ভাবেই যখন ফারুখের নাম নিশানা কিছু পেল না,তখন দিল আফরোজও বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, ফারুখ তাকে সত্যি সত্যি ফাঁকি দিয়েছে। অথচ সত্যিটা হলো ফারুখ নিজেই অদৃষ্টের এক চরম ফাঁকিতে পড়ে সাত সমুদ্র, তের নদীর ওপারে মার্কিন মলুকে অন্ধকার প্রকোষ্টে পড়ে চরম অনিশ্চয়তায় জীবনের এক একটা দিন কাটাচ্ছিল। অথচ অপন-পর কেউই সে দুর্বিসহ জীবনের খবরের কোন কিছু কোনভাবেই জানতে পারলো না।
ফারুখের অন্য মেয়েকে বিয়ে কারার খবর শুনে আফরোজ কষ্টে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। হলের রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভীষন কাঁদতো। এত বড় ধোকার কথা ভুলতে কিছুতেই তার নিজ মনকে সে শান্তনা দিতে পারছিলনা। বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ গুজে শুধু চিন্তা করতো আর বিষ্ময় নিয়ে নিজেকে একটাই প্রশ্ন করতো-
“এত সব মাখামাখি, এত সব নাম উপনামে ডাকা, এত স্বপ্ন, এত আহ্লাদ সবই কি ছিল ফারুখের প্রবঞ্চনা? ফারুখ, তুমি এতটা ঠক হতে পার কি করে?”
ফারুখের শুন্যতায় তাকে ঘিরে শত সহ¯্র স্মৃতিরা দলঁেবধে আফরোজের চোখের সামনে আয়নার মত যেন জীবন্ত হয়ে ভেসে ভেসে উঠতো আর তাকে তাদের ভালবাসার রঙীন অতীতে ভাসিয়ে নিত। ছোট-বড় সব স্মৃতির ঢেউয়ে অবগাহনে তার অন্তর শুধু ব্যথায় ভিজে সিক্ত হতো। পা ফেললেই ক্যাম্পসের কোনায় কোনায় যেন সে ফারুখকে অনুভবে ফিরে ফিরে পেত। তার মনে হতো ঐ বুঝি ফারুখ তার জন্য কলা ভবনের সামনে দাড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। মনে হতো এই বুঝি ফারুখ তাকে ফোন করে নতুন একটা নাম ধরে তাকে সম্বোধন করছে আর সেটাকে সে মুখে পাগলামী বলে উড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে আনন্দে পাগল হয়ে যাচ্ছে।
এভাবেই মাসের পর মাস অসহ্য এক অন্তর জ্বালায় দগ্ধ হয়ে মনে ভীষণ কষ্ট আর ঘৃনা নিয়ে ফারুখকে ভুলতে এক বছর পরে সোহাগ নামে এক ছেলের সাথে আবার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে আফরোজ। প্রেমের শোক ভুলতে নতুন প্রেম করা লাগে। অনেকটা কাটা দিয়ে কাটা তোলার মত। কিন্তু ফারুখ ছিল অসাধারণ; তার প্রেমের আর্টও ছিল যুগ শ্রেষ্ট। তাকে আফরোজ কতটুকু ভুলতে পেরেছিল তা শুধু আফরোজ জানতো আর আল্লাহ জানতো।
টানা এক বছর দুই মাস পরে আমেরিকায় গোয়েন্দাদের হাত থেকে ছাড়া পায় ফারুখ। গোয়েন্দা ব্ভিাগ তাদের ভুলের জন্য বিশেষ ভাবে দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু শুধু দুঃপ্রকাশ করে কিছু কিছু ভুল কর্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্য হয় না। একজন ছাত্রের দুইটা জীবন থাকে। একটা ছাত্র জীবন আর একটা মানব জীবন। ভুল করে তুলে নিয়ে গিয়ে ফারুখের সেই দুই জীবনের উপর অত্যাচারের যে স্টীম রুলার চালিয়েছিলো মার্কিন গোয়েন্দারা তার একটা মানানসই প্রায়শ্চিত্য করার জন্য তারা ফারুখকে আমেরিকায় বসবাসের বিশেষ অনুমতি পেতে সাহায্য করে এবং বৃত্তিসহ সেখানকার বিশ্বািদ্যালয়ে মাস্টার্স পড়ার সুযোগ করে দেয়। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারা তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে স্বপ্নের মত। ফারুখের ভাগ্য চক্করে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয়ে গেল। এজন্য গুণীজনরা বলে, অদৃষ্টের শেষ খেল না দেখা পর্যন্ত হতাশ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
ফারুখ মুক্ত হয়েই সর্বপ্রথম দিল আফরোজের নাম্বারে কল করতে থাকে কিন্তু বার বারই নাম্বারটি বন্ধ পায়। আফরোজ তার আগের ফেইচবুক আইডিটাও ডিএকটিভ করে রেখেছিল। তাই ফেসবুকেও তার সাথে যোগাযোগ করতে পারলো না ফরুখ। পেরেশান হয়ে সে ইমনের সাথে ফেইচবুক ম্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ করে এবং তার কাছ থেকে জানতে পারে যে, তার দেশের মাটি অন্য একজনের দ্বারা দখলে হয়ে গেছে। ইমন এই খবরটি সত্য দিয়েছিল কারণ এই সত্যের মধ্যে তার আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলে আরাম বোধ করার সুযোগ ছিল। যে ফল নিজে ভোগ করার সুযোগ হয় না সে ফল ভোগে শত্রæ বঞ্চিত হলে কিছুটা শান্তনা পাওয়া যায়।
আফরোজের নতুন প্রণয়ের খবর শুনে ফারুখ মনে ভীষণ চোট পেল কিন্তু সবই ভাগ্যের লিখন হিসাবে মেনে নিয়ে পড়া লেখায় মন দিলো।
এক বছর দুই মাস গোয়েন্দা হেফাজতে আর দুই বছরের মাস্টার্স শেষ করে মোট তিন বছর দুই মাস আমেরিকায় কাটিয়ে ফারুখ দেশে ফিরে আসলো।
দেশে ফিরে দেখতে পারলো বাশার চাচা তার আধা পাগল ছেলে জিয়ার সাথে বিয়ে দিয়ে সুবহানাকে তাদের বাড়ির বউ বানিয়ে নিয়েছে। ফারুখ অপহরণ হওয়ার তিন মাসের মাথায় এই বিয়ে হয়।এতিম সুবহানার একটা গতি হয়েছে দেখে ফারুখের প্রথমত খারাপ লাগলো না। কিন্তু এই পাগলের সাথে সে কেমন করে সংসার করছে সে কথা ভেবে তার কিছুটা সংশয়ও হলো।
দেশের মাটিকে হারিয়ে ফারুখ ইয়েস-নো কে নিয়ে একটু সিরিয়াসলী ভাবতে শুরু করেছিল। ভেবেছিল দেরী হলেও ইয়েস-নো কে বিয়ে করে তার মায়ের একটা বিশেষ ইচ্ছে মরনোত্তর পূরণ করবে। কিন্তু তার ইয়েস-নো যে রুপান্তর হয়ে তার জন্য চিরকালের জন্য ‘নো’ হয়ে গেছে সে কথা সে ভাবতে পারেনি।
খুব শীঘ্রই ঢাকার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারুখের দর্শণ শাস্ত্রের শিক্ষক পদে চাকরী হয়ে গেল। চাকরীটাতে যোগ দিয়ে লেকচারিং আর গবেষনার কাজের মধ্যে ডুবে সব ভুলে থাকার চেষ্টা করতে লাগলো ফারুখ। চাকরীতে শুধু বেতনই পাওয়া যায় না, চাকরীতে আর একটি বড় উপকার হলো এই যে, চাকরী জীবনে কাজের ব্যস্ততা মনুষকে দুনিয়া ভুলিয়ে রাখতে পারে।
কিছুদিন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শণ বিভাগ একটা সেমিনারের আয়োজন করেছিল। সেই সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল “আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রভাব ও প্রজন্মের করনীয়।” জীবনের চলমান ঘটনাক্রমে ফারুখও সেই সেমিনারে বক্তৃতা করতে এসেছিল।
তখনও আফরোজ ঐ বিভাগের একজন ছাত্রী। অনার্স শেষ হয়ে গেছে। শেষ হয়ে গেছে ফারুখের সাথে তার গভীর প্রেমের দিনগুলো। সোহাগের সাথে তার নতুন প্রেমের ট্রেন চলছে আর চলছে মাস্টার্স ক্লাসের পড়াশোনা।
সেমিনারের দিন দর্শন বিভাগের সব ক্লাস সাসপেন্ড করে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের আদেশে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সেমিনারে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।
সকাল দশটা। সেমিনার শুরু হলো। আফরোজ তার বান্ধবী নিপার সাথে গিয়ে সেমিনারে যোগ দিল। নিপা তার সবচেয়ে কাছের বান্ধবী। নিপার কাছে তার প্রেমের, শত্রæতার কোন গল্পই গোপন রাখে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একজন নিকটতম মানুষ থাকে যার কাছে সমন্ত গোপন বলে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যায়। আফরোজের জীবনে নিপা তেমনই একজন।
দুজনে গিয়ে বসলো সেমিনার হলের একদম পেছনের দিকে যাতে ফিস ফিস করে গল্প করা যায়। বাধ্য করে মানুষকে ফিজিক্যালী কোথাও উপস্থিত করা যায় কিন্তু ম্যানটালী উপস্থিত করা যায় না। জবরদোস্তী করে কারো দৃষ্টি ফেরানো যায় কিন্তু তার মনোযোগ ফেরানো যায় না। সেমিনারের গুরু-গম্ভীর কথা বার্তায় আজকালের ছেলে মেয়েদের জম্মের অরুচী। এ জন্য প্রথম বক্তার বক্তব্য শেষ হলো অথচ এই বক্তার পুরোটা সময় ধরে আফরোজ আর তার বান্দবী নিপা গল্প করে করে কাটিয়ে দিল। কারণ তারা ঠিক করে এসেছিল তারা কিছু শুনবে না; মজা করে গল্প করবে।
প্রথম বক্তার জন্য শ্রোতারা করতালী দেওয়া শুরু করলে আফরোজ ও নিপা একটু স্টেজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে একটা ভুয়া হাসি নিয়ে উচ্চ শব্দময় করতালীতে অংশ নিল। অন্যদের তুলনায় তারা দুজন একটু বেশিই জোরে তালু বাজাতে লাগলো। যেন বক্তৃতা না শুনে বক্তাকে যতটুকু ঠকানো হলো জোরছে তালু বাজিয়ে তা পুশিয়ে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা হলো। হাত তালির শব্দ ফুরিয়ে এলো। এরপর তারা একে অপরের দিকে একটু বেকে বসে পুনরায় গল্পে ফিরতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহুর্তে স্টেজ থেকে ঘোষণা আসলো-
“ এবার আপনাদের সামনে সন্ত্রাসবাদের প্রভাব নিয়ে তার গবেষণা ও নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ ফারুখ মোল্ল্যা।”
ফারুখ নামটা শুনে আফরোজ একবারে চমকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে স্টেজের দিকে তাকিয়ে দেখলো, এ হলো সেই ফারুখ যাকে সে ভালবাসতো, যে তাকে চরম ফাঁকি দিয়েছে। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল তার। সে কি ঠিক দেখছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য নিপাকে জিজ্ঞাসা করলো। নিপা ফারুখ কে চিনতো আর আফরোজের সাথে তার প্রেম কাহিনীর প্রায় সমস্তটাই জানতো। নিপা নিশ্চিত করলো যে আফরোজ ঠিকই দেখেছে। এই ফারুখ-ই সেই ফারুখ।
সঙ্গে সঙ্গে আফরোজের দুচোখে পানি ভর করে টলমল করতে লাগলো। তার দুচোখের সেই টলমলে জলরাশিতে প্রচন্ড ঘৃনা ছিল। ছিল অভিমান আর মায়া। এই মিশ্র উপাদানের এক অজানা শক্তির চাপ আফরোজকে হল ত্যাগে উৎসাহিত না করে চেপে, ঠেসে বসিয়ে রাখলো আর ফারুখের কথা না শুনে বরে হতে দিল না।
ফারুখ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাবাদের প্রভাব নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিল। কথা শীঘ্রই তার নিজের জীবনের দিকে নিয়ে গিয়ে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা-দুর্ঘটনার বর্ণনা করে যেতে লাগলো। সবাই তার চরম দুঃখের ঘটনা শুনে একবারে হতবাক হয়ে গেল। স্টেজের উপরে কিংবা নিচে বক্তা কিংবা শ্রোতা- সকলেরই গায়ের লোম খাটা হয়ে উঠলো। সবাই একবারে অশ্রæসিক্ত হয়ে গেল। কেউ কেউ তো কেঁদেই ফেলল। ফারুখ নিজেও কেঁদে ফেলেছিল দু’একবার। কান্না লুকানো যেমন কঠিন , তেমনি আবার সব জায়গা কান্নার জায়গা নয়। তাই বহু কষ্টে ফারুখ তার কান্না চেপেছিল।
বক্তৃতা করার সময়ে স্টেজ থেকে একবার আফরোজের চোখে ফারুখের চোখ পড়েছিল। তখন ফারুখ বেশ কয়েক সেকেন্ড আনমনা হয়ে পড়েছিল। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার কথার তালে ফিরেছিল। যে চোখে চোখ রেখে সেকেন্ড পেরিয়ে মিনিট আর মিনিট পেরিয়ে ঘন্টা হয়ে কেটে যেত, সেই একই চোখে চোখ পড়াতে ফারুখের হয়ত মনে হয়েছিল, সে এই চোখে আর দেখবেনা আফরোজ কে অথবা আফরোজের চোখে চোখ রাখার সমস্ত অধিকার সে হারিয়ে ফেলেছে। যার উপর অধিকার থাকেনা তার উপরে চোখের , মনের কোন কর্তৃত্বই বহাল থাকে না।
সব বলা হয়ে গেল। ভুমিকা, আলোচনা, উপসংহার। সব। হলের মধ্যে আফরোজই মনে হয় সবচেয়ে বেশি মনোযোগী শ্রোতা হয়ে ফারুখের কাহিনী শুনেছিল। আর শব্দ চাপা কান্নায় তার বুক ভেসেছিল।
সেমিনার চলতে থাকলো। পরবর্তী বক্তারা স্টেজে উঠতে লাগলো। কিন্তু আফরোজ ফারুখের বক্তৃতা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই চোখ মুচতে মুচতে সেমিনার হলের পেছন দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।
নিপা তার আসনে বসে রইলো। সে জানতো কি ঘটতে যাচ্ছে। আফরোজ এক পা, দু’পা করে হাটতে হাটতে কলা ভবনের সামনের মাঠে ঠিক সেই চেনা বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানে যেন পাথর হয়ে রুমালে,ওড়নায় মুখ-চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো।
ফারুখও স্টেজ থেকে নেমে সেমিনার হল থেকে বেরিয়ে দ্বিধা-সংকোচে আস্তে আস্তে সেই বটগাছের দিকে এগিয়ে গেল। দেখলো আফরোজ এখানে তার থেকে উল্টো দিকে মুখ করে দাড়িয়ে আছে। ফারুখ দু-এক পা দূরুত্ব রেখে আফরোজের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। এভাবে দাড়িয়ে কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। দুজনের কারো মুখ কেউ একটা কথা কেউ বের করতে পারল না। আফরোজের থেকে ফুফিয়ে কান্নার আওয়াজ আসতে লাগলো। ফারুখের চোখ ভিজে নিঃশব্দে পানি পড়তে লাগলো। এভাবে খ্ানিকটা সময় পেরিয়ে গেলে ফারুখ মুখ খুলে কান্নাভেজা কন্ঠে, কম্পনরত ঠোটে বলে উঠলো-
“ দেশের মাটি।”
এতদিন পরে এই প্রিয় ডাকটি শুনে আফরোজের মনের ভেতরে একেবারে উলোট-পালট হয়ে গেল। যেন টানা এক গ্রীষ্ম রোদে পোড়া দীর্ঘদিন মালির অনুপস্থিতিতে শুকিয়ে পলতে হয়ে যাওয়া ফুলগাছটা হঠাৎ পুরাতন পরিচিত সিঞ্চনের পানির ঝর্র্না বিন্দু পেয়ে একেবারে শেকড়ে-পাতায়-মাথায় প্রাণ ফিরে পেল।
সেমিনারে বক্তৃতায় সব প্রাকাশ হয়ে যাওয়ার পরে আফরোজের কাছে ফারুখের কোন কৈফিয়ত আর বাকী রইলো না। কিন্তু তার দেশের মাটি যে ইতোমধ্যেই বেদখল হয়ে অন্য কারো হৃদয়ে শাসিত হচ্ছে সেখান থেকে তাকে ছাড়ায়ে নিতে ফারুখের কোন উৎসাহ হল না। নিরুপায় আফরোজ ঘুরে দাড়ায়ে ফারুখ কে প্রশ্ন করলো-
“ফারুখ, আমি এখন কি করব?”
ফারুখ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল-
“নদী ভাঙনে আমার মা গেছে, ঘর গেছে। আর মনের ভাঙনে আমার দেশের মাটি গেছে। আমি জানি ভাঙনে যা যায় তা ফিরে আসার নয়।”
এই বলে এক পা, দু’পা করে পেছনে হেটে ফারুখ আবার সেমিনারে ফিরে গেল আর তার দেশের মাটি সেখানে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে তার দিকে অপলক চেয়ে রইলো।
(সমাপ্ত)
গল্প (দুই)ঃ
ছেদ
-সাঈফ আলম
(৪ আগষ্ট,পুটিয়া, ঝিনাইদহ)
একদিন দুপুর তিনটার দিকে মালয়েশিয়া থেকে লাল চানের বাড়িতে ফোন আসলো। লাল চাঁন লালও নয়, আবার চাঁনও নয়। তবুও সে লালচাঁন। তবে লাল বাদে এখন মানুষ তাকে শুধু চাঁন বলেই বেশি ডাকে। যদিও চাঁনের মত সে কারো কাছে কাঙ্খিত নয়।
তিন বছর ধরে সে মালয়েশিয়া আছে। এই দুপুর বেলা সাধারণত লাল চাঁন বিদেশ থেকে বাড়িতে ফোন করে না। কারণ বাংলাদেশের এই টাইমে সে মালয়েশিয়ায় কারখানায় কাজে ব্যস্ত থাকে। কাজের সময় মোবাইলে কথা বলা মালয়েশিয়ান বসগণ পছন্দ করে না। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে মোবাইলে দেশে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়লে গালি দেয়। মালয়েশিয়ান ভাষার গালি। কাটা ভাঙা ইংলিশ গালিও দেয়। যেমন ইউ বøাডি হেল। যে কোন ভাষায় কেউ রেগে মেগে গালি দিলে ভাষা না বোঝা গেলেও গালি যে দিচ্ছে তা বোঝা যায়।
শুধু বাড়ির ভালর জন্য লাল চাঁন এর মত অভাবী মানুষেরা বিদেশ যায়। সেই বাড়ির খবরই তাদের কাছে বড় খবর। বড় খবরের আশায় বিদেশে তাদের সবচেয়ে বড় পেরেশানি হয়। তাই লাল চাঁন সকালে কাজে যাওয়ার আগে একবার আর কাজ থেকে ফিরে রাতে আর একবার বাড়িতে ফোন দেয়।অনেকটা রুটিন হয়ে দাড়িয়েছে। রুটিন কাজে এক সময় বিরক্তি আসে । দূর দেশে থাকলে বাড়ির জন্য অবিরাম মন পোড়ে মানুষের। তাই প্রতিদিন যোগাযোগ করতে কারো বিরক্তি আসে না। লাল চাঁনেরও আসে না।
চাঁন মিয়া ইমোতে ভিডিও কল দেয়। কথা বলে। দেশের ভিটে মাটি, মা, বউ আর মেয়ের চলচ্চিত্র দেখে। খুব শান্তি পায়। সারা দিনের তপ্ত পরানটা জুড়ায়ে যায় তার। আপন মানুষের মুখচ্ছবি দেখে মানুষ যত শান্তি পায় অন্য কোন কিছু দেখে তত শান্তি পায় না। অবার এই মুখ যদি অপ্রিয় হয়, যদি শত্রæর মুখ হয়, তাহলে সে মুখ দেখে মানুষের যত অশান্তি হয় অন্য কোন কিছু দেখে তত অশান্তি হয় না। মা, বউ, আর মেয়ে টুনটুনি । এই তিনটে সোনার মুখ লাল চাঁন দেশে ফেলে গেছে। প্রতিদিন এই মুখ তিনটি দেখে বিদেশে তার পোড়া অন্তর শীতল হয়।
নিয়ম করে প্রতিদিন ভিডিওতে প্রিয়জনদের মুখ দেখে আর সে প্রিয় মুখের কথা শোনে বলে লাল চাঁনের মনেই হয়না যে, সে বাড়ির মানুষদের থেকে দূরে আছে। প্রযুক্তি এভাবে দূরকে নিকটবর্তী করেছে। বিশেষ করে ছোট্ট মেয়েটাকে না একদিন দেখলে, তার মুখের নানান হাসির আর মজার মজার কথা না শুনলে বিদেশে রাতে লাল চাঁনের ঘুমই আসে না। শুধু কর্ম কøান্তিই মানুষের চোখে ঘুম আনতে পারে না। সাথে মনের শান্তিও দরকার হয়। কারণ বিশেষে কোনদিন রাতে বাড়িতে কথা বলতে না পারলে লাল চাঁনের রাত ঘুমহীনভাবে অশান্তিতে পার হয়ে যায়, আবার পরের দিন সকালে কাজে গিয়েও কোন কিছুতে মন লাগাতে পারে না। সমস্ত দুনিয়া থেকে সে যেন বিয়োগ হয়ে থাকে।
সেদিন দুপুরে যখন ফোন আসে তখন লাল চাঁনের বউ বিলকিস বাড়ির বাইরে ছিল। পাড়ায় গিয়েছিল একটা কাজে। গ্রামের মহিলাদের বেড়ানোর স্থান প্রধানত দুইটা। এক হলো পাড়া। প্রতিদিন পাড়া না বেড়ালে এদের পেটের ভাত হজম হয় না। শহরে গ্রামের মত পাড়া থাকে না। তাই পাশের ফ্লাটের বাসিন্দারাও পর মানুষ হয়ে থাকে আজীবন। গ্রামের মহিলাদের বেড়াতে যাওয়ার দ্বিতীয় স্থানটা হলো বাপের বাড়ি। এটা অবশ্য বাৎসরিক। বছরে দু’একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পায় তারা।
পাড়ায় যাওয়ার সময় বিলকিস মোবাইলটা ফোনটা ঘরে বিছানার উপর রেখে গিয়েছিল। ঘরের দরজা খোলা ছিল। এখনো গ্রামে ঘরের দরজা খুলে পাড়া বেড়িয়ে আসা যায় নিশ্চিন্তে। গ্রামে ফোন চুরি হয়না। গ্রামের মানুষ সাধু হতে না পারলেও অনন্ত চোর হয় খুব কম। দ’ুএকটা ছ্যাছড়া চোর থাকলেও থাকতে পারে। শহরে শিক্ষিত চোর বেশি। এরা কলম দিয়ে চুরি করে। কলমের জোর বেশি তাই চুরিও করা যায় বড় রকমের। শহরে ছ্যাছড়া চোর আরোও বেশি। ছয়তলা থেকেও ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি চোরের হাত থেকে বাঁচানো যায় না।
পরপর কয়েকবার ফোনটা বেজে উঠলো। চাঁনের মা মাজু বেগম শুনতে লাগলো আর বউমাকে ডেকে মরতে লাগলো। সে নিজে কিভাবে ফোন কলের জবাব দিতে হয় তা বোঝেনা। তার সময় এসব যন্ত্র সে বাপের জন্মে কোনদিন দেখেও নি, শোনেও নি। ছেলের সাথে কথা বলতে তাকে এ যন্ত্র ধরায়ে দিলে সে কখনো স্ক্রিন সাইড বাইরের দিকে ধরে আবার কখনো স্পিকারযুক্ত মাথা নিচের দিকে ধরে। ফলে কিচ্ছু শুনতে পায়না। শুধু হ্যালো হ্যালো করে ক্লান্ত হয়। এসব কান্ড দেখে তার বৌমা শুধু হেসে ক্ষুণ হয়। তার পাঁচ বছরের নাতনী টুম্পাও হেসে মরে। শ্বাশুড়ীর প্রজন্মের সাথে বউমা আর নাতনীর সময়ের কি বিস্তর ব্যবধান! এই কালে মাজু বেগমরা কতটা অচল! নাতনী, বেটার বৌ উভয়ে বহুবার শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে মোবাইল ফোন কানে ধরে কথা বলতে হয়। তবুও সে পারে না। নিজে নিজে ফোন রিসিভ করা তো তার পক্ষে আরো অসম্ভব কাজ। মাজু বেগম এ কাজটা করতে পারলে সম্ভবত এটা হতো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কিংবা নবম।
অনবরত ফোন বাজতে থাকায় মাজু বেগম ঘরের ভেতর থেকে ফোনটা নিয়ে পাড়ায় বৌমাকে খুজতে বের হলো। মাজু বেগমদের সময় পাড়া বলতে ছিল আশে পাশের দু’এক বাড়ী। তার বাইরে না। আজকালের বৌদের জন্য পাড়ার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এখন পাড়া বলতে প্রায় পুরো গ্রাম।
মাজু বেগম তার বৌমাকে বাড়ি বাড়ি তালাশ করতে থাকলেন আর ফোন কল অনবরত বাজতে থাকলো। “তোমায় দেখলে মনে হয়…”। এই গানটা রিংটনে দেওয়া ছিল। ওটা বাজতে লাগলো। যারা মাজু বেগমকে যেতে দেখলো আর “তোমায় দেখলে মনে হয়” শুনলো তারা সবাই হাসতেছিল। তারা ভেবেছিল এটা গান। কিন্তু এটা ছিল কল রিংটন। এই রিংটনটা মাইকের মত আওয়াজ করে বাজতেছিল। মাজু বেগমের হাতে মোবাইল ফোন। আবার পাড়া বরাবর গান বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে। এ পাড়ায় এটা ভীষণ আশ্চর্য এক দৃশ্য। তাই বিস্ময় নিয়ে মানুষ শুধু তার দিকে তাকাচ্ছিল আর হাসতেছিল। এভাবে নয়টা বাড়ি পাড়ি দিয়ে মাজু বেগম বৌমাকে খুজে পেল বিলার বাড়িতে। দেখলো চাঁনের বউ বিলার বউ এর কাছে বসে গল্প করছে। বিলার বউ দর্জিগিরি করে। লাল চানের বউ তার কাছে ত্রিপিচ বানাতে দিয়েছিল। ত্রিপিচ পরা মাজু বেগমের পছন্দ না। তার পছন্দ শাড়ী। কিন্তু বিলকিসের শাড়ী পরতে ভাল লাগে না। শাড়ী পরলে তাকে নাকি খ্যাত খ্যাত দেখায়।
“বৌ মা, ধর ধর, মোবইল ধর। সেই কখন থেকে বাজেই যাচ্ছে। সারা পাড়া খুজে বেড়াচ্ছি আর তুমি এখানে আইসে মরে রয়েছ? দেখ মনে হয় লাল চাঁন ফোন করতেছে?”
এই বলে বৌমার হাতে মোবাইল দিতে না দিতেই কলটি আরো একবার বিফল হলো। চাঁনের বউ কল লিস্টে চোখ বুলিয়ে দেখতো পেল এ পর্যন্ত উনিশ বার কল করা হয়েছে বিদেশী একটা নাম্বার থেকে। নাম্বারটা একেবারেই অপরিচিত। এটা চাঁনের নাম্বার না। তার নাম্বার বিলকিসের মুখস্ত। তাছাড়া “আমার জান চাঁন” বলে সেভ করা। তার নাম্বার হলে তার নাম উঠতো।
অচেনা নাম্বার থেকে একটানা এতবার কল করছে কেন? কিসের একটা যেন ভয় হতে লাগলো বিলকিসের। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করা শুরু হয়ে গেল। এমন সময় ঐ নাম্বার থেকে আবার কল আসলো।
“হ্যালো।”
“হ্যালো কিডা?”
“এটা কি বিলকিস ভাবীর নাম্বার?”
“জী”। আপনি কে? এতবার ফোন দিচ্ছেন যে?”
“ভাবী আমার নাম ঝন্টু। মালয়েশিয়ায় আমি আর লালচাঁন ভাই এক সাথে থাকি । আমার বাড়ি মাগুরায়।”
“ও আচ্ছা। ভাল আছেন ভাই?”
“জ¦ী আমি ভাল আছি। কিন্তু ভাবী লালচাঁন ভায়ের একটা সমস্যা হয়ে গেছে।”
কথাটা শুনেই বিলকিসের জান খাচাঁ ছাড়া হয়ে গেল।
“ও আল্লাহ গো! তার কি হয়েছে?”
এই বলে সে হাউমাউ করে কান্নাকাটি লাগিয়ে দিল। বউমার পাশেই দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছিল চাঁনের বৃদ্ধ মা। সেও কিছু না বুঝেই হাউমাউ করে উঠলো-
“ওরে সোনা। আমার মানিকের কি হয়েছে, বৌমা? কি বিপদ হয়েছে রে তার? ও আল্লাহ, ও আল্লাহ, আমার যাদুর কি হয়েছে রে?”
ইতোমধ্যেই মোবাইলের অপর প্রান্ত থেকে ঝন্টু সাহেব ইনিয়ে বিনিয়ে লালচাঁনের দঃসংবাদটা বলে শেষ করলেন। অনেক কষ্ট হলো বলতে। দুঃসংবাদ নিজে শোনা ও অপরকে জানানো দুটোই শক্ত কাজ। দুর্বল চিত্তের মানুষ এই শক্ত কাজ দুটির একটিও করে মানসিকভাবে সোজা থাকতে পারে না। ঝড়ে গাছ ভাঙার মত ভেঙে পড়ে। বেদনায় দুমড়ে, মুষড়ে যায়।
মোবাইল রাখার পূর্বে ঝন্টু সাহেব বিলকিস ভাবীকে কিছু শান্তনাও দেওয়ার চেষ্টা করলেন। দুঃখে ভেঙে পড়া, কান্নারত মানুষকে বেশি শান্তনা দিলে অপচয় হয়। অধিকাংশই সে শুনতে পায় না ভাল করে। কারণ একজন মানুষ একই সময়ে দুইটা কাজ সমান মনোযোগ দিয়ে করতে পারে না। এটা মনোবিজ্ঞানীদের কথা। ঝন্টু সাহেব মিসেস চাঁনকে শান্তনা দিয়ে বলল-
“ভাবী, ভেঙে পড়বেন না। চাঁন ভাই তো তবুও জানে বেঁচে আছে। কতজন তো ভাবী লাশ হয়ে বিদেশ থেকে বাড়ি ফেরে।”
শান্তনার এই সরল বাক্য তিনটে খরচ করে পরে সর্বশেষ খবরা-খবর জানাবে বলে ঝন্টু সাহেব আপাতত ফোন কেটে দিলেন।
ফ্যাক্টরীতে কাজ করার সময় সেদিন দুপুর বারটার দিকে দুর্ঘটনাক্রমে মেশিনে লালচাঁনের ডান পাটা হাটুর নিচ থেকে কাটা পড়েছিল। একদম দেহ থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর এই দুর্ঘটনার কথাটা তার বাড়িতে জানাতেই মালেয়েশিয়া থেকে একের পর এক কল করে যাচ্ছিল ঝন্টু সাহেব।
গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে খসে পড়লে গাছ তবুও চলতে পারে। কারণ গাছের চলা বলতে একস্থানে দাড়িয়ে থাকা বোঝায়। কিন্তু মানুষের শরীর থেকে কোন অংগচ্ছেদ ঘটলে মানুষ চলতে পারে না। কারণ মানুষের চলা বলতে দেহটাকে একস্থান থেকে দুনিয়াব্যাপী চরে বেড়ানো কে বোঝায়। পেট চালানো বোঝায়। সংসার চালানো বোঝায়।
এক পা হারিয়ে বিদেশে লালচাঁন তার কোম্পানির বিবেচনায় অচল হয়ে গেলেন। লালচাঁনের ব্ঙাালী সহকর্মীরা সবাই তার পক্ষে তার কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের যথেষ্ঠ আবেদন-নিবেদন করেছিল। কিন্তু শেষমেষ ক্ষতি পূরণ তার কপালে জোটেনি। শুন্য দু’হাতে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। শুধু বিমান ভাড়াটা দিয়েছিল কোম্পানি। সেটা ঐ অচল উড়িয়ে দূর করার জন্য।যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ বাস। এই হলো বিদেশে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের বসবাসের সূত্র, শর্ত। দেশে, বিদেশের অনেক কোম্পানি সস্তা শ্রমিকদের এভাবে শুধু ক্ষতিই করতে পারে, কিন্তু ক্ষতি পূরণ করে দিতে পারে না।
লাল চাঁনের মা ছেলের পা কাটা পড়ার খবরটা শুনে একেবারে পাগল হয়ে গেল। মনে হলো তার সোনার চাঁনের পা নয়, যেন তার কলিজাটাই কাটা পড়েছে। সন্তানের সাথে মায়ের কলিজাটা লটকানো থাকে। লইলী-মজনুর কাহিনীতে লাইলীর গায়ে চাবুক কষলে মজনুর পিঠে তার দাগ ওঠেছিল। একথা আষাড়ে গল্প। এই গল্পে সবাই মজা পায়। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। তবে ছেলের ক্ষতিতে মা ক্ষতবিক্ষত হয়। একথা চরম সত্য। জানোয়ার ছাড়া সবাই এ সত্য বিশ্বাস করে। চাঁনের মা ছেলের জন্য শুধুই বিলাপ করে বেড়াতে লাগলো। খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। শুধু কাঁদতো আর কাঁদতো।আর আল্লাহকে প্রশ্ন করতো-
“আল্লাহ, আমার পা দুডো ক্যান নিলে না, আল্লাহ? ক্যান আমার সোনার চাঁনের পাটাই, দেখলে তুমি? আমার সোনার চাঁন এখন কি করে হাটবে রে, আল্লাহ?”
একদিন পাড়া থেকে কিছু মানুষ লালচাঁনকে দেখতে আসলো। তাদের কাছে লালচাঁনের মা জিজ্ঞাসা করলো-
“শুনিচি আজ কাল কত উপায় বের হয়েছে। কত যন্ত্রপাতিও হয়েছে। একজনের চোখ আর এক জনের চোখে লাগায়ে দেয়। এক জনের কিডনি আর একজনের পেটে ঢুকায়ে দেয়। আমার একটা পা কেটে আমার লালচাঁনরে লাগায়ে দেওয়া যায় না? সিরাম কোন ব্যবস্থা নেয়?”
একথা শুনে সবাই বড়ই আপসোস করলেন। আর ভাবলেন, আহা রে! এর নামই তাহলে মা! সবাই চাঁনের মাকে জানালেন যে, এরকম কোন ডাক্তারী ব্যবস্থা আছে বলে তাদের জানা নেই।
ঘটনার পর প্রায় মাস হয়ে গেল। লালচাঁন দেশে ফিরে আসলো। তিন বছর পর ফিরে আসলো। সেই একই লালচাঁন। শুধু একটা পা নেই। সেই মাথা আছে শুধু চুলগুলো ঝরে টাক হয়ে গেছে। সেই হাত দুটো আছে তবে তা শূন্য, কোন টাকা পয়সা নেই।কাটা পাটা তখনো পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। ঘা পুরোপুরি শুকাইনি। গরীবের ঘা শুকাতে দ্বিগুণ সময় লাগে। কারণ গরীবের ঘা শরীর-মন উভয়কেই সমান জোরে গভীরে আঘাত করে।
এক মাস, দু’মাস করে সময় চলে যেতে থাকলো। কিন্তু লালচাঁনের সংসার অচল হয়ে আসতে লাগলো। বসে খেলে রাজার ধনেও কুলায় না। লালচাঁন রাজা নয়। প্রজাদের মধেও সে হতভাগা। তার এখন রিক্ত হস্ত। এভাবে বসে বসে তার আর কয় দিনই বা চলে। সংসারে লালচাঁন ব্যতীত উপার্জনের জন্য দি¦তীয় আর কোন পুরুষ নেই। বাবা মারা গেছে সেই ছোট কালে। বাবার কথা কিছু মনে নেই লালচাঁনের। ছোট কালের কথা সবার মনে থাকে না। যাদের থাকে তারা বড় হয়ে খুব গল্প কথক হয়। লাল চাঁন গল্প বলে না। আজ সে নিজেই গল্পের লোভনীয় বিষয় বস্তু।
লালচাঁনের আর কোন ভ্ইা-বোনও নেই। সেই পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। মাতা পিতার একমাত্র সন্তান হলেই ভাল থাকা যায়, ভাল পরা যায়, ভাল খাওয়া যায় – এমন কোন কথা নেই। অর্থ থাকলে দশ ভায়েরও চলে। না থাকলে, এক জনের ও আটকে যায়।
দেড় কাঠার এক ভিটে মাঠি। তার উপরে দুই রুমের এক টিনের ছাপড়া ঘরে লালচাঁনের বসবাস। আর মাঠে ছয় কাঠার একটা আবাদী জমি। আবাদ যা হয় তাতে তাদের সারা বছর পেট চলেনা। পেট জমির ধার ধারে না। সে শুধু খাদ্য চেনে। খাদ্য ফুরালেই সে খাদ্য চায়। লালচাঁনের সম্পদ বলতে বাড়তি কিছু আর নাই।
চারটি পেটের খাদ্যের চিন্তায় লালচাঁন তার সেই ছয়কাঠা জমি বিক্রি করে দিল। ক্রয়-বিক্রয় মানুষ প্রয়োজনে করে। তবে শেষ সম্বল বিক্রি করে দিতে মানুষের অন্তর কেঁদে যায়। লালচাঁনেরও অন্তর কাঁদতে লাগলো। কেঁদে শিশুদের লাভ হয়। কারণ কাঁদলে শিশুদের খাদ্য, খেলনা ইত্যাদি প্রাপ্তী হয়। অন্যান্য অবদার ও পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু বড়দের কেঁদে লাভ হয় না। কাঁদলে বড়দের কেবল হ্রদপিন্ড অকেঁজো হতে থাকে।
জমি বিক্রির টাকা দিয়ে লালচাঁন একটা গাভী গরু কিনলো। আর বাড়ির অদূরে রাস্তার ধারে একটা মুদি দোকান দিল। ভ্যানে চড়ে বাজার থেকে মাল কিনে এনে দোকানে বেচাকেনা শুরু করে দিল। কিন্তু মানুষ খুব বাকী খায় তার দোকান থেকে। বাকী টাকা চাইলে কেউ দিতে চায় না। ধানাই পানাই্ করে। ফলে মহাজনের কাছেও দেনা বাড়তে থাকে।
গাভীটি সাত মাসের গর্ববতী ছিল। আর তিন মাস পরে বাচ্চা হবে। লালচাঁন চায় এঁড়ে বাছুর হোক। এঁড়ে গরু বড় করে কোরবানীর সময় বিক্রি করলে ভাল পয়সা পাওয়া যায়। এছাড়াও গাভীর দুধ বিক্রি করেও কিছু টাকা হবে। এই আশাতে গাভীটির খুব খাতির যত্ন চলতে লাগলো।
লালচাঁনের বৃদ্ধ মার সাথে গাভীটির গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে গাভীটিকে বাড়ির আশে পাশে নিয়ে গিয়ে ঘাস খাওয়াতো। মাথায় হাত বোলাতো। গরুর মাথায় হাত বোলালে গরুরা খুব খুশী হয়। আহ্লাদে আরো এগিয়ে এসে গা ঘষতে থাকে, ঘাড়,গলা, মাথা এগিয়ে দেয়, চাটাচাটি করতে চায়। শয়তান মানুষের মাথায় হাত বুলালেও খুশি হয় না। এরা অন্যের সাথে গা ঘেষে চলে সুযোগ বুঝে ক্ষতি করার জন্য।
একদিন গাভীটকে বাড়ির পাশে এক খন্ড পতিত জমিতে খুটো মেরে ঘাস খাওয়ার জন্য রেখে আসে লালচাঁনের মা। বুড়ো মানুষ। গায়ের জোর সব গেছে। মুগুর বাড়িয়ে খুটো মাটির গভীরে পুতে দিতে পারে না। মেয়ে মানুষের চেয়ে মেয়ে গরুর গায়ে জোর অনেক বেশি। লালচাঁনের মা বাড়িতে চলে আসার পর গাভিটি খুটো উপড়ে ফেলে পাশে তফসের বিশ্বাসের জমিতে গিয়ে ধান খেতে থাকে। । কাঁচা ধান গাছ খেয়ে পেট মোটা করে ফেলে। পরের ধন মেরে খেয়ে অনেক মানুষেরও পেট পটকা মাছের মোটা হয়ে যায়। তবে তারা হজম করে ফেলে। গরুও হজম করে ফেলে। হজম শক্তিতে গরু আর ঘুষ খোররা সমান।
তফসের বিশ্বাস গরুতে তার জমির ধান খাওয়ার দৃশ্য দেখে চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করলো আর অশ্রাব্য গালি ঝাড়তে লাগলো। তার মুখ খুব খারাপ। তার কথায় মানুষের হদয় কাটে। আর তার কাজ কর্মে মানুষের হ্রদয় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। লোক ঠকিয়ে বিস্তর জমিজমা করেছে জীবনে কিন্তু তার হ্রদয় জমিন চিরকালই সংকীর্ণই রয়ে গেছে। দুনিয়ার এক কৃপন সে। কৃপন মানুষ নিশ্চিত বড় লোক হয়। তবে ধনে, মনে নয়।
গালিগালাজের আওয়াজ শুনে লাল চাঁনের মা ছুটে গিয়ে দেখলো তার গাভীটিকে ধরে জোর করে টেনে টেনে খাওয়াড়ে দিতে নিয়ে যাচ্ছে তফসের বিশ্বাস। এ সমাজে অবলা পশুকে ধরেই অনায়াসে খাওয়াড়ে দেওয়া যায়। অথচ সব খেয়ে দেশ শেষ করে ফেলা হারামীদের ধরে মানব খোয়াড়ে ভরে দেওয়া অত সহজ হয় না । বুড়ি দৌড়ে গিয়ে তফসের ব্শ্বিাসের পা জড়ায়ে ধরলো। কান্নাকাটি করে বলল-
“ভাই, মাপ করে দাও। আমার গরুটাকে মাপ করে দাও, ভাই। আমাগের এমনিই বিপদের শেষ নেই, ভাই। গরুটারে খোয়াড়ে দিলি আর ছাড়াতি পারবো নানে। এট্টা পয়সা নেই ঘরে। তোমার দোহায় নাগে, এই সব্বনাশটা করে না, ভাই।”
এই বলে গাভীর গলার দড়ি ধরে লাল চানের মা পেছনের দিকে আর তফসের বিশ্বাস সামনের দিকে গাভীটিকে টানাটানি করতে লাগলো। এক পর্যায়ে ধাক্কা মেরে বুড়িকে মাটিতে ফেলে দিয়ে গাভীর দড়ি হ্যাচকা টান দিয়ে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গরুটাকে নিয়ে গিয়ে সোজা খোয়াড়ে ঢুকায়ে দিয়ে আসলো নির্দয় তফসের বিশ্বাস।
সারা দিন ধরে লাল চাঁনের মা গরুটার জন্য চোখের জল ফেলতে লাগলো আর আহাজারী করতে লাগলো। কি করে, কিভাবে তার গাভীটাকে মুক্ত করে আনবে সেই চিন্তা করে মরে যেতে লাগলো। গরুটার জন্য মায়ের ছটফটানি আর কান্নাকাটি দেখে অসহায় লালচাঁন মাকে আশা দিয়ে বলল-
“মা কান্দিস নে। যে ভাবেই হোক সন্ধ্যের আগেই তোর গরুটাকে ছাড়ায়ে আনবানে।”
গরুর জেল হওয়ার ঘটনায় বাড়িতে ছেলের বউ বিলকিস অবশ্য খানিকটা এক পাক্ষিক জগড়া বইয়ে দিল । শ্বাশুড়ির উপর রাগ ঝাড়লো বেশ খানিকটা। ইদানিং বিলকিস সব কিছুতেই রাগারাগি করে কথা বলে। স্বামীকে আর দুচোখ পেতে দেখতে পারে না।খুব হেলা-তাচ্ছিল্য করে। গালি দেয়। খোটা দেয়। স্বামীকে সম্বোধনের জন্য তুমি থেকে এখন তুই তে চলে এসেছে। পুরুষ মানুষের পয়সা না থাকলে বউ এর কাছে তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে যায়। হাতে পয়সা আসা শুরু করলে আবার বউ এর আদর যত্নও ফেরত আসা শুরু করে। চাঁনের বউ শাশুড়ির আর স্বামীর উপর পরোক্ষভাবে রাগ ঝাড়তে ছোট মেয়েটারে ধরে ধরে মারে। পরিবারে বড়দের উপর রাগ হলে তা প্রকাশ করতে শিশুদের আর বাসন কোসনকে বলির পাঠা বানায় মানুষ। গরু খাওয়াড়ে যাওয়ার ঘটনায় বিলকিস বেগম শ্বাশুড়িকে ধমক দিয়ে কৈফিয়ত চাইলো এভাবে-
“হাতে কি তেল দিয়ে গরু বাইন্দিছিলে? খুটো উপড়ে ফেল্ল কি করে? তোমার ভাতার তো তালুক রেখে গেছে। এখন যাও সেই তালুক বেচে গরু খালাস করে আনো গে। আমি কিছু জানিনে। আমার বা পা কান্তেছে গরু খালাস করার জন্যি। যা পারিস তুই আর তোর খোড়া বিটা কর গে যা।”
লাল চাঁনের দোকানে কেজি দুই চাল জমে ছিল। কোন কোন বাড়ির বউরা চাল দিয়ে বিনিময়ে সদায় নেয় তার দোকান থেকে। এমনি কেউ কখনো তাকে এক মুঠো চাল দিতে আসে না। সন্ধ্যায় দোকানের সেই দুই কেজি চাল দিয়ে খোয়াড় থেকে গরুটাকে মুক্ত করে আনে চাঁনের মা। কিন্তু সেই রাতের কোন এক প্রহরে গরুটি সবার অগোচরে খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়ে গোয়ালের মধ্যেই মরে পড়ে থাকে। গরুটির পেট ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। জিহবা বের হয়ে ছিল। চোখ দুটো উল্টে ছিল। মৃত্যুর আগে খুব কষ্ট হলে মানুষ পশু সবারই চোখ উল্টে যায়। গাভীটির নাক, মুখ দিয়ে ফ্যানা ঝরছিল। পরে জানা গিয়েছিল তফসের বিশ্বাস ঘটনার আগের দিন তার ধানে বিষ দিয়েছিল। এটা খুব মারাত্মক বিষ ছিল। বিষ দিলে অপকারী পোকার সাথে সাথে উপকারী পোকাও মারা পড়ে। উপকারী গরু ছাগল ও মারা পড়ে। লালচাঁনের গাভীটা তাদের উপকারে আসার আগেই মরে গেল। বড় আর একটা ক্ষতি হয়ে গেল লালচাঁনের সংসারে।
গরুটা মরে যাওয়ার পরে লালচাঁন চিন্তায় ভেঙে পড়লো। তার চিন্তাটা অর্থনৈতিক। তার মায়েরটা তারও অধিক কারণ গরুটা তার ভাল একজন সাথী ছিল। সময় কাটানোর উপায় ছিল। তাকে ঘিরে তার স্বপ্ন ছিল। লালচাঁনের বর্তমান চিন্তা কি করে তার সংসার চলবে এবার। সংসারের চিন্তা একজন সংসারীর সবচেয়ে বড় চিন্তা। সন্ন্যাসীর সে চিন্তা থাকে না কারণ সে চিন্তার ভার সে বইবে না বলেই সংসার দ্যাগ করে গৃহ হতে পথে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সংসারীর যখন কপাল দোষে গৃহ হারিয়ে পথে বসার উপক্রম হয় তখন ভাবনায় তার শরীরের অবশিষ্ট বল টুকু ফুরিয়ে আসতে থাকে। দুচোখে শুধুই অন্ধকার দেখে। লালচাঁনও তেমন সামনে শুধুই ঘোর অন্ধকার দেখতে লাগলো।
প্রিয় গরুর শোকে আর তার লালচাঁনের চিন্তায় মাজু বেগম হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন। একেবারে বাক শক্তিও হারিয়ে ফেললেন।শরীরের বাম পাশটা অচল, অবশ হয়ে গেল। বুড়ো শরীর নানান রোগের বসতঘর। কোন ওষুধ এ ঘর বাঙতে পারে না। লালচাঁনের পক্ষে তার মায়ের চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা ছিলনা। দোকান থেকে সারাদিন যা আয় হয় তাই দিয়ে কোন মতে কষ্টে দিন যায় রাত আসে। গ্রামের শরাফত ডাক্তার কে ডাকলেও আসতে চায় না। গরীবের চিকিৎসা করতে কেউ আসতে চায় না।শহরের বড় ডাক্তার কিংবা গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার কেউই না। একালে সবাই ডাক্তার হয় পয়সা কামাবার লক্ষ্যে। গরীবের সেই পয়সা থাকে না।তাই তাদের কাছে ডাক্তার যেতে চায় না। গরীব মানুষ তাদের লক্ষ্য নয়। দু’একজন ভাল ডাক্তারও আছে। কিন্তু এত বড় দেশে দু’একজন ভাল ডাক্তার দিয়ে আপনি কি করবেন? অনেক বার খবর দেওয়ার পর শরাফত ডাক্তার এসে দেখে বলল যে, বুড়ির ব্রেইন স্ট্রোক করেছে। দ্রæত শহরে নিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে।
রাতে স্ত্রীর সাথে মায়ের চিকিৎসার উপায় নিয়ে আলোচনা তুলতেই চাঁনের বউ একবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো-
“বুড়ি মানুষ মরলে কি?” আর কত বাচঁবে? আর বেঁচে থেকেই বা কি উদ্ধার করছে আমাদের, শুনি?”
এমন নিষ্ঠুর কথাটা শুনে লালচাঁনের হ্রদয়টা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। দুঃখ ও রাগ নিয়ে বউ’র কথার জবাবে বলল-
“মা টা তো আর তোমার না। এই মা টা যে শুধুই আমার মা। তাই এ রকম নিষ্ঠুর কথা বলতি পারলে। তোমার মা হলি আজ ইরকম করতে পারতে না।”
“থাক হয়েছে । বড় মা ভক্ত হয়েছে রে। পথের ভিখেরি আবার মা’র চিকিৎসা করাবে।” বিলকিস বলল।
“ দোকান বিক্রি করে দিয়ে আমি মাকে শহরে নিয়ে চিকিৎসা করাবো।”
এ কথা বলতেই লালচাঁনের বৌ বসা অবস্থা থেকে একবারে দাড়িয়ে গেল। রেগে অগ্নিমুর্তি হয়ে বলল-
“ও রে আমার গোলামের কথা শোন দেখি। বলি গোলামের ঘরের গোলাম, দোকান বেচলি গিলিবিনি কি? তোর মেয়ের মুখি ভাত জুটপেনে কি করে?”
মায়ের জন্য ভারাক্রান্ত মনের ভিতরে স্ত্রি বিলকিসের এক একটা গালি যেন একটা করে ধারালো ছুরির মত যন্ত্রনাদায়কভাবে বিধতে লাগলো। রাগ সামলাতে না পেরে তার ক্রাচের লাঠি দিয়ে এক ঘা বসায়ে দিল বউ এর কানে, চোয়ালে। ওমা গো, মরিচি গো, বলে বিলকিসও ফিরে উঠে লালচাঁন কে দু’হাতে সজোরে এক ধাক্কা মেরে উল্টে ফেলে দিয়ে গালি দিতে দিতে ঘরের বাইরে চলে গেল।
সে সময় মেয়ে টুনটুনি দাদীর কাছে বসে ছিল। মা-বাবার রাগারাগি আর মারামারি দেখে ভয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতেছিল। শিশুরা পিতামাতার মধ্যে যুদ্ধ দেখতে পারে না। মা-বাবার মধ্যে শান্তি দেখলে শিশুরা সবচেয়ে সুখ পায়। লালচাঁনের মা ছেলে আর ছেলের বউ এর হাতাহাতি শুয়ে শুয়ে দেখলেন। কি যেন বলার চেষ্টা করলো খুব কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না। মুখ থাকে কিন্তু অনেক সময় বলার মত কথা থাকেনা মানুষের। আবার অনেক সময় অনেক কথা বলার থাকলেও সেগুলো বলে ফেলার সময় মুখ খুলতে চায় না। মুখ থাকতেও কথা বলতে না পারা খুব যাতনার। লালচাঁনের মার ঠোট দুটো কয়েক বার নড়ে উঠেছিল। সম্ভবত সে বউমাকে অনুনয় করে বলতে চেয়েছিল-
“আমার চিকিৎসা করা লাগবে না, বৌমা। দোকানও বিক্রি করতে হবে না। শুধু আমার অভাগা লালচাঁনকে তুই কষ্ট দিসনে, মা।”
মেয়ে টুনটুনি লাঠিটা কুড়ায়ে বাবার হাতে দিয়ে বাবাকে উঠতে সাহয্য করলে লালচাঁন উঠে গিয়ে মায়ের পাশে বসে তার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। ছেলের হাতের প্রতিটা স্পর্ষে তার মা যেন এক স্বর্গসুখে গভীর ঘুমে ঢলে পড়লেন। আর বুজে যাওয়া চোখের দু’কোন বেয়ে বড় দুফোটা অশ্র জল বেরিয়ে আস্তে আস্তে গড়িয়ে কপোল বেয়ে মাটির দিকে ধায় করলো। লালচাঁন ডান হাতটা দিয়ে যত্ন দিয়ে, আলতো করে সেই অশ্রæ মুছে তার নিজের কপালে মুছে নিল। যেন মায়ের চোখে অশ্রু ঝরানোর সমস্ত দায় অপরাধী সন্তান হিসাবে নিজের কাঁধে তুলে নিতে লাগলেন। নিজের চোখের অশ্রæ সংবরণ করতে পারলো না। তার দুচোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়তে লাগলো মায়ের বিছানায়। এ যেন আদরের সন্তানের জোখে বয়ে যাওয়া আষাড়ের এক শান্ত বর্ষণ যার ধ্বনিতে মাতাল হয়ে তার মা একবারে নিশ্চুপ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।
সেই রাতেই লালচাঁনের মা পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। প্রায় সমস্ত রাত তার স্ত্রী আর ঘরে ফিরে দেখেনি শ্বাশুড়ি বাঁচলো, না মরলো। ঘরের বাইরে উঠোনের এক কোনে দাঁড়ায়ে মোবইলে কার সাথে যেন বিলকিস সে রাত্রে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছিল। কি কথা হয়েছিল, কার সাথে কথা হয়েছিল কিছুই লালচাঁনের খেয়ালে আসেনি। শুধু একবার একটা কথা স্পষ্ট হয়ে তার কানে এসে বেজেছিল-
“তুমি আমাকে যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে দূরে কোথাও নিয়ে যাও। এই ফকিরের ঘর আমার আর ভাল লাগছে না।”
এ কথায় সেদিন লালচাঁন কি বুঝেছিল তা সেই জানে। স্ত্রীর এ কথাগুলো সে আদৌ মনে রেখেছিল কিনা তাও সে জানে। কারণ সে রাতে মা ভিন্ন জগতের অন্য কোন বিষয়ে তার কোন খেয়াল ছিল না। মায়ের মৃত্যুর চেয়ে সন্তানের জন্য বড় কোন বিষয় জমিনের উপরে আর হতে পারে না। হয়তো সে ঠিক শুনেছিল কিন্তু তাতে সে বাড়তি কোন ভয় অনুভব করেনি। কারণ রেল লাইনে মাথা কাটা পড়লে দেহ নিয়ে ভেবে কি লাভ হয়। তবে সে পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, তার স্ত্রী অন্য কোন পুরুষে মজেছে। তার সংসারে এখন বিলকিসের শুধু দেহটাই কেবল অনিচ্ছাই ঘুরছে, ফিরছে। মনে-প্রাণে সে এ সংসারে অনুপস্থিত। শারীরীক ভাবেও কবে উধাও হয়ে যাওয়ার সুবিধাজনক কোন প্রহরের জন্য অপেক্ষা করে চলেছে হয়ত। লালচাঁন সব বুঝেও স্ত্রীকে সে এ বিষয়ে কিছুই বলল না। কারণ সে বুঝেছিল তার শক্তিতে এখন চরম ভাটা পড়েছে। তার নিজের অভিকর্ষ বল পেরিয়ে তার স্ত্রীকে এখন ভিন্ন কোন গ্রহ টানছে দারুন কোন উৎসাহে। এখানে তাকে আটকানোর চেষ্টা করার চেয়ে বড় পাগলামী আর হয় না।
মায়ের মৃত্যুর ঠিক এক মাস দুই দিন পর সত্যি সত্যিই বিলকিস রাতের অন্ধকারে স্বামী, সন্তান রেখে তার নতুন প্রেমিক পুরুষের সাথে পালিয়ে গেল।
মানুষেরা খুব ছি ছি করেছিল। লালচাঁনের বৌ এর এই কর্মকান্ডে এলাকাময় আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠে কিছুদিন ধরে তা বইতে থাকলো। সমালোচনা আর নিন্দে করার ক্ষমতা আল্লাহ বাঙালীকে অন্যান্য সকল যোগ্যতা-দক্ষতার চেয়ে কিঞ্চিত হলেও একটু বেশি দিয়েছে বোধ হয়। ব্ঙাালীদের এই একটি কাজে অনন্ত উৎসাহ আর শক্তির কোন অভাব ঘটে না। আপিন না খেয়ে মরলেও একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসবে না এখানে। কিন্তু আপনি ক্ষুধার জ্বালাই চুরি করে বসলে আপনার শরীরের ছাল,বাকল তুলতে কারো ডাকার প্রয়োজন পড়বে না। মৌমাছির মত ঝাঁকে ঝাঁকে এসে হাজির হবে আর কথার অঘাতে, হাতের আঘাতে আপনাকে শেষ করে দিতে চাইবে। মা বেঁচে থাকতে, বৌ টিকে থাকতে কেউ কোন দিন উকিঁ দিয়েও দেখলো না যে, লালচাঁনের কিসে চলছে, কেমন করে চলছে। বউ অন্যের হাত ধরে বাড়ি ছাড়ার পর এখন অনেকেই তাকে শান্তনা দিতে আসল। এই শান্তনার বানী শুনে শুনে লাল চানের দিন কেটে যাবে হয়তো কিন্তু এতে তার আর তার একমাত্র মেয়ের পেটও চলবে না, জীবনও চলবে না।
মা মারা গেলে কেউ এসে বলে না যে, আমি তোমার মা হবো। পৃথিবীতে দুইটি মানুষ আছে যার ডুপলিকেট দুনিয়ার উপরে মিলবে না। এক হলো মা। আর এক হলো বাবা। অন্য কেউ মা হলে সে হবে সৎ মা আর বাবা হলে হবে সৎ বাপ।
তবে বউ মারা গেলে অনেকেই এসে বলবে আমি তোমার বউ হবো। লালচাঁনের বউ চলে যাবার পরে দ্বিতীয় বিয়ের দু’একটা প্রস্তাব আসতে লাগলো। কিন্তু তিনি সব নাকচ করে দিলেন। মা বিলকিস চলে যাবার পরে তার মেয়েটা মায়ের জন্য ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল। কিন্তু সেও এখন শান্ত হয়ে এসেছে। তাই নতুন করে বিয়ের কথা মাথায় না এনে লালচাঁন তার মেয়ের জন্য মা-বাবার দ্বৈত্য ভূমিকা পালন করতে লাগলেন।
মেয়েকে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দিল। সকালে উঠে লালচাঁন নিজ হাতে রান্না করে। মালয়েশিয়া থাকতে নিজে রান্না করে খেত। সেই চর্চাটা তার বেশ কাজে দিয়েছে এখন। মেয়েকে খাওয়ায়ে স্কুলে পাঠায়। আর নিজে গিয়ে বসে দোকানে। স্কুল থেকে ফিরে মেয়ে বাবার সাথে দোকানে বসে থাকে। দোকানের মধ্যে এটা ওটা নিয়ে নাড়া চাড়া করে সময় কাটায়। দুপুরে দোকান বন্ধ করে বাপ মেয়ে এক সাথে আবার বাড়ি চলে আসে। বিকালে লালচাঁন আবার দোকানে চলে যায়। কতক দিন মেয়েটা তার সাথে আবার দোকানে ফিরে যায়। আবার কতক দিন পাড়ার ছেলে মেয়েদের সাথে খেলে। আবার দু’একদিন দুপুরে খাওয়ার পরে বাবার সাথে গল্প্ করতে করতে ঘরেই ঘুমিয়ে পড়ে।
সেদিনও ঘুিময়ে পড়েছিল। লাল চাঁনেরও মেয়ের সাথে গল্প করতে করতে কাক ঘুম হয়ে যায়। হঠাৎ পাড়ার একজন মহিলা একটা জরুরী সদায় কেনার জন্য ডেকে দোকানে নিয়ে যায় লালচাঁন কে। এরপর একে একে আরো খরিদদার জমে গেল সেই বিকালে। এত বেশি খরিদদার এর আগে তার দোকানে কোন দিন হয়নি। সেদিন প্রায় সন্ধ্যা অবধি বেচা-কেনা খুব ভাল হলো। বেচাকেনা ভাল হলে দোকানদারের মন ভাল থাকে আর ব্যবসায়ের গভীরে মন প্রবেশ করে।
বেচাঁ কেনায় ডুবে যাওয়ায় লালচাঁন মেয়ের কথা ভুলে গিয়েছিল। এমন সময় সন্ধ্যার আযান পড়ে গেল। হঠাৎ মেয়ের কথা তার স্মরণ হয়ে বুকের মধ্যে কেন যেন একটা ভয় অনুভব করে উঠলো। দ্রæত দোকান বন্ধ করে সে বাড়িতে চলে আসলো। ঘরে ঢুকে দেখে মেয়ে তখনো মেঝের উপরে উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে।মেয়ের পাশে বসে তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগেলো আর ডেকে উঠনোর চেষ্টা করতে লাগল-
“টুনটুনি। মা আমার। উঠে পড় আমার সোনা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে। ওলে বাবা লে, আজ আমার আম্মাজানটা লম্বা ঘুম দিয়েছে লে। এবার উঠে পড়, মা। কই টুনি সোনা? রাত হয়ে গেল যে, ওঠো ওঠো।”
লালচাঁনের টুনটুনি আর জেগে উঠলো না। সে চিরকালের ঘুমে মজে গিয়েছিল।
অনেক ডাকাডাকি করেও যখন টুনটুনির ঘুম ভাঙাতে পারছিল না তখন লালচাঁন ভয় পেয়ে যায়। এবার নিজের হাতে মেয়েকে উপুড় থেকে চিৎকরে দেখলো তার মুখ দিয়ে সাদা ফেনা বের হচ্ছে। সারা শরীর নীল বর্ণ হয়ে গেছে। লালচাঁন মেয়েকে তুলে নিয়ে শক্ত করে জড়ায়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ব করলো। তার হাউমাউ করে কান্নার শব্দ শুনে পাড়াপড়শিরা এসে দেখলো লালচাঁনের হাতে তার মেয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। সবাই ধরাধরি করে হাসপতালের দিকে ছুটলো। হাসপাতালের ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলল রোগী সাপে কেটে পাঁচ ঘন্টা আগেই মারা গেছে।
জীবন বদলের স্বপ নিয়ে ভিন দেশে দু’পা বাড়িয়েছিল লালচাঁন। কিন্তু অদৃষ্টের খেলায় মুঠোভরা দুঃস্বপ্ন নিয়ে ফিরে আসলো দেশে। তবে এক পায়ে। এর পরে একে একে মা, স্ত্রী, আর কলিজার টুকরো সন্তানও ছেদ হয়ে গেল জীবন থেকে। ছোট বেলায় ট্রেনে কাটা পড়েছিল তার বাম হাতের তিনটি আঙুল। তখন বন্ধুরা বলতো-
“তোর সৈনিকের চাকরী হবেনা। অঙ্গচ্ছেদ হলে সেনাবাহিনীতে নেয় না।”
কিন্তু জীবন যুদ্ধে লালচাঁন আজ অনেক বড় সৈনিক। জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু সবচেয়ে প্রিয় তার সব কিছু ছেদ হয়ে যাওয়ার পরেও আবার নতুন করে ঘর বেঁধেছে লালচাঁন। চালিয়ে যাচ্ছে এক অবিরাম জীবন যুদ্ধ। এক পায়ে আর সাত আঙুলে।
(সমাপ্ত)