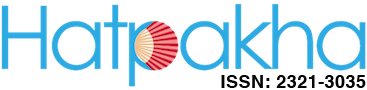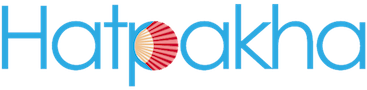আজকাল মধ্যবিত্তের জীবনে এক নূতন সংস্কৃতির উদয় হয়েছে। গতকাল আমার এক কলেজের বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, তার ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে। সেখানে দেখলাম বেশ জোরদার আলোচনা হচ্ছে যে, বিয়ের লৌকিকতা পর্ব মিটলেই নবদম্পতি মিলে মালয়েশিয়া যাবে মধুচন্দ্রীমা করতে। সরকারি চাকুরে ছেলের বাপ, মানে আমার বন্ধুটি যখন বিয়ে করেছিল, তখন অনেক কষ্টে পাঁচদিন পুরী যাবার খরচটুকু জোগাড় করতে পেরে ছিল। ওই আসরে উপস্থিত আমাদের আর এক বন্ধুর মেয়ের স্বামী বতর্মানে ঐ মালয়েশিয়াতেই একটা পর্যটন সংস্থায় কর্মরত। সেই সুবাদে বন্ধুটি সস্ত্রীক মেয়ে জামাইয়ের ওখানে, মানে মলয়েশিয়া ঘুরে এসেছে। বিয়ে বাড়ির বন্ধুমহলের আড্ডার মুল আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলো বিদেশ ভ্রমণ। খাওয়াদাওয়ার পর বাড়িতে ফেরার পথে ভাবছিলাম, বিদেশ তো দূরের কথা, আমিতো আমার ছেষট্টিটা বসন্ত পার করেই ফেলেছি, তবুও নিজের দেশের কিছুই তো ঘুরে দেখা হয়নি। নিম্নবিত্ত পরিবারের থেকে বেড়ে ওঠা আমার অধিকাংশ বন্ধুদেরও অবস্থা প্রায় আমারই মতো অথবা আরও শোচনীয়। আমিতো তবু কর্মসুত্রে অনেক জায়গাতেই কাটিয়েছি, অনেকের তো সেই সুযোগটুকুও হয়নি। পিছনে কাটিয়ে আসা দিনগুলোতো মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম আর নিজের ছোট্ট পরিসরে নিজের থাকা জায়গাগুলোকে যেভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেটা ভাবতে ভাবতেই মনটাকে ফেলে আসা দিনগুলোতে চলে এলাম।
বাংলায় জন্ম, বাংলায় বড়ো হয়ে ওঠা, শিক্ষা প্রাপ্তি তবুও বাংলার কিছুই কি দেখা হয়েছে নাকি ছাই আমার? আর ভারতীয় রেলের কর্মজীবনের অনেকটা সময় আমার বাংলার বাইরেই কেটেছে। জীবনের চোদ্দটা বছর বড়ো কিছু কম সময় নয়। পুরো চোদ্দটা বছর মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের দূর্গ, বিলাসপুর, স্যাডোল আর সরগুজা জেলায় দিন কেটেছে আমার। এই সমস্ত জায়গাগুলোর মধ্যে কোন যায়গা থেকে তেইশ বছর আগে কিংবা কোন যায়গা থেকে তারও অনেক আগে আমি ছেড়ে চলে এসেছি। আমি থাকার সময় এই অঞ্চলগুলো ভারতের সবচেয়ে বড়ো রাজ্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তখনও এই অঞ্চলের মানুষজনকে ছত্তিশগড়ী বলে ডাকা হতো। আমি বাংলায় ফিরে আসার দুবছর পরে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০০ সালে, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যকে বিভক্ত করে ছত্তিশগড়কে আলাদা রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। আমার থাকা জায়গাগুলোর মধ্যে স্যাডোল মধ্যপ্রদেশে থেকে গেলেও দূর্গ, বিলাসপুর আর সরগুজা এই জায়গাগুলো বর্তমানে ছত্তিশগড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ছত্তিশগড় রাজ্যের প্রায় প্রতিটা জায়গাই পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গৌরবে সম্বৃদ্ধ, তবুও কেমন যেন উপেক্ষিত। উপেক্ষার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দর্শনীয় জায়গাগুলো একইরকম ভাবে বহুকাল অনাদরে পড়ে থেকেছে। ইতিহাস বলে বিশাল ছত্তিশগড় রাজ্যকে প্রাচীনকালে ঈক্ষাকু বংশের রাজত্ব চলাকালীন সময়ে “দক্ষিণ খোসালা” বলা হোত। বতর্মানে ছত্তিশগড়ের রাজধানী “রায়পুর” সেযুগেও “দক্ষিণ খোসালার” রাজধানী ছিল। পরবর্তীকালে কলচুরী রাজত্বে শাষন করার সুবিধার্থে “দক্ষিণ খোসালাকে” বিকেন্দ্রীকরন করে “রায়পুর” ও “রতনপুর” দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। কলচুরী আমলে এই অঞ্চলের আরও বিকেন্দ্রীকরন করা হয়। প্রতি বারোটা গাঁও মানে গ্রাম মিলে বানানো হয় একটি “বারাহ” আর প্রতি সাতটি “বারাহ” নিয়ে গঠিত হয় একটি করে “গড়”। পুরো রাজ্যটা ছত্রিশটা “গড়ে” বিভক্ত করা হয়। স্থানীয় লোকজন বলে থাকেন যে ছত্রিশটা “গড়” মানে ছত্রিশটা কেল্লা ছিল এই অঞ্চলে। সেটা থেকেই ছত্তিশগড় নামের উৎপত্তি। এই ছত্রিশটা গড় বা কেল্লার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি । যদিও কিছু কিছু অঞ্চলের নামের সাথে গড় কথাটা জুড়ে আছে তবে ছত্রিশটা গড়ের অঞ্চল আছে কিনা জানিন। কেল্লা না থাকলেও আমি মেরেকেটে সাতটা গড়ের নাম যুক্ত জায়গার নাম শুনেছি । রায়গড়, ডোঙ্গোড়গড়, বান্ধবগড়, মনিন্দ্রগড়, সুন্দরগড়, খয়রাগড়, টিটলাগড়। আরও গড়ের নামে জায়গা হয়তো আছে, কিন্তু আমার জানা নেই। ছত্তীশগড় নামের উৎপত্তি নিয়ে আরও একটা মতবাদ হোল ছেদি বংশের শাষন চলাকালীন এই অঞ্চলকে ছেদিশগড় বলা হোত, সেটাই লোক মুখে পরিবর্তিত হতে হতে ছত্তীশগড়ে পরিনত হয়েছে। বাংলা আমার জন্মধাত্রী মাতৃভূমি আর চোদ্দ বছর আমাকে সযত্নে লালন পালন করার জন্য আমি চত্তিশগড়কে আমার দ্বিতীয় মাতৃভূমির মতোই সন্মান করি।
এই অঞ্চলে আমার প্রথম পোষ্টিং ছিল দূর্গ জেলায় “ভিলাই” অঞ্চলে। “ভিলাই মার্শালিং ইয়ার্ডে” টাইপ টু কোয়ার্টারে একা ব্যাচেলার থাকি। এখানে আসা ইস্তক লোকজনের মুখে ডোঙ্গরগড়ে “বোমলাই” মাতার কথা শুনে আসছি। স্থানীয় চত্তিশগড়ী লোকজনের মুখে এই ব্যাঘ্র বাহিনী “বোমলাই” মাতার কথা শুনেছি। ইনি অত্যন্ত জাগ্রত দেবী বলে এখানকার মানুষজন বিশ্বাস করেন । কারো কারো মুখে শুনলাম মাতার এই ক্ষেত্রটি নাকি আসামের সতীপিঠ কামরূপ ক্ষেত্রের মতোন। ঝাড়ফুঁক আর জাদুটোনায় অসম্ভব বিশ্বাস এখানকার মানুষজনের যা আমাকে স্থম্ভিত করেছিল। আসামের কামরূপের মতোন যাদুটোনার সাহায্য বোমলাইতেও নাকি মানুষকে পশু বা পাখিতে পরিনত করে রাখা হয় এমনটাই স্থানীয় মানুষেজনের বিশ্বাস। কোন সময় তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্র ছিল এই ডোঙ্গরগড়। ডোঙ্গর একটা মারাঠি শব্দ, যার মানে পর্বত আর গড় হোল গিয়ে কেল্লা। আড়াই হাজার বছর আগে ঘন জঙ্গল ও পাহাড় অধ্যুসিত এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন বীরসেন। নিঃসন্তান বীরসেন শিব ও পার্বতীর আরাধনা করেন ও মাতা পার্বতীর কৃপায় একবছর পরে পুত্র সন্তান লাভ করেন। বীরসেন তার পুত্রের নাম রাখেন মদনসেন। বীরসেন পাহাড়ের মাথায় নিজের আরাধ্য দেবী মাতা পার্বতীর অর্থাৎ মাতা “বোমলাই” এর মন্দির বানিয়ে সেখানে নিত্যপুজা শুরু করেন। মদনসেনের পুত্র কামসেন উজ্জয়ীন রাজা বিক্রমাদিত্যর সঙ্গে ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হন। রাজা কামসেন “বোমলাই” মাতার আশির্বাদ ও কৃপা ধন্য ছিলেন। রাজা কামসেনের রাজ দরবারে কামকন্দলা নামে একজন অসামান্য সুন্দরী নর্তকী ও মাধবানল নামে একজন গায়ক ছিলেন। এদের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ ছিল। একদিন এদের সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা কামসেন মাধবানলকে একটি বহু মূল্যবান হার উপহার দিলেন। মাধবানল ঐ হারটি নিজের গলায় না পরে রাজা কামসেনের সামনেই নিজের প্রেমিকা কামকন্দলাকে পরিয়ে দিলে রাজা কামসেন প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করেন এবং এই আচরণের অপরাধে গায়ক মাধবানলকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত মাধবানল উজ্জয়ীন রাজা বিক্রমাদিত্যর আশ্রয় নিয়ে প্রেমিকা কামকন্দলার মুক্তি প্রার্থনা করলেন। ইনিই সেই বেতাল খ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্য। রাজা কামসেনের কাছে উজ্জয়ীন রাজা বিক্রমাদিত্যর দ্যুত গিয়ে কামকন্দলাকে মুক্তি দিতে বললে এবং রাজা কামসেন তাকে মুক্ত করতে অশ্বীকার করলে ভয়ংকর যুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন বিক্রমাদিত্যের আরাধ্য দেবতা শিব প্রথম দিকে বিক্রমাদিত্যর পক্ষে ছিলেন তাই কামসেন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিলেন। এরপর যে মুহূর্তে মাতা বোমলাই কামসেনের পক্ষে দাঁড়ালেন, সেই মুহূর্ত থেকে শিব নিজেকে বিক্রমাদিত্যর পক্ষ থেকে সরিয়ে নিলেন। মাতার অশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে শক্তিশালী রাজা বিক্রমাদিত্য পরাজিত হলেন। মাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বোমলাই পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে মাতা বোমলাই বিক্রমাদিত্যকে আত্মহত্যা করতে বাধা দিলেন। বোমলাই মাতার আদেশে কামসেন কামকন্দলাকে মুক্তি দিয়ে মাধবানলের সাথে মিলিত হতে দিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য মাতা বোমলাইকে এখানেই নিত্য পুজো করতে লাগলেন। চত্তিশগড়ী মানুষজন বলে থাকে যে মাতা বোমলাই ইচ্ছা না করলে তার দর্শন করা সম্ভব হয় না। ভিলাই মার্শলিং ইয়ার্ডের “জি-কেবিন” থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় আপ বোম্বে এক্সপ্রেস ধরে ডোঙ্গড়গড় পৌছে বোমলাই মাতা দর্শন করে দুপুরের ডাউন বোম্বে মেল ধরে সন্ধ্যায় ভিলাই ফিরে আসা যেত। আমার কোয়ার্টারে আমারই সমবয়সী সেন বলে একটি ট্রেনস বাবুকে কিছুদিন আমার সাথে থাকতে দিয়েছিলাম। দুজনে মিলে এক রবিবার বোমলাই দর্শনে যাব ঠিক হোল। বোম্বে এক্সপ্রেস রোজ রোজ একঘণ্টা লেটে ভিলাই জি-কেবিনে আসতো। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সকাল সাড়ে ছটায় জি-কেবিনে এসে দুজনে দেখি, সেইদিনই ট্রেন সঠিক সময় সাড়ে পাঁচটায় “জি-কেবিনে” এসে চলেও গেছে। বোমলাই মাতা এ যাত্রায় আমাদের দুরেই ঠেলে রাখলেন।
এরপর বছরখানেক বাদে রেলের কাজে আমাকে দু রাত আর তিন দিনের জন্য ডোঙ্গরগড় গিয়ে থাকতে হয়। বর্ষাকালে ডোঙ্গড়গড় যাবার সময় এন. ভি. পিল্লেদার সাথে মালগাড়ির ডিজেল ইঞ্জিনের ফুটপ্লেটে আর ফেরার সময় স্টীম ইঞ্জিনের ফুটপ্লেটে সফর করার সময় এই অঞ্চলের অনন্য প্রকৃতি আমাকে তার দর্শন দিতে কার্পণ্য করেননি। তখন আমার বন্ধু দিলীপ, তাপস, দুলাল আর নারায়ন ডোঙ্গরগড়ে পোস্টেড। কাজের জটিলতা এতটাই বেশি ছিল যে তাপসের সাথে এক সন্ধ্যায় ছোট বোমলাই দেখেই ফিরে আসতে হোল। ছোট বোমলাই মানে মাতার ভগ্নি। ইনি পাহাড়ের নীচে অবস্থান করেন। এত কাছে এসেও বোমলাই দর্শন আমার কাছে অধরাই থেকে গেল। এর পাঁচ বছর পরে আবারও আমাকে একরাতের জন্য ডিউটিতে ডোঙ্গরগড়ে থাকতে হয়েছিল। এবারে স্বপনদা আর সুনীল কুমারদা আমার সাথী হয়েছিল। কিন্তু এবারও কাজের জটিলতার কারনে বোমলাই মাতার মন্দিরে যাবার সুযোগ হোলনা। ধরেই নিয়েছিলাম বোমলাই মাতার মন্দির অবধি বোধহয় আর আমার যাওয়া হবে না। তিন তিনবার ব্যার্থ হবার পর আমি, আমার দেড় বছরের মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ভিলাই “জি- কেবিন” থেকে চরোদার “এইচ-কেবিনের” স্টেশন মাষ্টার সরকার দা, বৌদি ও তাদের ছেলে মিঠুনকে নিয়ে সকালের বোম্বে এক্সপ্রেস ধরে চতুর্থবারের প্রচেষ্টার পর ডোঙ্গরগড়ে “বোমলাই” মাতার দর্শন লাভ করলাম। খাড়া পাহাড়ের হাজারটা পাথরের সিড়ি চড়ে বোমলাই মাতার দরবারে পৌছতে হয়। বেশ কষ্টকর চড়াই। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য ডুলির ব্যাবস্থা আছে দেখলাম । আমরা ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে নিয়ে হাজারটা সিড়ি চড়েই পৌছে গেলাম মায়ের থানে। এখোন এখানে জঙ্গলের লেশমাত্র নেই। মায়ের থানে সেদিন একদম ভিড় ছিলনা। লাল রঙের সিঁদুরে রাঙানো মায়ের পাথরের মুর্তি। শান্ত পরিবেশে শুকনো নারকোল দিয়ে মায়ের পুজো দেওয়া হোল। পাহাড়ের উপর থেকে ডোঙ্গরগড় স্টীম লোকো শেডটা খেলনার মতোন দেখাতে লাগলো। বতর্মানে আর না চাইলে মায়ের দরবারে যেতে চড়াই করার কষ্ট করতে হয়না কারণ, সরকার রোপওয়ে বানিয়ে দিয়েছে। প্রতি রামনবমী তে এখানে বিরাট মেলা বসে। নবরাত্রীও এখানে ধুমধাম করে পালন হয়। মাতা বোমলাই হয়তো চাইছিলেন আমি সপরিবারে তার দর্শনে আসি, তাই হয়তো আগের তিনবার আমার পক্ষে মায়ের দরবারে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। সেটাই আমাদের প্রথম আর শেষ বারের মতোন মাতা বোমলাই দর্শন।
ভিলাই মার্শালিং ইয়ার্ড (BMY) যায়গাটা আদতে দেওবলদা আর চরোদা নামে দুটো অতি প্রাচীন গ্রামের মধ্যবর্তি বিরাট একটা কাটখোট্টা শুস্ক প্রান্তর। রুক্ষ লাল মোড়ামের দেশ। দেওবলদা গ্রামে অবস্থিত আছে প্রায় ১২০০ বছরের অধিক পুরোনো একটা চুড়া বিহীন শিব মন্দির। পাথরের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠলে মন্দিরের চাতাল। সেখান থেকে আবার সিড়ি দিয়ে নীচে নামলে মন্দিরের গর্ভগৃহ। অনুভব হবে পাতালে নামছি। মাটির নীচে প্রায় অন্ধকার গর্ভগৃহে কালো পাথরের লম্বাটে শিব লিঙ্গকে তামার সাপ জড়িয়ে আছে। এখানে শিবের নিত্য পুজো হয়। তখনও অবধি একাও পুজো করতে পারা যেতো । এই মন্দিরের গঠনশৈলী দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদের ধারনা কোনসময় এই “দেওবলদা-চরোদা” অঞ্চলটি চোল সম্রাজ্যের অধীন ছিল। লোকশ্রুতি, এই মন্দিরটি তৈরির সময়, মন্দির গাত্রে নিখুঁত মুর্তি খোদাই করার জন্য কারিগররা নগ্ন হয়ে কাজ করবেন এবং কাজের সময় কেউ সেই নগ্নতা দেখবেন না, এমনই শর্ত হয়েছিল রাজা ও কারিগরদের মধ্যে । মন্দিরের চুড়া ও কারুকার্য সম্পুর্ণ হবার আগেই, রানি সেই শর্ত ভেঙে নির্মাণ কাজ দেখতে গেলে, নগ্ন কারিগররা পাশের পুস্করনীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রান বিসর্জন দেন। আশ্চর্যর ব্যাপার এই, যে লাল মোড়ামের শুস্ক দেশে মন্দিরের পাশে এই পুস্করনীতে সারা বছর জল টলটল করে। কারিগরদের আত্মবলির ফলে মন্দির নির্মাণ অসম্পুর্নই থেকে যায়। তাই এই মন্দিরে চুড়া নেই। মন্দির গাত্রে বেশ কিছু মুর্তি আছে। মন্দিরটি বর্তমানে ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের দ্বারা সংরক্ষণ প্রাপ্ত।
ভিলাইতে প্রথমটায় আমি, তপন, বিশু আর রতীশ পোস্টিং পাই। দুবছরের মধ্যে বিশু রায়পুর আর রতীশ দিল্লিরাজরা ট্রান্সফার হয়ে চলে যায়। সেবার সচীদা, সুব্বাদা ও তপনদের বিভাগীয় পিকনিকে আমিও চললাম “রাজীম”। সচীদা ও সুব্বাদারা অন্য বিভাগের হলেও কখনো তপনদের সাথে আমাকে আলাদা ভাবতো না। সেবারে পিকনিকে আমাদের গন্তব্য হোল “রাজীম”। ভিলাই থেকে রায়পুর হোল কুড়ি কিলোমিটার আর রায়পুর থেকে রাজীমের দূরত্ব হোল চল্লিশ কিলোমিটার বা তার থেকে সামান্য কিছু বেশি। রায়পুর স্টেশনের একনম্বর প্ল্যাটফর্মের গায়েই ছোট রেল লাইনের নীচু প্ল্যাটফর্ম। সেখান থেকেই প্রতিদিন কয়েক জোড়া ন্যারো গেজের খেলনা ট্রেন প্রথমে আহ্বানপুর জংশনে গিয়ে পৌঁছয়। সেখান থেকে লাইন দুভাগে ভাগ হয়ে একটা লাইন দিয়ে রাজীম অবধি আর একটা লাইন দিয়ে ধামতারি অবধি যায়। পিকনিকের জন্য ট্রেনে না গিয়ে সবাই মিলে ডিপার্টমেন্টের গাড়িতে “রাজীম” রওনা দেওয়া হোল। আমার কাছে একটা পকেট টেপ রেকর্ডার ছিল। কর্ড লাগিয়ে কারো অসুবিধা না করে নিজের পছন্দের গান শোনা যেতো। তপন নিতে এসেছিল আমাকে, হাতে ওর একটা ক্যাসেট, আমাকে দিয়ে বললো শুনিস। গাড়িতে বসে রেকর্ডারে ক্যাসেট চালিয়ে কর্ড কানে গুজে দিতেই অন্য জগতে পৌঁছে গেলাম। পন্ডীত নিখিল ব্যানার্জীর সেতারে রাগ “মেঘ” বাজছে। সঙ্গীত প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে না বললেই নয়। আমার জানা সাতটা গড়ের একটা হোল খয়রাগড়। এখানে একটা সঙ্গীতের বিশ্ববিদ্যালয় আছে। খয়রাগড় সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পুত্র বিখ্যাত সেতার বাদক পন্ডিত বুধাদিত্য মুখার্জী ভিলাই নগরের বাসিন্দা। তপন তখন সেখানে সেতারের শিক্ষা গ্রহন করছিল। কলকাতাকে সংস্কৃতির পিঠস্থান বললেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধাত্রী ভুমি কিন্তু কখনও বাংলা নয়। এছাড়াও ভিলাইতে কে.পি. বিশ্বকর্মা বা লালসাহীর মতোন অতি অল্প শিক্ষিত ও অতি নিম্নবিত্ত রেলের কারিগরি বিভাগের শ্রমজীবী মানুষদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ও দক্ষতা দেখা আমার কাছে এক বিশ্ময়কর অভিজ্ঞতা। ভিলাইতে থাকাকালীন তপনের অনুপ্রেরণায় আমি পুরোপুরি মার্গ সঙ্গীতের অনুগ্রাহী হয়ে উঠলাম। দুজনে দুকানে কর্ড গুজে সবটুকু রাস্তা পন্ডিত নিখিল ব্যানার্জীর “মেঘ” রাগের নেশায় চলে এলাম। রাজীমে পৌঁছে কান থেকে কর্ড খুলে তাকিয়ে মনে হোল শহরটা ঘিঞ্জি ও নোংরা। একটা ব্যাস্ত নদীর পুল পার করে একটা ফাঁকা মাঠে পিকনিকের আসর বসলো। সামনে দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছ জল, তপন উৎসাহে ঠান্ডাতেই জলে নেমে গেল। নদীতে কোথাও হাটু জল আবার কোথাও কোমর জল। দু চারটে নৌকা আছে ঘাটে বাধা। একটা নৌকায় বসে আমি আর তপন অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম। সকালের জলখাবার খেয়ে বেড়িয়ে পড়লাম নদীর পাড় ধরে অজানার সন্ধানে। নদীর ধার ধরে খানিকক্ষণ এগিয়ে দেখলাম এক বিশাল ও বিস্তির্ণ বালুকা প্রান্তর। নদীটা এখানে বাঁক নিয়েছে। তীর তীর করে বয়ে চলা এক পা পাতা ডোবা শ্রোতের জল পেরিয়ে বিশাল বালুকা প্রান্তরের মাঝামাঝি প্রায় কুড়ি ফুট উচু চবুতরার (ঢিপির) উপর শিব মন্দির। সিড়ি দিয়ে উঠে মন্দির দর্শন করে ফিরে আসছি তখন সচীদাদের সাথে দেখা হোল। ওরা জানালো রাজীম লোচন মন্দির দেখে ওরা এই দিকে যাচ্ছে। আমরাও রাজীম লোচন মন্দিরে গেলাম কিন্তু ততক্ষণে মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। দুপুরে পিকনিকের খাবার খেয়ে বিকেলের মধ্যে পিকনিকের দল ভিলাই ফিরে এল।
এর পাঁচ বছর পরে আমি আমার দুই বছরের মেয়েকে ও স্ত্রীকে নিয়ে আরও একবার রাজীম যাই। এবারে আমাদের সঙ্গী ছিলেন চরোদার “এইচ-কেবিনের” স্টেশন মাস্টার সরকার দা, বৌদি আর তার ছেলে মিঠুন। সরকারদার সহকর্মী দাস বাবু “বালুদ” আর “দিল্লিরাজরার” মাঝে “কুসুমকাশা” স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিলেন। চোখের কিছু সমস্যা হওয়ার কারনে ডিপার্টমেন্ট ওনাকে ন্যারো গেজে আহ্বানপুর জংশনে বদলি করে দেয়। রায়পুর স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে নীচে ন্যারো গেজের স্টেশন থেকে খেলনা গাড়ি চেপে সবাই মিলে বিকেলে আহ্বানপুরে দাস বাবুর রেল কোয়ার্টারে গিয়ে উঠলাম। বিকেলে আড্ডা মারার পর দাস বাবু দিনের শেষ ধামতারি লোকালটা এ্যাটেন্ড করতে এলেন। আমরাও এলাম আহ্বানপুর স্টেশনটা দেখতে। স্বপ্নের মতোন মনে হোল জায়গাটা, একদিকে চার পাচটা খেলনা গাড়ির ডাব্বাতে গুটিকয়েক যাত্রী, আলো বিহীন ছোট্ট জনমানব শুন্য প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনে না আছে কোন দোকান পাট না আছে কোন হকার। ধামতরির শেষ ট্রেনটা ছেড়ে গেলে পরে নেমে স্টেশন চত্বরে নেমে এল অদ্ভুত নিশঃব্দতা, ওদিকে অল্প কিছুটা দুরে মেনরোডে যানবাহনের হেড লাইটের আলো, ভীড় আর ব্যাস্ততা।
আহ্বানপুরে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে আবারও সেই খেলনা গাড়িতে চেপে এলাম রাজীমে। নদীর এপারে স্টেশন। এবারে কিন্তু কিছুটা পড়াশোনা করেই রাজীমে এসেছি। ছত্তিশগড়ের “প্রয়াগ” হোল রাজিম। প্রতি বছর এখানে মাঘী পুর্নীমা পূর্নিমা থেকে শিবরাত্রী অবধি “কুম্ভ” মেলা হয়। মহানদী, পৈরী আর সোন্দুর তিনটি নদীর মিলন হয়েছে রাজীমে। আগেরবার যে বিশাল বালুকা প্রান্তর দেখেছিলাম সেইটাই সঙ্গম স্থল। যথার্থই ত্রিবেনী সঙ্গম এটা, কোন কাল্পনিক তৃতীয় নদীর উপস্থিতি নেই রাজীমের এই প্রয়াগে। আগেরবার যে নদীর পাশে পিকনিক হয়েছিল সেটা ছিল মহানদী আর পায়ের পাতা ভিজিয়ে যে নদীটি পার করেছিলাম সেটা ছিল পৈরী। বর্ষাকাল ছাড়া সোন্দুর সাধারণত শুকনো থাকে। হাঁটুজল মহানদী পার করে জলে ভিজে এলাম কুলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। জলের সাথে বাচ্চাদের একটা সহজাত বন্ধুত্ব থাকে। আমার দুবছরের মেয়ে আর এগারো বছরের মিঠুন হাঁটুজল মহানদী পার করার সময় জলে এমন লাফালাফি করতে লাগলো যে সবাই ভিজে একশা। সঙ্গমের একেবারে মাঝখানে চারিদিকে বিশাল বালুকা প্রান্তরের মধ্যে প্রায় কুড়ি ফুট উচু আটকোনা বিরাট “চবুতরা” বা চওড়া ঢিপির উপর কুলেশ্বর মহাদেব মন্দির। সঙ্গমটা এতটাই চওড়া যে বর্ষার সময় জলে ভরে গেলে এপার ওপার দেখা যায় না। তখন নৌকায় ছাড়া এই মন্দিরে আসা যায় না। ত্রিবেনীর জল চবুতরার শীর্ষ অবধি পৌছে যায়। এই মন্দিরের পুজারী ও সাধকরা তখন নৌকাতেই যাতায়াত করেন। মন্দিরের মহামন্ডপে একটা শিলালিপি আছে। সেই শিলালীপি থেকে জানা যায় এই প্রাচীন মন্দিরটা নবম শতাব্দীতে তৈরি। সেই প্রাচীন নবম শতাব্দীতে, বর্ষার সময় জলস্তর বৃদ্ধির কথা ভেবে, এই উঁচু পাথরের চবুতরটি বানানো হয়েছিল। চবুতরটি যতটা উঁচু তারচেয়েও বেশি গভীরে এর পাথরের তৈরি মজবুত ভিত্তি। এতটাই মজবুত যে ১৯৬৭ সালে বর্ষাকালে প্রবল জলোচ্ছাসে চবুতর ও মন্দিরটি ডুবে গেলেও জল সরে যাবার পর দেখা যায় মন্দির ও চবুতরের কোন ক্ষতি হয়নি। শিবলিঙ্গে পয়সা ফেললে সেটা এত নীচে চলে যায় যে প্রতিধ্বনি শৃষ্টী করে। কথিত আছে শ্রী রামচন্দ্র বনবাস কালে এখানে তার ইষ্টদেব মহাদেবের পুজো করেছিলেন।
এটা ফেব্রুয়ারি মাস, তাই ত্রীবেনী সঙ্গমের অধিকাংশ অংশেই জল নেই। দীর্ঘ বালুকা ভুমি মাড়িয়ে, আর তিরতির করে বয়ে চলা পৈরী নদীর পায়ের পাতা সমান জল পেরিয়ে, আমরা এলাম রাজীম লোচন মন্দিরে। প্রাচীনকালে রাজীমের নাম ছিল “কমলক্ষেত্র”। এমনটাই বিশ্বাস যে ব্রহ্মান্ড শৃষ্টী কালে শ্রীবিষ্ণুর নাভি কমল এখানে স্থীত ছিল। ব্রহ্মা এখান থেকেই শৃষ্টী রচনা শুরু করেন। সেই কারনে রাজীমের নাম “কমলক্ষেত্র”। পূর্বপুরুষদের মোক্ষ লাভের উদ্যেশ্যে মানুষজন এই প্রয়াগে শ্রাদ্ধ, তর্পন আর পিন্ড দান করে থাকেন। রাজীব লোচন হলেন শ্রীবিষ্ণু। আরো একটা কথা চালু আছে, সেটা হোল পুরীর প্রভু “জগন্নাথ” দর্শনে প্রাপ্ত পূন্য সম্পুর্ন হয় রাজীব লোচনের দর্শনলাভ করার পরেই। অত্যন্ত প্রাচীন এই মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দী সময়কালে তৈরি। মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন মুর্তি। মিথুন মুর্তিও আছে কয়েকটা। কালো পাথরের বিষ্ণুমুর্তি মন্দিরের প্রতি জায়গা থেকে দৃশ্যমান। এখানে সকালে শ্রীহরির বালক রুপ, দুপুরে যুবক রুপ ও রাতে বৃদ্ধ রুপ দর্শন হয়। সকালে শ্রীহরির বিছানায় শয়ন চিহ্ন আর ভোগে আঙ্গুলের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। রাজীম লোচন দর্শন করার পর আমরা একটা হোটেলে খাওয়া সেরে বাসে করে রায়পুর ফিরে এলাম।
প্রথম দফায় তিন বছর ভিলাইতে কাটানোর পরে আমাকে “স্যাডোলে” আসতে হয় আমার কর্মজীবনের প্রথম প্রোমোশনটা লাগু করার জন্য। বিলাসপুর ডিভিশনের বঙ্গ ব্রিগেড এমন একটি চিত্রনাট্য সাজিয়েছিল যাতে প্রোমোশনের টোপে ভিলাই ছাড়তে বাধ্য হই এবং তাদের পক্ষে কৌশলে আমাকে মনিন্দ্রগড় পাঠানো সহজ হয়ে যায়। সে এক অসম যুদ্ধ আমাকে একা লড়তে হয়েছিল। যদিও স্যাডোলে রায়দা ও মন্ডলদা খানিকটা সহানুভূতিশীল ছিলেন কিন্তু তাদের কিছুই করার ছিলোনা। শ্যাডোল থেকে “বান্ধবগড়” খুব কাছে। বান্ধবগড় ভারতের অন্যতম সেরা “ন্যাশানাল পার্ক” যেখানে প্রতিবছর হাজার হাজার দেশি ও বিদেশী পর্যটক কেবলমাত্র বাঘ দেখতেই আসেন। “চার্জার” নামে একটি বাঘ এখানে দীর্ঘদিন পর্যটকদের মনোরঞ্জন করেছে। কখনো পর্যটকদের গাড়ির বনেটে বসে থেকে, কখনো গাড়ির পাশে দৌড়ে আবার কখনো বা রাস্তায় বসে হাই তুলে “চার্জার” বান্ধবগড় অরন্যে প্রচুর দর্শক টেনে এনেছে। “চার্জার” মারা যাবার পরে এই অরন্যের প্রতিটি কর্মী কেদেঁছেন। “চার্জরের” সন্তানরা সন্তদিরা এখন বান্ধবগড় জঙ্গলের শাষক। ভারতের প্রথম সাদা বাঘ এই বান্ধবগড়ের জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল। বাঘ ছাড়াও বান্ধবগড়ের ঘন অরন্যে ভাল্লুক, বাইসন, বুনো কুকুর, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ ও অন্যান্য জানোয়ারদের অভয়ারন্য। স্যাডোল থেকে ট্রেনে কয়েকটা স্টেশন পর “উমারিয়া” স্টেশন। “উমারিয়া” হোল বান্ধবগড় অরন্যের প্রধান প্রবেশ মার্গ। বান্ধবগড়ে জঙ্গলের মধ্যে অবশ্য একটা ভাঙা কেল্লা আছে, পর্থটকরা দুর থেকে সেটা দেখেও আসেন। কেবলমাত্র সাড়ে চার মাসের জন্য স্যাডোলে অবস্থান কালে মনিন্দগড় ট্রান্সফারের ডামাডোলের মধ্যে আমার আর “বান্ধবগড়” যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কয়লার খনি আর জঙ্গলে ঘেরা স্যাডোলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুব সুন্দর। স্যাডোল ছেড়ে কাটনির দিকে এগোলে বাঁধোয়া-ঘুঁনঘুটি চড়াই আর জঙ্গল। রেলগাড়ির স্টলিং এর স্বর্গরাজ্য ছিল। জহরদা কয়েকবার বলেছিল, বাঁধোয়ার জঙ্গল দেখতে যাবি নাকি? কিন্তু যাওয়া আর হোল কই। স্যাডোলে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছিলাম, এখানে বাজারে চাপড় দিয়ে মাংস কাটার মতোন করে মাছ কেটে দিতো। স্যাডোল অঞ্চলটা মহাভারতের বর্নিত “বিরাট রাজ্যের” অন্তর্গত ছিল। অভিমন্যু পত্নী উত্তরার শৈশব এখানেই কাটে। মামা শকুনীর কাছে পাশা খেলায় হেরে যাওয়ায়, শর্ত পালন করতে বারো বছর বনবাস সমাপ্তির পরে, বৃহন্নলা রূপী অর্জুন ও দৌপ্রদী সহ পঞ্চপান্ডব এই “বিরাট রাজ্যে” এক বছর অজ্ঞাতবাসে কাটান। বিরাট রাজ্যেই ভীম কীচক বধ করেছিলেন। এখানে লোকমুখে বিরাট মন্দির আর “বানগঙ্গার” কথা শুনতে পেলাম। শ্যাডোলে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল শনিবার। কোনও এক শনিবারে সাইকেলে চেপে একাই রওনা দিলাম “বানগঙ্গা” আর বিরাট মন্দির দেখতে। জায়গাটা কোথায়, সেটা রাস্তায় লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে চলেছি। সবাই বলে একটু দুরে, কিন্তু রাস্তা আর ফুরোতে চায় না। ছোট্ট জেলা শহর স্যাডোল। শহর পেরিয়ে এসে ধান ক্ষেতর ভিতর দিয়ে এসে অবশেষে বিরাট মন্দিরের দর্শন পেলাম। এখানেই “বানগঙ্গা” রয়েছে। সকালবেলায় বলেই হয়তো কোথাও কোনও লোকজন নেই। দশম শতাব্দীতে কলচুরী রাজাদের তৈরি প্রাচীন মন্দিরটি অত্যন্ত অবহেলায় পড়ে আছে। সেই সময় চত্তীশগড়ের সমস্ত ঐতিহাসিক জায়গাগুলো খুবই অবহেলায় পড়ে ছিল। পঞ্চপান্ডবদের অজ্ঞাত বাসের আগেও মাতা কুন্তী সহ পঞ্চপান্ডব একবার “বিরাট রাজ্যে” এসেছিলেন। এই অঞ্চলে জলের বড়ো অভাব ছিল। এখনো স্যাডোলে জলের অভাব আছে। মাতা কুন্তীর পুজো করার উপলক্ষ্যে জলের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, গান্ডীব ধনুক দিয়ে বান ছুড়ে, এখানেই অর্জুন পাতাল ফুঁড়ে শৃষ্টী করেন এই কুন্ড, যা “বানগঙ্গা” বলে পরিচিত । পাথরের গভীর চৌবাচ্চার মতোন কুন্ডটা, তাতে অপরিস্কার জল। বিরাট মন্দিরের গায়ে নানা মুর্তি এবং বেশ কিছু খাজুরাহ সাদৃশ্য নরনারীর মিথুন মুর্তি নজরে পড়লো। ছোট পাথরের তৈরি শিবলিঙ্গ। আশেপাশে অনেক ধংসাবশেষ অবহেলায় ইতস্তত পড়ে আছে। শুনেছি বতর্মানে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগ এটি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। স্যাডোল থেকে চলে আসার পর লোকমুখে শুনেছি বানগঙ্গা থেকে দুই কিংবা আড়াই কিলোমিটার দুরে গেলেই নাকি “সোহাগপুরে” পৌঁছে যেতাম। সোহাগপুরেই নাকি বিরাট রাজ্যের রাজধানী ছিল। শুনেছি বিরাট নগরীর বেশ কিছু নিদর্শন এখনো নাকি এখানে এলে দেখা যায়। অজ্ঞাতবাসের সময় যে গাছটিতে বৃহন্নলা রূপী অর্জুন তার গান্ডিব ধনুকটা লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেটিও সোহাগপুর এলে দেখা যায়। জানতাম না, তাই সোহাগপুরে আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। পর্যটক তো নই, তার উপর পেটের টানে লোহা লক্করের সাথে সহবাস করতে কলকাতা থেকে সুদূর স্যাডোলে আসা। কি আর করা যাবে, বানগঙ্গার চারিদিকে একা একাই খানিকটা ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে স্যাডোলে ফিরে এলাম।
মনিন্দ্রগড়ে দুবছর থাকাকালীন তেমন ভাবে ঘুরে কিছু দেখা হয়নি। জঙ্গল আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা মনিন্দ্রগড়ে প্রকৃতি দেখেই সময় কেটে যায়, ইতিহাস বা পুরানের খোঁজ করা দরকার পড়েনা । মাটির নীচে কয়লার পর্যাপ্ত ভান্ডার খুঁজে পাবার পরে, জঙ্গল ও আদিবাসী অধ্যুসিত এই অঞ্চলে একশো বছর আগে বৃটীশরা রেল লাইন বসায়। এর পরেই এদিকে বর্হিজগতের মানুষজনদের আনাগোনা শুরু হয় । স্থানীয় সিদ্ধিবাবা পাহাড় আর উদলকাছাড়ের ঝর্না ছাড়া বিশেষ কোথাও যাওয়া হয় নি। এই দুটো যায়গার কথা আমি সবিস্তারে আমার “হাউজ অফ স্টীল হরসেস” গল্পে জানিয়েছি। ভুমিকম্প প্রবন এই অঞ্চল, আমি দু বছরের অবস্থান কালে দুবার ভুমিকম্পর সাক্ষী থেকেছি। স্যাডোল আর মনিন্দ্রগড় থাকাকালীন অনেকেই আমাকে হরিণের মাংস খাওয়াতে চেয়েছে। আমি এসব প্রস্তাব এড়িয়ে গেছি। দীপুদার কোয়ার্টারে ঘনশ্যাম দাশ বলে একটি বাঙালি ছেলে বিলাসপুর থেকে মাঝেমাঝে এসে দুচার দিন থাকতো। রেলেরই কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতো। একদিন একটা গুলতি নিয়ে আমাকে বলল চলুন দাদা, বুঁনো হাঁস শিকার করে আসি। আমি অবিশ্বাস প্রদর্শন করায় বলল ঠিক আছে, রাতে রান্না করলে আপনি পাবেন না। সন্ধ্যার সময় সে সত্যিই গুলতি দিয়ে মারা দুটো ছোট হাঁস নিয়ে ঘরে ফিরলো। কেটে রান্না করে দীপুদাকে আর আমাকে খাওয়ালো।
চাকরিতে জয়েন করার পরে আমাদের আটজনের একটা দল বিলাসপুরে তিন মাসের জন্য ট্রেনিং করেছিলাম। সেইসময় স্টেশনের বিপরীত দিকে “মরিমাই” মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মেঠো পথ ধরে পাঁচ মিনিটের মতো হাঁটা পথ, কিন্তু পথে একটা গা শিরশির করা ব্যাপার ছিল। শোনা যায় বিলাসপুর যখন শহর ছিলোনা তখন থেকেই ঘন জঙ্গলের মাঝে এই মন্দির ছিল। এমনটা শোনা যায় যে একবার কোন একটি শিশুর মৃতদেহ এই মন্দিরে আনার পর নাকি, মায়ের কৃপায় শিশুটি প্রান ফিরে পায়। মৃত মানুষ যে দেবী মাতার স্পর্শে জীবন ফিরে পায় সেইতো “মরিমাই”। সেই সময় থেকে এই মন্দিরেকে “মরিমাই” মাতার মন্দির নামে ডাকা হয়। অসুস্থ ও রোগে ভোগা মানুষজন এখানে এসে “মরিমাই” মায়ের কাছে সুস্থতা কামনা করে। তন্ত্রমন্ত্র ও তুকতাকের একটা মহল ছিল মন্দিরে। সাদা পাথরের তৈরি মহামায়ার ছোট মুর্তি। এর বারো বছর পরে একদিন কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি আবারও একবার এই মন্দিরে আসি। এবারে কোথায় সেই জঙ্গল, সব জঙ্গলে ভোঁ-ভাঁ। পিচের রাস্তা, পথের দুধারে নূতন নূতন সব বাড়ি গড়ে উঠেছে। মন্দিরে চত্বরের মধ্যে অবশ্য তুকতাকের পরিবেশটা তখনও ছিল। মন্দিরে একটি অসুস্থ শিশুকে নিয়ে বাচ্চাটির মা ও বাবা আর একজন রক্ত বস্ত্রধারী সাধু যেন কিসব করছিল। এরপর ছাব্বিশ বছর কেটে গেছে এখানে আর কখনো আসিনি। আজকের অবস্থা কেমন তা কে জানে?
বিলাসপুর থেকে পরপর দুই বছরে এক একবার করে মোট দুবার অমরকন্টক ঘোরা হয়ে গেল। প্রথমবার ডিসেম্বরের শেষে সেকেন্ড নাইট ডিউটি পর ছাপান্ন ঘন্টার রেষ্টে স্ত্রী আর চার বছরের মেয়েকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম অমরকন্টক দেখতে। পরেরবার আমার মেজদি, জামাইবাবু আর ভাগ্নে এসেছিল বিলাসপুরে আমার বাড়িতে বেড়াতে। ওদের নিয়ে সপরিবারে প্রথমে গিয়েছিলাম জব্বলপুর, তারপর সেখান থেকে বাসে করে অমরকন্টক ঘুরতে গিয়েছিলাম। প্রথমবার রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা অবধি ডিউটি করার পর সকাল নটার ইন্দোর প্যাসেঞ্জারে উঠে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে বারোটা নাগাদ পৌছলাম প্রেন্ডা স্টেশনে। একঘণ্টা পরে প্রেন্ড্রা বাস ডিপো থেকে বাস ছাড়লো অমরকন্টকের উদ্যেশ্যে। ঘন্টা দেড়েক সময়ের মধ্যেই পৌছে গেলাম “বৈতরণী” অর্থাৎ অমরকন্টকের বাস স্টপেজে। যাত্রা পথের শেষের দিকটায় বাসটি পাক খেতে খেতে পাহাড়ি রাস্তায় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অবশেষে প্রায় সমতল অমরকন্টকে পৌঁছে গেল। সাতপুরা আর বিন্ধ্য পর্বত, মাঝে মহাকাল পাহাড়ের চূড়ায় নর্মদার তটে পুণ্যতীর্থ অমরকণ্টক। পুরান থেকে শুরু করে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত, সব জায়গাতে এই অমরকণ্টকের কথা বলা হয়েছে। গোটা অমরকন্টক অসংখ্য মন্দির রয়েছে। অগস্ত্য মুনীর আদেশে মাথা নুইয়ে থাকা বিন্ধ্য পর্বতমালার একটি শৃঙ্গ হল অমরকণ্টক। এখন থেকেই পৌরাণিক মতে দিব্যতীর্থ নদী নর্মদার যাত্রা শুরু। গঙ্গা উপাসনার নদী, সরস্বতী জ্ঞানের নদী, নর্মদা তপস্যার নদী। নর্মদা কুণ্ডে উঠে আসা জল গোমুখনালার ভিতর দিয়ে এসে পড়েছে কোটি তীর্থে। নর্মদার উত্সমুখের সন্ধান পান মরাঠা রাজা প্রথম বাজীরাও। পুরাণ বলে, নারদ, বশিষ্ঠ, কপিল, ভৃগু, দুর্বাসার মতো মহান মুনি ঋষিরা তপস্যা করেছেন নর্মদা তীর্থে। অমরকণ্টক নাকি একাধারে শৈব পীঠ, তন্ত্র পীঠ ও অঘোর পীঠ। তাই এখানে তপস্যা করলে, অন্য যে কোনও স্থানে তপস্যার চেয়ে দ্রুত সিদ্ধিলাভ হয়। তাই প্রাচীনকাল থেকে সমস্ত মুনি-ঋষি সাধনক্ষেত্রে হিসেবে নর্মদার পূণ্য তটকে বেছে নিয়েছেন। আজও অমরকন্টকে গেলে প্রচুর গুহা আর তাতে সাধুদের তপস্যা করতে দেখা যায়।
অমরকন্টকের বাস স্টপেজের নাম “বৈতরণী”। বাস থেকে নেমে প্রথমেই মনে হোল যথার্থ নাম দেওয়া হয়েছে। “বৈতরণী” পার করেই তো স্বর্গে প্রবেশ করা যায়। ওপারে জঙ্গল, পাকা রাস্তার ধার ধরে স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারা লাইন করে ঘরে ফিরছে। সার্কিট হাউজে থাকার জায়গা দিল না। কাছাকাছি একটা ধর্মশালায় দুশো টাকা দিয়ে একটা ঘর নিলাম। ফ্যামিলি ছাড়া এরা ঘর দেন না। সাধারণ ব্যাবস্থা হলেও ঘর ও বিছানা কম্বল বেশ পরিস্কার পরিছন্ন, তার সাথে এ্যাটাচ বাথরুম। ধর্মশালায় কোনও খাওয়ার বন্দোবস্ত নেই। পরেরবারে মেজদির সঙ্গে এলে এই ধর্মশালায় জায়গা পাইনি, তাই সবাই মিলে শিখেদের গুরুদ্বোয়ারাতে আশ্রয় পেয়েছিলাম। তখনও বেলা ছিল, হেঁটে হেঁটে আধা কিলোমিটার দূরে নর্মদা মন্দিরে পৌছে গেলাম। বিরাট দরজা দিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকলাম। মন্দিরে প্রধান দেবী নর্মদা আর চারদিকে বিভিন্ন দেবতার ছোট ছোট মন্দির। এই মন্দিরের ভিতরেই একটা বিরাট চৌবাচ্চার মতোন জলাধার। মন্দিরের গায়েই জলাধারের মধ্যে একটি ঘেরা কুন্ড, তার উপর টাঙানো বোর্ডে লেখা “নর্মদার উৎস স্থল”। এখান থেকে শৃষ্টী হয়ে নর্মদা নদী গুজরাটে গিয়ে আরব সাগরে মিশেছে। পৌরাণিক মতে দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যা দেবী নর্মদা। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে শিব চতুর্দশীর দিন দেবী নর্মদার জন্মতিথী বলে মানা হয়। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে, মাতা নর্মদাকে, অত্যন্ত পবিত্র নদী বলে মানা হয়। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে মানুষের সমস্ত পাপ নর্মদা নদীতে এসে ধুয়ে যায়। এমনটাও বলা হয়ে থাকে যে স্বয়ং মা গঙ্গা সংবৎসর সমস্ত প্রানীকুলের পাপ ধুতে ধুতে নিজে অপবিত্র হয়ে ওঠেন, আর সেইজন্য প্রতি বছরে কৃষ্ণগাভীর রুপ ধরে বৈশাখ মাসের সপ্তমীতে নিজে একবার নর্মদাতে এসে সেই সমস্ত পাপ ধুয়ে আবার শুদ্ধ হয়ে চলে যান। সমুদ্রমন্থন কালে উত্থিত কালকুট বিষ পানের পর বিষের জ্বালা নিবারনে মহাদেব এই অমরকন্টকে এসে পাঁচ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেন। সেইসময় তপস্যারত নীলকন্ঠ মহাদেবের গলার ঘাম থেকে শৃষ্ট নর্মদা মাতা। জন্মের সাথে সাথেই শিবের দক্ষিণ চরনে আশ্রয় নিয়ে শিবেরই তপস্যায় মগ্ন হয়ে থাকলেন দেবী । তপস্যা ভঙ্গের পর শিব দেখলেন এক অপুর্ব সুন্দরী কন্যা তার পায়ে বসে তারই তপস্যা রত। সন্তুষ্ট শিব তার নাম রাখেন নর্মদা। শিবের বরে নর্মদা গঙ্গার সমান পবিত্রতার অধিকারী হলেন। শিব অশীর্বাদ দিয়ে বললেন, গঙ্গা মাত্র পাঁচ হাজার বছরের জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। গঙ্গা চলে যাবার পর নর্মদাই হবেন ভারতের সবচেয়ে পবিত্র নদী। আর একটি মত অনুযায়ী শিবের কন্যা নর্মদা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। নর্মদা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি কুমারী হয়েই থাকবেন। অমরকন্টক অঞ্চলে তখন দেবতা ও যক্ষরা প্রতিনিয়ত বিচরণ করতে আসতেন। নর্মদার সৌন্দর্যে পাগল হয়ে একে একে দেবতারা নর্মদাকে বিবাহ প্রস্তাব দিতে লাগলেন আর প্রত্যাখ্যাত হতে থাকলেন। প্রত্যাখ্যাত হয়েও দেবতাগন হাল না ছেড়ে, নর্মদাকে অনুসরণ করতে থাকলে এই অমরকন্টক পর্বত ও জঙ্গলে নর্মদা তাদের সাথে লুকোচুরি খেলে শিবের শরণ নিলেন এবং শিবের বরে দেবতাদের হাতে ধরা না দিয়ে তাদেরকে বোকা বানিয়ে পবিত্র নদী হয়ে বয়ে নীচে চলে গেলেন। মন্দিরের বাইরে সামান্য দূরে রাস্তার অন্যদিকে কলচুরি যুগে প্রস্তুত একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের ধংসাবশেষ অত্যন্ত অবহেলায় পড়ে রয়েছে । একদিকে যখন কলচুরি যুগের শৃষ্টী মন্দির দৃষ্টকটু ভাবে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে অন্যদিকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে জৈন্যদের বিশাল আধুনিক মন্দির নির্মাণ কাজ চলেছে।
রাতে একটা হোটেলে দেশী ঘি দিয়ে মাখা গরম রুটি তরকারি খেয়ে ধর্মশালায় চলে এলাম। খাবার হোটেলটা পরিস্কার পরিছন্ন ছিল তবুও একদম লোকজন ছিলোনা। পরেরবার এখানেই খেয়েছিলাম, কিন্তু কার্তিক পুর্ণিমার হবার জন্য অনেক তীর্থ যাত্রী ছিল, তাই হোটেলেও ভিড় ছিল। তখনো এদিকে টিভি আসেনি। শীতের সময় তাই তাড়াতাড়ি কম্বলের নীচে আশ্রয় নিলাম। পরের দিন সকালে স্নান করে বেড়িয়ে পড়লাম। বাইরে বেড়িয়ে দেখলাম দুটো দল শেয়ারের জিপ গাড়ি নিয়ে লোক হেঁকে যাচ্ছে। দুদিকে আলাদা আলাদা যায়গায় নিয়ে যাবে জিপ। একদল নিয়ে যাবে “সোণমুড়া” আর একদল নিয়ে যাবে “কপিলধারা”। সোনমুড়ার দিকের শেয়ার জিপে উঠে বসলাম। নর্মদা মন্দির থেকে তিন চার কিলোমিটার দূরে শোনমুড়া থেকে “শোন” নদীর উৎপত্তি। এখানেই “শোন” নদীর উৎসের পাশে দেবী শোনাক্ষীর মন্দির, যা একান্ন সতীপীঠের অন্যতম পীঠ। শোনমুড়ায় দেবীর বাম নিতম্ব পড়েছিল। একটা ছোট কুঁয়োর মতো, আর তার চারিদিক সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। এটাই শোন নদীর উৎস। সামান্য দূরে আর একটা কুঁয়ো মতোন বাঁধানো, এটা হোল “ভদ্র” নদীর উৎস। ঢালু পাহাড়ি পথ বেয়ে চলে সামান্য অগ্রসর হয়ে ভদ্র মিশে যাচ্ছে শোনের স্রোতে। এখানে আরেকটি কাহিনী শোনা যায়, যেটা বলে ব্রহ্মার দুই ফোটা চোখের জল থেকে “নর্মদা” আর “শোনের” উৎপত্তি। নর্মদা ও শোনের বিবাহ স্থির হলে নারদের ভাঙানিতে ভদ্র শোণের কাছে এসে জানায় নর্মদা বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। এই কথা শুনে শোণ বরবেশ ত্যাগ করে ধ্যানে বসেন। ওদিকে বিবাহ অনুষ্ঠানে সময়কালে শোন না এসে পৌঁছলে লগ্নভ্রষ্টা নর্মদা, নদী হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে চলে গেলেন আরব সাগরে মিশে যেতে। নর্মদার নদী হয়ে যাবার খবর পেয়ে সমস্ত প্রতারণাটা বুঝতে পারেন শোন। ক্রোধে ভদ্রকে গ্রাস করে নদ রুপ ধারন করে শোন পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বিহারে এসে গঙ্গায় মিলিত হলেন। এখানে বানরের দল থিকথিক করছে। একটু এগিয়ে হটাত করে পাহাড় খাড়া ভাবে শেষ আর সেখান থেকে “শোন” নদ অনেক নীচে ঝড়ে পড়ছে। সামনে বিস্তির্ণ ফাঁকা দিগন্ত। এই জায়গাতে তিন দিক লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে দিয়েছে। এটি একটা সানরাইজ পয়েন্ট। ভোরে প্রচুর লোক সানরাইজ দেখার জন্য এখানে আসে। আমারা অবশ্য কোনবারই সানরাইজ দেখতে যাইনি। এই দিকে মাই-কি-বাগিয়া, কর্ণ মন্দির আরও অনেক যায়গাতেই জিপে করে নিয়ে গেল। অনেকদিনের আগের ব্যাপার সবটা মনে পড়েছে না।
নর্মদা মন্দিরে ফিরে এসে অন্য জিপে করে আমাদের নিয়ে এল কপিলধারাতে। কোটি তীর্থ থেকে নর্মদা আন্তর্ধান করে এই কপিলধারাতে এসে আবারও প্রকট হন। সামান্য বয়ে চলার পর কয়েকশো ফুট নিচে আছড়ে পড়ছে নর্মদার জলধারা। ভক্তরা বলেন মা “নর্মদার প্রতিটি কঙ্কড়ই হল শঙ্কর”। অনেকটা ওপর থেকে নর্মদা ঝরে পড়ছে সশব্দে। জলের নীচে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, তাই অনেকই একটু পাশে থেকে স্নান করছেন। এই গহন অরণ্যে জলপ্রপাতের সামনে বসে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন কপিলমুণি। তা থেকে জলপ্রপাতের নাম কপিলধারা। অমরকণ্টকে এসে কপিলধারা দর্শন করলে মোক্ষলাভ হয়, এমনই জনশ্রুতি। বারবার প্রয়াগ গিয়েও সেই পুণ্য হয় না, একবার অমরকণ্টক আর কপিলধারা দর্শন করলে হয়। পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ার পর, নর্মদার জল ধারা হয়ে বয়ে গিয়েছে আরও গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয়বার কপিলধারায় এসে খুব বিপদে পড়েছিলাম। কার্তিক পূর্ণিমার দিন ছিল। এখানকার সাধুদের বিশ্বাস, মা নর্মদা এদিন কুমারীর রূপ ধরে অমরকন্টকে বিচরণ করেন। প্রতিটি সাধুদের আড্ডা থেকে আমার মেয়েকে ধরে টানাটানি শুরু করলো। কুমারী নর্মদা জ্ঞানে পুজো, ভোজন আর সেবা করবে বলে। এখানে আসা প্রতিটি কন্যা শিশুর সাথে ঐ দিন সাধুরা এমনটাই আচরণ করেন। সে এক বিড়ম্বনার পরিস্থিতি। হাত জোর করে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রত্যেকের কাছ থেকে এড়িয়ে যেতে লাগলাম। সঙ্গে মেজদি, জামাইবাবু আর ভাগ্নে থাকাতে সুবিধে হয়েছিল। কপিলধারা থেকে পাহাড় বেয়ে বেশ খানিকটা নামলে “দুধধারা”। এখানে নর্মদা খানিকটা চওড়া হয়ে খুব সুন্দর ঝর্নার আকার নিয়েছে। জলের ফেনায় ফেনায় রঙ সাদা দুধের মতোন বলে এই ঝর্নার নাম “দুধধারা”। এখান থেকেই নর্মদা গভীর জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। অমরকন্টকে অজস্র মন্দির ও দেখার জায়গা। প্রতিটি জায়গার আলাদা পৌরাণিক মাহাত্ম্য, আলাদা আলাদা ইতিহাস। নিজেদের গাড়ি ভাড়া করে দুদিন লাগে সবটা ঘুরে দেখতে। আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভবপর ছিল না । বিকেলে অমরকন্টক থেকে বিলাসপুরে আসার সরাসরি একটা বাস ছিল। বৈতরনী বাস স্টপেজ থেকে বাসে বিলাসপুর চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা লাগে। পথে বাস “আচানকমার” বলে একটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকখানি পথ যায়। বতর্মানে এটা ন্যাশানাল পার্ক হয়েছে। শুনেছিলাম গোটা কয়েক বাঘ আছে জঙ্গলে। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসার সময় মনে হোল ট্রেনের রাস্তায় পেন্ড্রা হয়ে না গিয়ে বাসের রাস্তায় “আচানকমার” জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অমরকন্টক যাতায়াত অনেক বেশি আকর্ষণীয়।
বিলাসপুর থেকে কোরবা যাবার পথে পড়বে একটা ছোট্ট শহর “রতনপুর”। শাষন কার্য্যের সুবিধার কারনে “দক্ষিণ খোসালার” বিকেন্দ্রীকরনের কারলে “রতনপুর” একটি অংশের রাজধানী হয়ে ওঠে। বিলাসপুর থেকে রতনপুরের দূরত্ব মোটামুটি পচিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার। অমি সপরিবারে তিনবার রতনপুর ঘুরতে গেছি। প্রথমবার কোরবা থেকে বেড়াতে আসা দীপুদা ও বৌদির সাথে বাসে চেপে। পরের দুবার জিপ ভাড়া করে একবার মেজদি কে নিয়ে আর শেষবারে বাবা ও মাকে নিয়ে। “ত্রেতা” ও “দ্বাপর” দুই যুগেই “রতনপুরের” নাম উল্লেখ আছে। রামায়নে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রর মাতা কৌশ্যলার জন্মস্থান রতনপুর। এটাও শোনা যায় যে মাতা পার্বতীকে অপহরণ করার অপরাধে লঙ্কাপতি রাবনের ভগ্নিপতি, শূর্পণখার স্বামী, কার্পারদিদেব শিবের হাতে এখানে নিহত হন। ব্যাথিত শূর্পণখার কাজল নয়নের অশ্রু জলে তৈরি হয় রতনপুরের “কাজল তালাও”। রতনপুর কেল্লার পাশেই একদম মেন রাস্তার ধারেই কাজল “তালাও”। মহাভারতেও রতনপুরের কথার উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে রতনপুরের রাজপুত্র “তমরধ্বজ” অর্জুনের অশ্বমেধের ঘোড়া আটক করে রতনপুরে নিয়ে আসে। অর্জুন রতনপুর আক্রমণ করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলেন রতনপুরের রাজা “ময়ূরধ্বজ” অত্যন্ত ধার্মিক তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজে গিয়ে তার সাথে কথা বলবেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শ্রীকৃষ্ণ এসে রাজা “ময়ূরধ্বজ” কে বললেন যে তার একমাএ ছেলেকে বাঘে ধরেছে। ব্রাহ্মন নিজের প্রানের বিনিময়ে তার একমাএ ছেলেকে ছেড়ে দিতে বললে বাঘটি বলেছে যে একটি শর্তে সে তার ছেলেকে ছেড়ে দিতে পারে। যদি রাজা ময়ূরধ্বজের দেহের একটা আড়াআড়ি টুকরো করে ব্রাহ্মন আনতে পারেন তবে ব্রাহ্মণের ছেলেকে বাঘটি ছেড়ে দেবে। ব্রাহ্মণের কাতর বিনতীতে, রাজা ময়ূরধ্বজ নিজের দেহ আড়াআড়ি ভাবে দুটুকরো করে ফেললেন। ব্রাহ্মন বেশী শ্রীকৃষ্ণ বললেন রাজার চোখে জল অথএব রাজার এই শরীর দান অপবিত্র, তাই তিনি এই দেহ গ্রহণ করবেন না। রাজা ময়ূরধ্বজের রানী বললেন “দেখুন দ্বীজ কাটা শরীরের একটা অংশের চোখে জল থাকলেও অন্য অংশে হাসি বিরাজ করছে”, কাজেই আপনি সেই হাসি মুখের দিকের টুকরো গ্রহন করুন। প্রসন্ন শ্রীকৃষ্ণ নিজের রূপ ধারন করে রাজার প্রান ফিরিয়ে দিলেন। রাজার কথায় রাজপুত্রও অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ফিরিয়ে দিলেন।
প্রথমবার বাসে করে রতনপুর বাজারে নেমে প্রিক্সায় চেপে গেলাম প্রায় দশ কিলোমিটার দুরে “কুঠাঘাট” ড্যামে। একটা খালের পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তার পথ দিয়ে পৌছলাম কুঠাঘাট ড্যামের পাদপ্রান্তে। সিড়িতে চড়ে ড্যামের উপরে উঠে আসতেই সামনে খুলে গেল দিগন্ত। বিরাট ড্যাম, চারিদিকে পাহাড়ের মাঝে বেঁধে রাখা হয়েছে জলকে, অসাধারণ সুন্দর শোভা। পাহাড়, জঙ্গল আর জলের এক অপুর্ব চিত্রপট। “খারুন” নদীর বাঁধ এটা। রায়পুর ছেড়ে ভিলাইয়ের দিকে যাবার সময় “খারুন” নদী পেরিয়ে দূর্গ জেলার ভিলাই ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। সেই সুবাদে “খারুন” নামটার সাথে দারুণ পরিচয় ছিল। সেই ছোট্ট “খারুন” নদীর বাঁধের কি অসাধারণ চেহারা ভাবাই যায়না। ড্যামের জলে কুমীর আছে তাই জলে নামা বারন বলে একাধিক বোর্ড লাগানো ছিল। সেই সময়টা আরও পচিশ বছর এগিয়ে গেছে। এখন নাকি ওখানে পিকনিক করার অনুমতি পাওয়া যায়। জিপ নিয়ে যে দুবার গিয়েছিলাম সেবার মেন রাস্তা দিয়ে সোজা ড্যামের কার্যালয়ের সামনে দিয়ে গিয়েছিলাম। ড্যামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপোভোগ করে চলে এলাম রতনপুর কেল্লায়। ভগ্নদশা কেল্লার, কোনও দেখভাল নেই। ভিতরে ঢোকা গেলনা দূর্ঘটনায় ঘটার ভয়ে। তাছাড়া সাপ ও বিচ্ছুর ভয়ও ছিল। এখন শুনেছি সবকিছু পরিস্কার করে পর্যটকদের জন্য দেখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। রতনপুরে পয্যটকদের থাকার জন্য হোটেল হয়েছে। রতনপুরের কেল্লার সঠিক ইতিহাস কেউ জানেনা। অনুমান করা হয় রাজা রতনদেব এগারোশো শতাব্দীতে এই কেল্লা তৈরি করেছিলেন। এরপর আমরা হেঁটে চললাম রতনপুরের মহামায়া মন্দিরে। অনেকটা হাটাপথে গেলে মন্দিরটা পাওয়া যাবে তবে হাটতে হাটতে বোঝা গেল মায়ের মন্দিরে ভালোই ভক্ত সমাগম হয়। এটা সতীপিঠের একটা পিঠ, সতীর কাঁধ এখানে পড়েছিল। রাজা রতনদেব এগারোশো শতাব্দীতে এই মন্দির বানিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় আরতি দেখে বিলাসপুরে ফিরে আসি। রতনপুর প্রবেশের দুই কিলোমিটার আগে মহামায়ার ভৈরব মন্দির পড়ে, যদিও যাতায়াতের পথে এই মন্দিরে আমারা কখনো থামিনি। বিলাসপুর থেকে আরেকটা জায়গায় যাওয়া যায়। সেটার নাম তালাগাঁও। বিলাসপুর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মণিয়ার নদী। খুব পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা জল। আর আছে দুই মন্দির দেওরানী-জেঠানী। এটা দুই জায়ের মন্দির। সবটাই ধ্বংস স্থুপ। এই অঞ্চলে খনন করে অনেক দেব দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। সবগুলো ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং অদ্ভুত আকৃতির। আমার অবশ্য তালগাঁও যাবার সৌভাগ্য হয়নি, তবে আমার অনেক পরিচিতজন ওখানে গিয়ে দেখে এসেছে।
রামের বনবাসের মতোন চত্তিশগড়ে আমারও চোদ্দ বছরের বাস। ভিলাইতে মন বসে গেলেও সাত বছরের বেশি এখানে থাকতে পারিনি। বাকি সাত বছর মনিন্দ্রগড় আর বিলাসপুর অর্থাৎ “দক্ষিণ খোসালার” রতনপুর ক্ষেত্রে কাটিয়েছি। আমি জানিনা বিদেশের মাটিতে প্রতি ছত্রে ছত্রে এত পৌরাণিক কাহিনী বা এত গৌরবময় ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় কিনা? তবে ছত্তিশগড়ে প্রকৃতি, পৌরাণিক কথা, ইতিহাস ও মানুষজনের পরশ যেভাবে আমাকে সম্বৃদ্ধ করেছে তাতে সামান্য সময়ের জন্য বিদেশ ভ্রমণ নাইবা হোল, তাই আমার অন্তত কোন অপ্রাপ্তির অনুভূতি নেই। ছত্তিশগড় বেড়াতে যান, ছত্তিশগড়কে অনুভব করুন আর ভালোবাসুন।