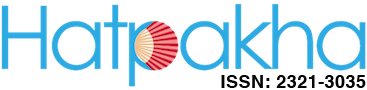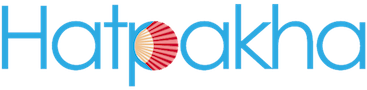“বাউল” শব্দটি শুনলে বা কোন বাউল দেখলে সাধারণভাবে আমাদের মনে হয়, কোনো ঘরছাড়া উদাসী সাধকের কথা, কিংবা কোনো এক বিশেষ দর্শনের কথা অথবা কোনো মরমী গানের কথা। সত্যিকার অর্থে বাউল হলো এসকল অর্থের বিচারে যেকোন একটি এবং একই সাথে সকল অর্থের সমাহার। বাউলের ভিত্তি হলো বহুবিধ ধর্ম-দর্শনে সৃষ্ট “বাউলতত্ত্ব”। এই তত্ত্বকে মান্য করে যে বা যারা স্বতন্ত্র জীবনযাপনের পথ বেছে নেন, তিনি বাউল বা বাউল সাধক। এই তত্ত্বকে যখন বিশেষ সুরে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখন তা হয়ে উঠে বাউল গান। বাউলগণ একদিকে গানের মাধ্যমে সাধনার তত্ত্ব প্রচার করেন, অপরদিকে তাঁরা গানের মাধ্যমেই “মনের মানুষ”, “প্রাণের মানুষ” অর্থাৎ ঈশ্বর-আল্লাহ-ভগবানকে খুঁজেন। বাউল তত্ত্বে বা আদর্শে দীক্ষিত না হলে কারো পক্ষে বাউল গানের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব না। যেমন মহাত্মা লালনের একটি গান:
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কি
ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম, তারে তোমরা বলবে কি?
তিন মাসের এক কণ্যা ছিল, নয় মাসে তার গর্ভ হল
এগার মাসে তিনটি সন্তান, কে বা করবে ফকিরি?
ঘর আছে তার দুয়ার নাই রে, লোক আছে তার বাক্য নাই রে
কে বা তারে আহার জোগায়, কে বা দেয় সন্ধ্যাবাতি?
ফকির লালন ভেবে বলে, ছেলে মরে মাকে ছুঁলে
এই তিন কথার অর্থ না জানলে, তার হবে না ফকিরি।।
বাউল সাধনার শীর্ষস্তরে না গিয়ে কারো পক্ষে কি এই গানে কি বলা হয়েছে তা বুঝা সম্ভব? তবুও আমরা নিজেদের মতো করে এরকম গানগুলোর একটা মানে দাঁড় করিয়ে নিই। সেই মানেটা কতটা গভীরে যেতে পারে বা কতটা নিগূঢ়তাকে স্পর্শ করতে পারে তা কেবল প্রকৃত বাউলগণই বলতে পারবেন। আবার এখানেও প্রতিবন্ধকতা আছে, কেননা প্রকৃত বাউল হলে তাঁর কর্তৃক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বক বিতরণ করাও যথেষ্ট কঠিন। কারণ বাউলতত্ত্বের সাধকরা বেদ, বাইবেল বা কোরানের মত মান্য করা যায় – এমন কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। বাউলদের কাছে ধর্মগ্রন্থের চেয়ে গুরু বা মুর্শিদ বড়। বাউল সাধকরা কোনো অলৌকিক গল্পকথা দ্বারা তাঁদের দর্শনকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেন নি। বাউল সাধকদের ভাবনা গ্রন্থাকারে প্রচারের পরিবর্তে শিষ্যদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। সে কথাও আবার সবার জন্য হয়ে উঠে নি। কারণ গুরুর বারণ – “আপন সাধনার কথা, না বলিও যথা তথা”। তাই বাউলতত্ত্ব পরিণত হয়েছে গুপ্তবিদ্যায়। এ বিদ্যার পারিভাষিক শব্দাবলির গভীরে লুকিয়ে আছে তাত্ত্বিক রহস্যময়তা। মনে হতে পারে বাউল গুরুরা নিজেরাই নিজেদের কথা রাখেন নি। কারণ তাঁরা তাঁদের গানে গানে সর্বজনের কাছে বাউলতত্ত্বের গোপন কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু ভাবসন্ধানের বিচারে সে গান কি সকলের বোধগম্য হয়ে উঠেছে? নিতান্তই শ্রোতা হিসেবে যাঁরা সুরের মোহে বাউল গানে মুগ্ধ হন, ভাবসন্ধানে এসে তাঁরাই অসহায় বোধ করেন। গানের সুরে বাউল গান কাছে টানে, আর ভাবের সুরে বাউলতত্ত্বের মর্মের গভীরে টেনে নিয়ে যায়। বাউল গানের সুর লোকজ। বাংলা লোকগানের প্রধান চারটি ধারার সুরের ভিতরে বাউল সুর একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তবে সুরের কাঠামোগত রূপের ভিতরে পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি এবং পশ্চিমবঙ্গের কীর্তনের প্রভাব। উদ্দীপনামূলক গানে রয়েছে চঞ্চল গতি। আনন্দ প্রকাশের অংশ হিসেবে গানের সাথে এঁরা নাচে। এঁদের নাচ ধরা-বাঁধা ছকে আবদ্ধ নয়। এ নাচে বন্ধনের আড়ষ্ঠতা নেই, আছে মুক্তির আনন্দ। বাউল নিজে নাচে যত, শ্রোতাকে নাচায় তাঁর চেয়ে বেশি। বাউল ভাবের ঘোরে নাচে, আর শ্রোতা সে নাচে উদ্বেলিত হয়। বাউলের গানে তাল নেই, আছে ছন্দ। তালটা যান্ত্রিক বলে, তাতে আনন্দ কম। ছন্দ হলো নান্দনিক, তাই ছন্দ আনন্দময়।
ইতিহাসবিদদের মতে, সতেরো শতকে বাংলাদেশে বাউল মতের উদ্ভব হয়। এ মতের প্রবর্তক হলেন আউল চাঁদ ও মাধববিবি। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষায় “বাউল” শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে বাহ্যজ্ঞানহীন, উন্মাদ, স্বাভাবিক চেতনাশূণ্য, ক্ষ্যাপা ইত্যাদি। যাঁরা বাউল ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন এবং যাঁরা প্রথাগত ধর্মমতের বাইরে এসে ভিন্নমতকে গ্রহণ করতে পারেন নি মূলত তাঁরাই এই নামগুলো দিয়েছিলেন। এরূপ ধারণার পিছনে বাউলদের জীবনযাত্রার ধরণই দায়ী ছিল। কারো মতে সংস্কৃত “বায়ু” শব্দটি থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি। সংস্কৃত বায়ু = বাংলা “বাউ” শব্দের সাথে “ল” প্রত্যয়যোগে বাউল শব্দটির উৎপত্তি, অর্থাৎ বাংলার যে সব লোক “বায়ু” অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাহায্যে সাধনার মাধ্যমে আত্মিক শক্তি লাভ করার চেষ্টা করেন, তাঁরাই বাউল। কারো মতে যে সব লোক প্রকৃতই পাগল, তাই তাঁরা কোনো সামাজিক বা ধর্মের কোনো বিধিনিষেধ মানে না, তাঁরাই বাউল। আবার কেউ কেউ বাউল শব্দটিকে মুসলমান সাধক অর্থে আরবি “অলী” শব্দের বহুবচন “আউলিয়া” শব্দ হতে “ইয়া” প্রত্যয়ের পতনে উৎপত্তি বলে মনে করে থাকেন। তাঁদের মতে বাংলার যে সব লোক মুসলমান দরবেশদের মতো লম্বা আলখেল্লা পরে, তাঁদের বাণী ও বিশ্বাসে আস্থাপরায়ণ হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, তাঁরাই বাউল। এই জন্যই নাকি বাউল-সন্ন্যাসীদের “ফকির” বলা হয়। সর্বোপরি বাউলেরা নিজেরা যেহেতু নিজেদের বাউল নামটি দেন নি, সেহেতু “বাউল” শব্দটির উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা নিয়ে নানা ধরনের মত প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বাউল মতের মর্মকথা অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার।
বাউল গানে নিতান্তই প্রেম বা প্রকৃতির গান নেই। এদের গানের একমাত্র বিষয় বাউল ভাবনা কেন্দ্রিক তত্ত্বকথা। বাউলতত্ত্বের সাধকগণ বাউল গানে প্রথাগত রাগরীতিকে অনুসরণ করেন নি। শাস্ত্রীয় বা নাগরিক গানের তালের পরিবর্তে, তাঁরা ভাবের দোলায় আপন ছন্দে গান বেঁধেছেন। এদের গানে নানা ধরনের রূপক শব্দ পাওয়া যায়। যা ভাব প্রকাশের সহায়ক হলেও এর বাণী সাধারণ মানুষের কাছে সহজে ধরা দেয় না। বাউল গানের বাণী চর্যাপদের মতই “সন্ধ্যাভাষা”। যেখানে বাইরে এক কথা থাকে কিন্তু ভিতরে অন্য ভাব থাকে। এই গানের বাণীতে পাওয়া যায় প্রশান্ত ভাব, যা আধ্যাত্মিক দর্শনকে প্রকাশ করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এ গানের বাইরের রূপ প্রতীকী; ভিতরের কথাটাই আসল। লালন যখন বলেন, “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।” তখন আক্ষরিক অর্থে ”খাঁচা” এবং ”পাখি” মূল তত্ত্বকে প্রকাশ করে না। কিন্তু প্রতীকী ”খাঁচা” শব্দের মূল অর্থ যখন হয় ”দেহ” আর “পাখি”র অর্থ হয় “প্রাণ” বা “মন”, তখন ভাবের ঘরে নতুন চৈতন্যের উদয় হয়। বহুদিন ধরে অজস্র বাউল গানের ভিতর দিয়ে বাউল দর্শন বর্ণিত হয়েছে। এ দর্শন এমনি প্রতীকী মোড়কে আবদ্ধ। গুরুর কাছে বসে শিষ্যরা বাউলতত্ত্বের গোপন অর্থ আয়ত্ত্ব করেন সযত্নে। তাঁদের কাছে এ সকল গানের ভাবের বিচার হয় আরও গভীর তত্ত্ব কথায়।
একালে তালে বেঁধে যে বাউল গান উপস্থান করা হয়, তাতে তালের শুদ্ধতা থাকে, কিন্তু অনেক সময় বাউল গানের ছন্দটাই হারিয়ে যায়। আবার বাউল গানের সুরের ঢং রেখে গান বাঁধলেই কেবল বাউল গান হয় না। তার ভিতরে বাউল দর্শনও থাকা আবশ্যক। বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, হিন্দুধর্ম থেকে আগত বাউলগণ নামের শেষে “দাস” ও “বাউল” এবং মুসলিম ধর্ম থেকে আগত বাউলগণ নামের শেষে “শাহ্”, “ফকির” ও “বাউল” যুক্ত করে দেশ-বিদেশ সফর করছেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন। মানুষের সামনে বিভিন্ন রং-এর বাহারি তালি দেয়া পোষাক পরিধাণ করলেও তাদের বেশিরভাগেরই যাপিত জীবন কিন্তু বেশ আয়েশি। অপরদিকে সমাজের বিভিন্ন অংশের চাপ সামলাতে সামলাতে বাউল সাধনা-তত্ত্ব বিলুপ্ত প্রায়। হাটে-মাঠে-গঞ্জে-আখড়ায় বাউল হিসেবে আমরা যাদের দেখি, তাদের অধিকাংশই কর্মে ভীত একশ্রেণির মানুষ, কিংবা বাউল বেশ ধারণ করে নানাধরণের অপকর্মে লিপ্ত। বাউলরা আজ দারুনভাবে পণ্যে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটা সময়ে বাউলতত্ত্ব ও সাধনা ধর্মাশ্রয়ীদের বেশ বিপদেই ফেলে দিয়েছিলো। শাস্ত্র-কিতাবের বাইরে গিয়ে এবং সকল প্রকার জাত-পাতকে পিষ্ঠ করে বাউলগণ মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ঈশ্বর খুঁজেছেন। তাঁদের সাধনায় ঈশ্বর ছিলোনা, বর্ণ-ধর্ম ছিলোনা, ধনী-গরীব ছিলো না । কিন্তু তাঁদের গুরু ছিলেন, মুরশিদ ছিলেন।
বাউলদের জ্ঞান আহরণের জন্য তা ছেঁকে নিতে হবে মারফতের মাধ্যমে। মারফত জানতে হয় মুর্শিদের মাধ্যমে। মুর্শিদ হলো সেই শক্তির আঁধার, যিনি শিষ্যকে সরল-গরল, ভালো-মন্দের ভেদ-প্রভেদ বুঝিয়ে দেন। মুর্শিদ শিষ্যকে বাউলের গোপনীয় গুহ্যতত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন। বাউলেরা সাধনার আশ্রয় হিসেবে দেহকে অবলম্বন করে থাকেন এবং দেহ-ঘরের মধ্যে তাঁরা সৃষ্টি-স্রষ্টার অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন, আর গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাউলেরা সাধনার ধারা অব্যাহত রাখেন। এক্ষেত্রে গুরুকে তাঁরা স্রষ্টার সমতুল্য বিবেচনা করেন। তাঁরা মনে করেন গুরু বা মুর্শিদকে ভজনা করার ভেতর দিয়ে স্রষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করা যায়। দেহের আধারে যে চেতনা বিরাজ করছে, সে-ই আত্মা। এই আত্মার খোঁজ বা সন্ধানই হচ্ছে বাউল মতবাদের প্রধান লক্ষ্য। বাউলরা আল্লাহ, ঈশ্বর কিংবা সৃষ্টিকর্তাকে নিরাকার মানতে নারাজ। ঈশ্বর নামক শক্তিকে তারা সাকার হিসেবেই মানেন। যেমন ভাটির বাউল শাহ আব্দুল করিম বলেছেন; “আমি কখনোই আসমানি খোদাকে মান্য করি না। মানুষের মধ্যে যে খোদা বিরাজ করে আমি তার চরণেই পূজো দেই।” বাউল করিমের এ কথায় স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ হয় যে বাউলরা নিরাকার সৃষ্টিকর্তা মানতে নারাজ। বাউলদের বিশ্বাস মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা আসীন, তাই মানুষ ভজলেই ঈশ্বরের নৈকট্য সম্ভব। এ প্রসঙ্গে ড. আহমেদ শরিফ তার বাউলতত্ত্ব গ্রন্থে লিখেছেন ”বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাউল মত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে হয়েছে বাউল সম্প্রদায়। তাই পরমত সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনে ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এদের বৈশিষ্ট্য।” তাই মুসলমান বাউলদের হিন্দু গুরু বা হিন্দু বাউলদের মুসলমান গুরু এমন প্রায়শই দেখা যায়। বাউলতত্ত্বের আদর্শসমূহ হলো – গুরুবাদ, শাস্ত্রহীন সাধনা, দেহতত্ত্ব, মনের মানুষ, রুপ-স্বরূপ তত্ত্ব ইত্যাদি। বাংলাদেশের বাউলেরা এভাবেই অকাট্য যুক্তির আলোকে শরিয়তি গ্রন্থকে সামনে রেখেই গুরুবাদী ধারার সাধনচর্চাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয়, মানুষ-গুরু ভজনা এবং মানুষকে সেজদার যোগ্য বিবেচনা করে, তার ভেতর দিয়েই যে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ ইবাদত সম্ভব; বাংলার বাউল-সাধকেরা সেকথা ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করেন নি।
বাংলার বাউল-সাধক পদকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হলেন ফকির লালন সাঁই। লালন সাঁই তাঁর সমগ্রজীবন ব্যয় করেছেন বাউল-সাধনার স্থায়ী ও একটি গানগত রূপ দিতে, তাঁর গানে বাউল-সাধনার করণ-কার্যের নানাবিধ নির্দেশনা আছে। তিনি দৈন হতে শুরু করে গোষ্ঠ, গৌর, আত্মতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি পর্বের গানের পাশাপাশি সমাজ-সংস্কারমূলক মানবিকতার উদ্বোধনমূলক গান রচনা করেছেন। বাউল-সাধনার গুরু-শিষ্য পরম্পরার লালন প্রবর্তিত ধারাটি অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত বেগবান রয়েছে। লালনপন্থী সাধকদের মধ্যে পদ রচনায় অন্যান্য যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে দুদ্দু শাহ, খোদাবক্স শাহ, বেহাল শাহ, মকছেদ আলী সাঁই, মহিন শাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ও ভারতের বাউল-সাধক, পদকর্তা ও সংগীতশিল্পী হিসেবে যাঁদের স্বীকৃতি রয়েছে, তাঁরা হলেন যাদু বিন্দু, দ্বিজ দাস ঠাকুর, পাঞ্জু শাহ, গোসাই গোপাল, হাসন রাজা, আলফু শাহ, জালালউদ্দিন খাঁ, রশিদ উদ্দিন, উকিল মুন্সি, পাগল বিজয়, দূরবীন শাহ, আলাউদ্দিন শাহ, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, ভবা পাগলা, রজ্জব আলী দেওয়ান, মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান, নবনী দাস বাউল, পূর্ণদাস বাউল, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ। যুগে যুগে কালে কালে শত সহস্র বাউলেরা পূর্বে যেমন এই সাধনা ও গানের ধারা চর্চা করেছেন, বর্তমান কালেও অগণিত বাউল-সাধক-ভক্তগণ এই ধারা অব্যাহত রেখে চলেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গেলে এখনও বাউলের দেখা মেলে, এমনকি চলতে পথে রাস্তায়, ট্রেনে, বাসে বা শহরাঞ্চলেও বাউল শিল্পীদের প্রসার চোখ এড়িয়ে যায় না, কেননা তাদের কণ্ঠে থাকে সুমধুর গান আর ভাবের বিস্তার।
২০০৫ সালে “ইউনেস্কো” বিশ্বের মৌখিক ও দৃশ্যমান ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে বাউল সঙ্গীতকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষনা করেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সৃজনশীল সাধকদের মধ্যে “বাউল সম্প্রদায়” অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বাউলদের রচিত সঙ্গীতে ভাবের গভীরতা, সুরের মাধুর্য, বাণীর সার্বজনীন মানবিক আবেদন বিশ্ববাসীকে যেন এক মহামিলনের মন্ত্রে আহ্বান করে। আবার, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো বাংলার বাউল সঙ্গীতকে ”দ্যা রিপ্রেজেন্টেটিভ অব দ্যা ইন্ট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি”র তালিকাভুক্ত করেছে। অবশ্য তারও আগেই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাটের দশক হতেই যেন ইউরোপ-আমেরিকার নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউলগান ও বাউলদের সাধনপদ্ধতি নিয়ে নানা ধরণের গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি এই বাংলার বাউলগান পরিবেশন করতে গ্রামের বাউল-সাধক শিল্পীগণ বিভিন্ন দেশ-বিদেশেও ভ্রমণ করেছেন। তবে, জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাউলদের সাধনা কিংবা সঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহের সূচনা হয়ে ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী অথবা নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের তৎপরতায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “বাংলার বাউল” সম্পর্কে বিশেষভাবে বিশ্ববাসীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে ছিলেন, এমনকি তিনি তাঁর নিজের রচনাতেও ভাবসম্পদ হিসেবে বাউলগানের ভাবাদর্শ গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি” এর সুরও গৃহীত হয়েছে বাউল গগন হরকরার গান হতে। বর্তমানে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার” আবহমান বাউলগান সংরক্ষণের জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছেন। গত ২২ জানুয়ারি, ২০২০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে বলেছেন, “এখন সরকার বাউল গানকে বিশ্ব-ঐতিহ্য করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। তাই অনুরোধ করব, বাউল গানে সম্পৃক্তরা যেন এমন কোন কাজ না করেন, যাতে বিশ্ব-ঐতিহ্য বাউল গান প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।” বাউল শিল্পীরা আশা করছেন, বাংলাদেশে বাউল গান এবং বাউল তত্ত্বের ধারা খুব সহসাই বিলুপ্ত হবে না, বরং বাউল গানের প্রচার ও প্রসার আরও ব্যাপক আকারে হবে এবং বাউল শিল্পীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের যোগ্যতায় পরিচিত হতে পারবেন।